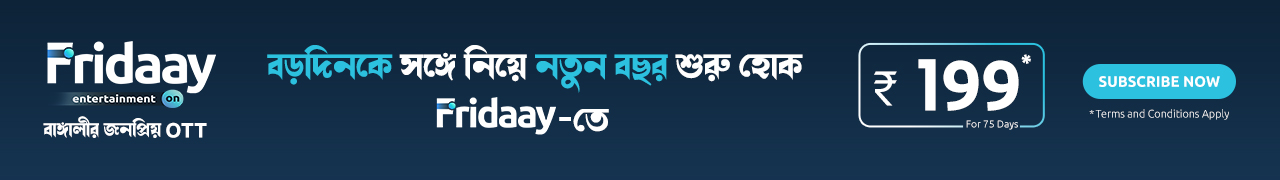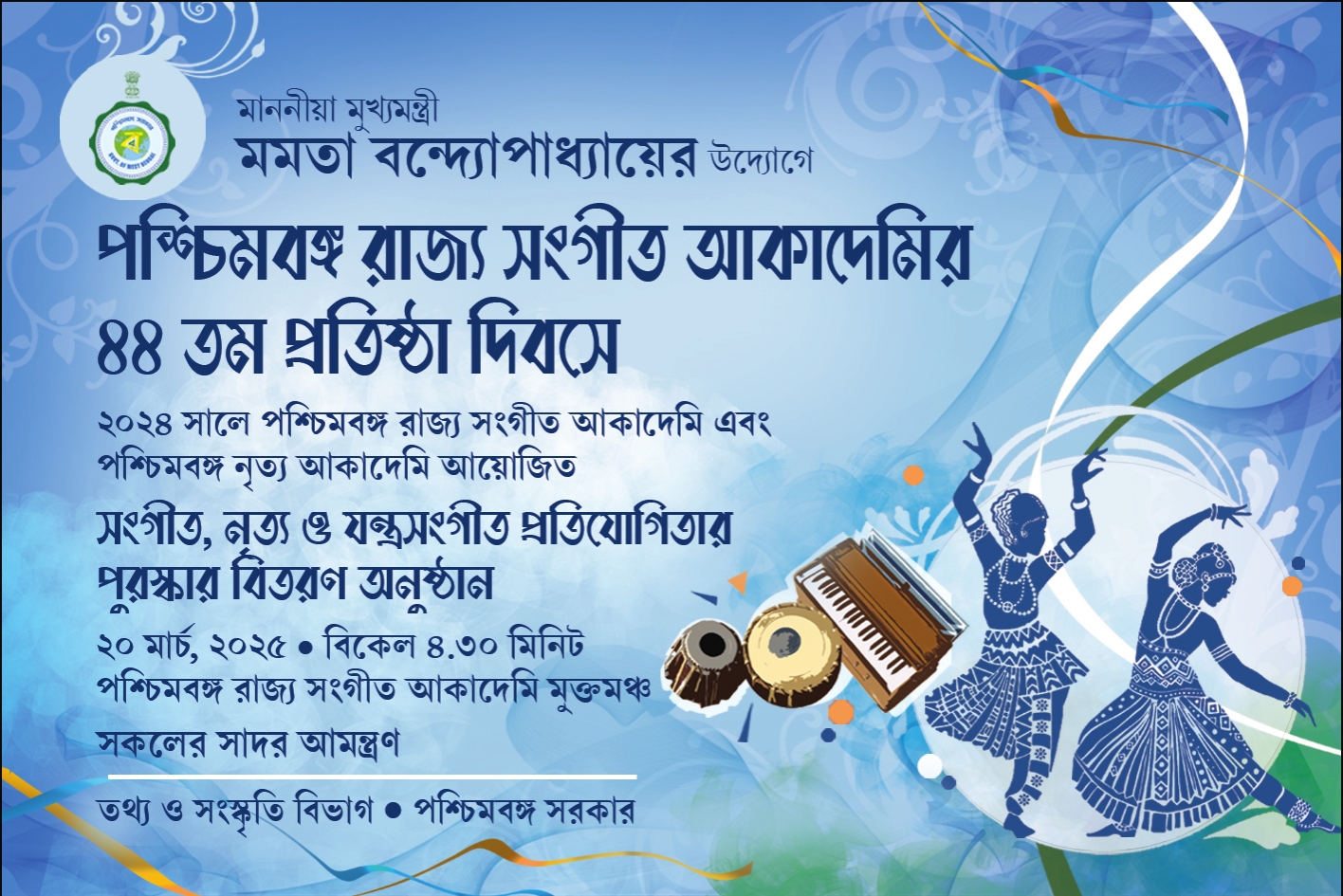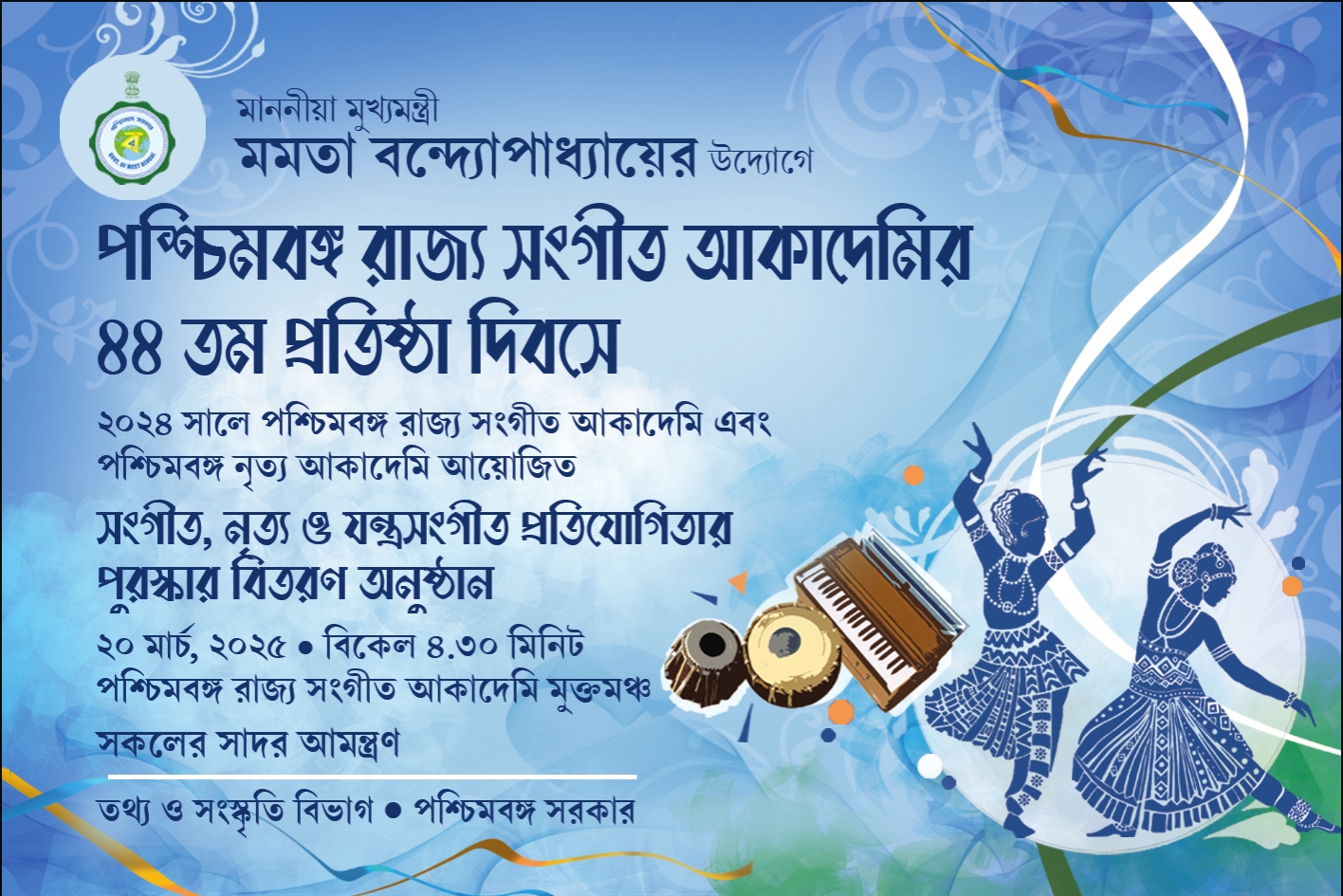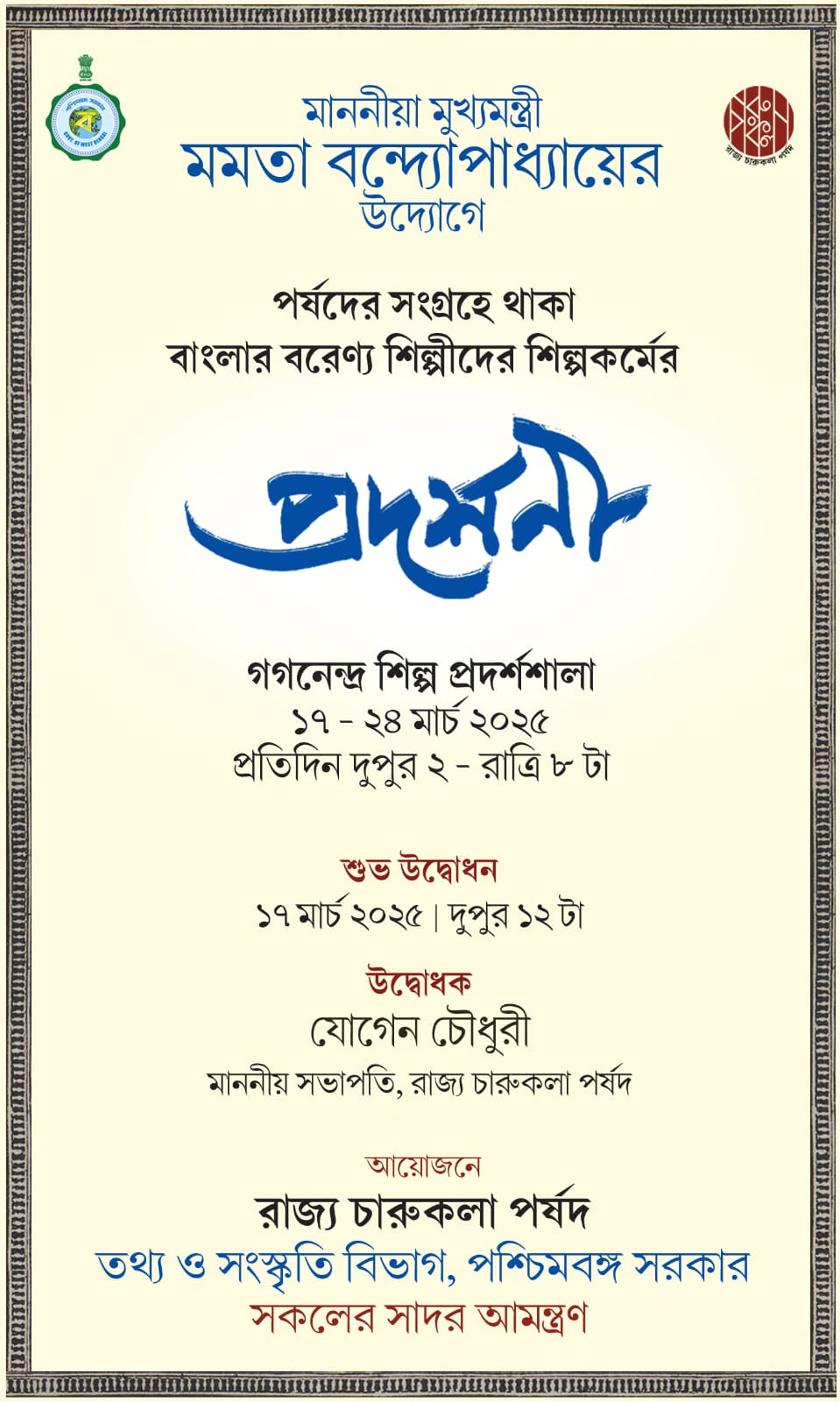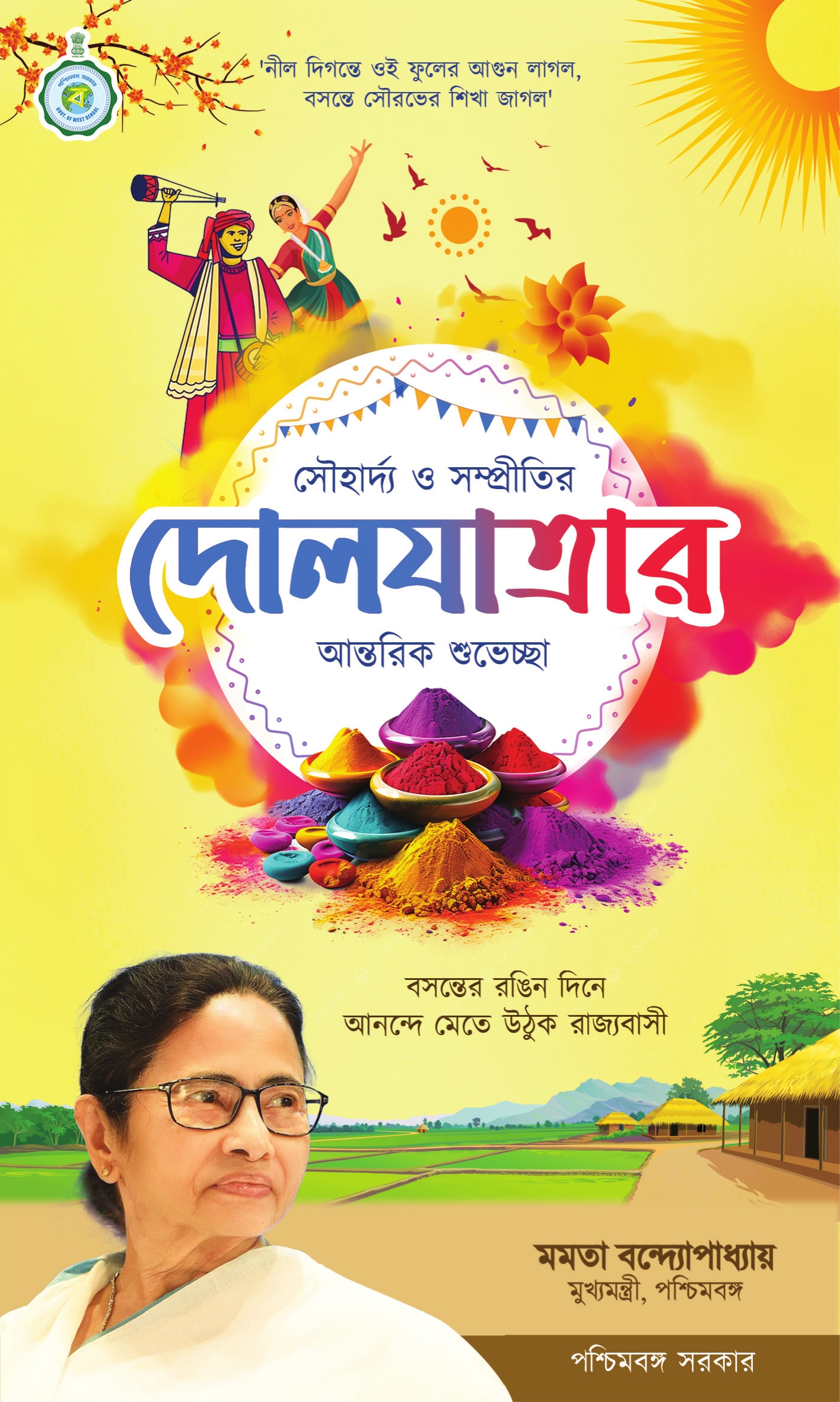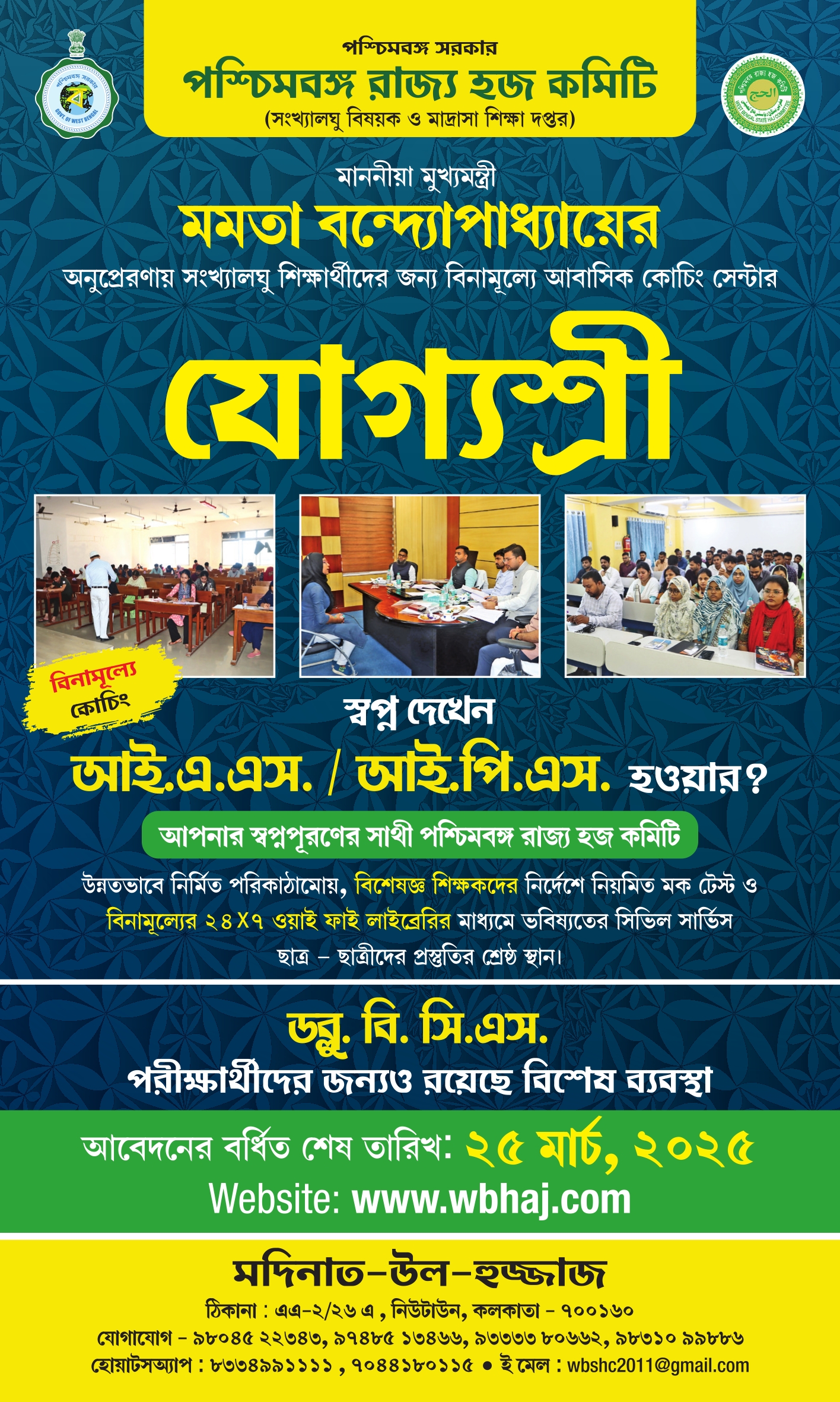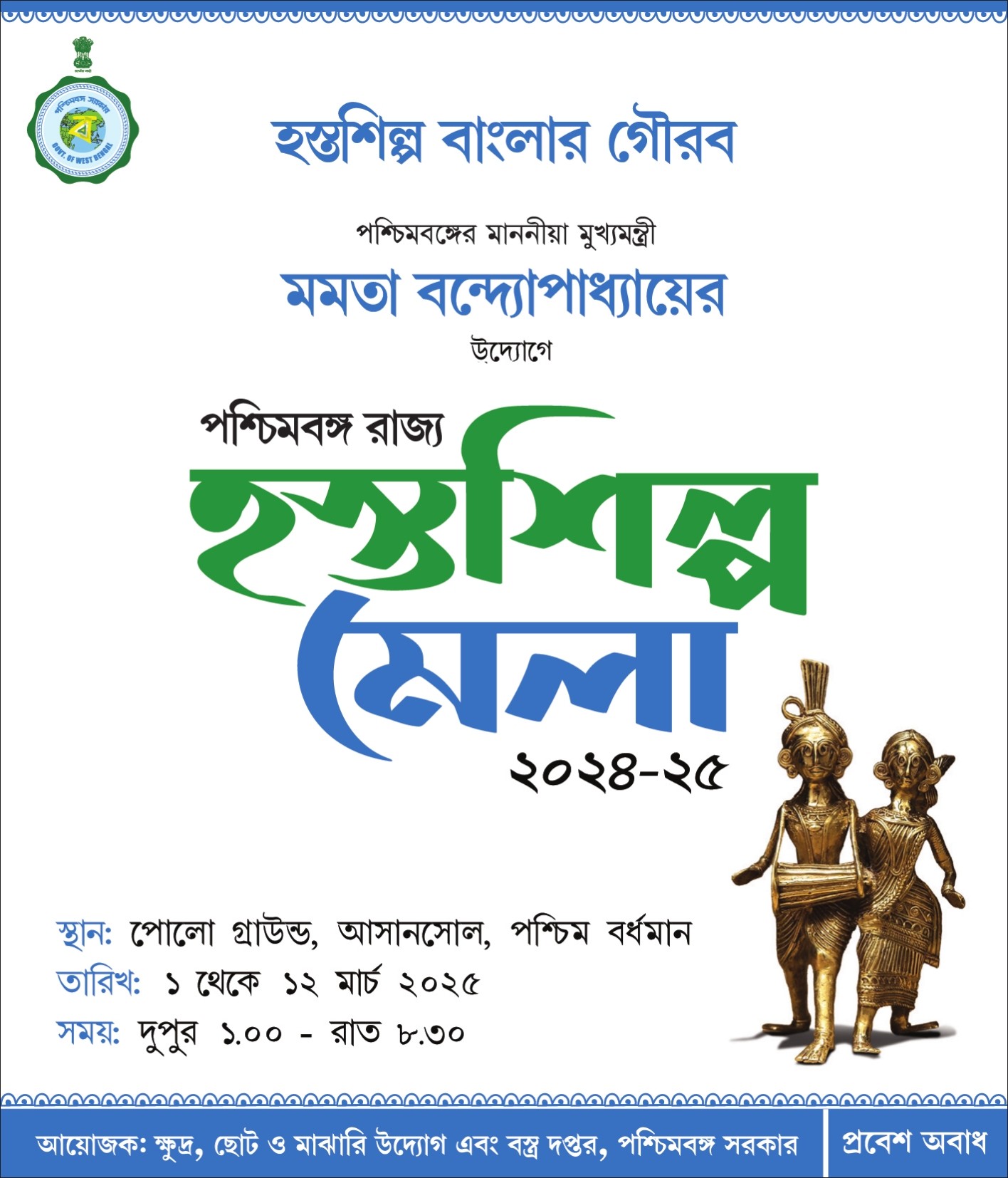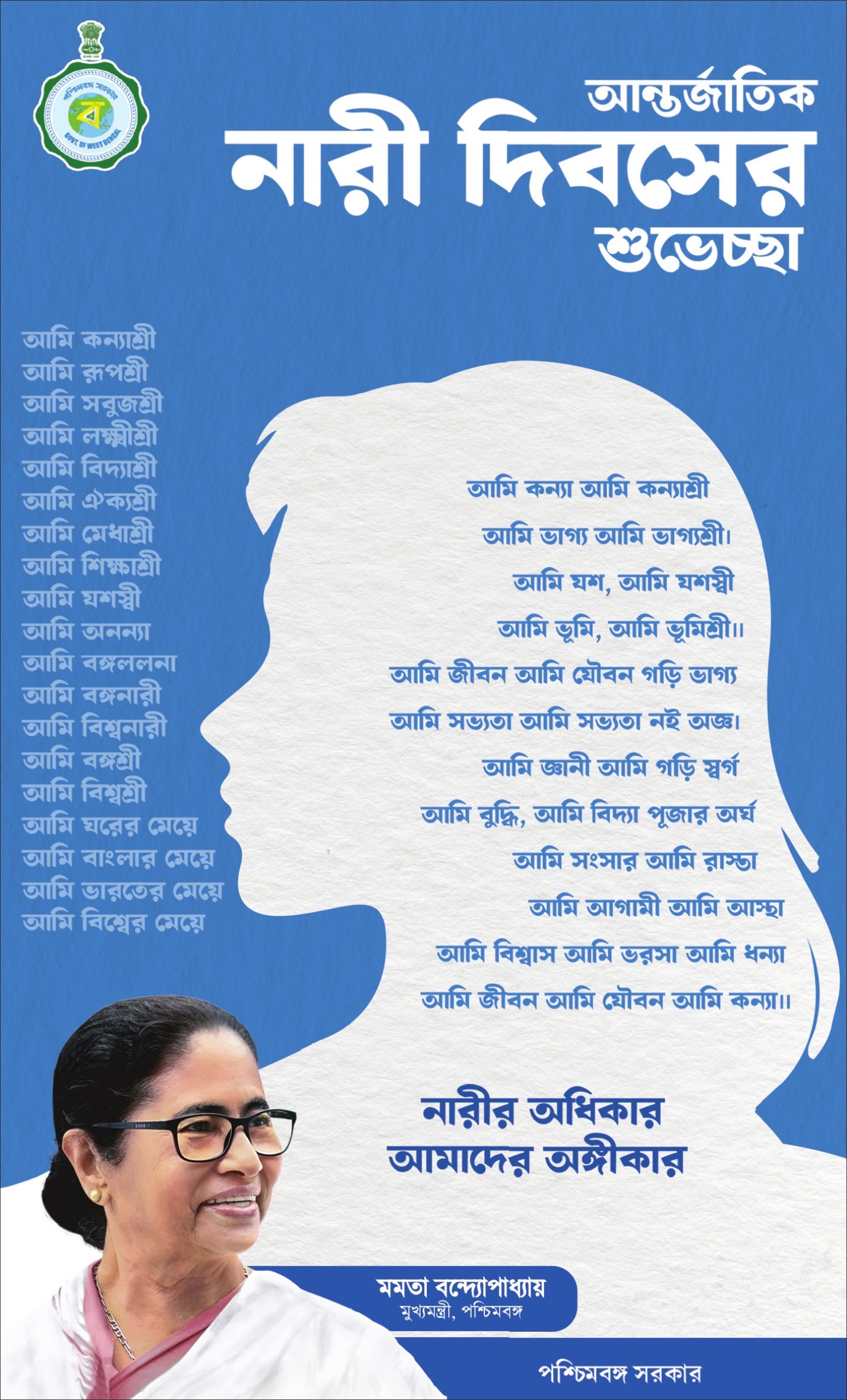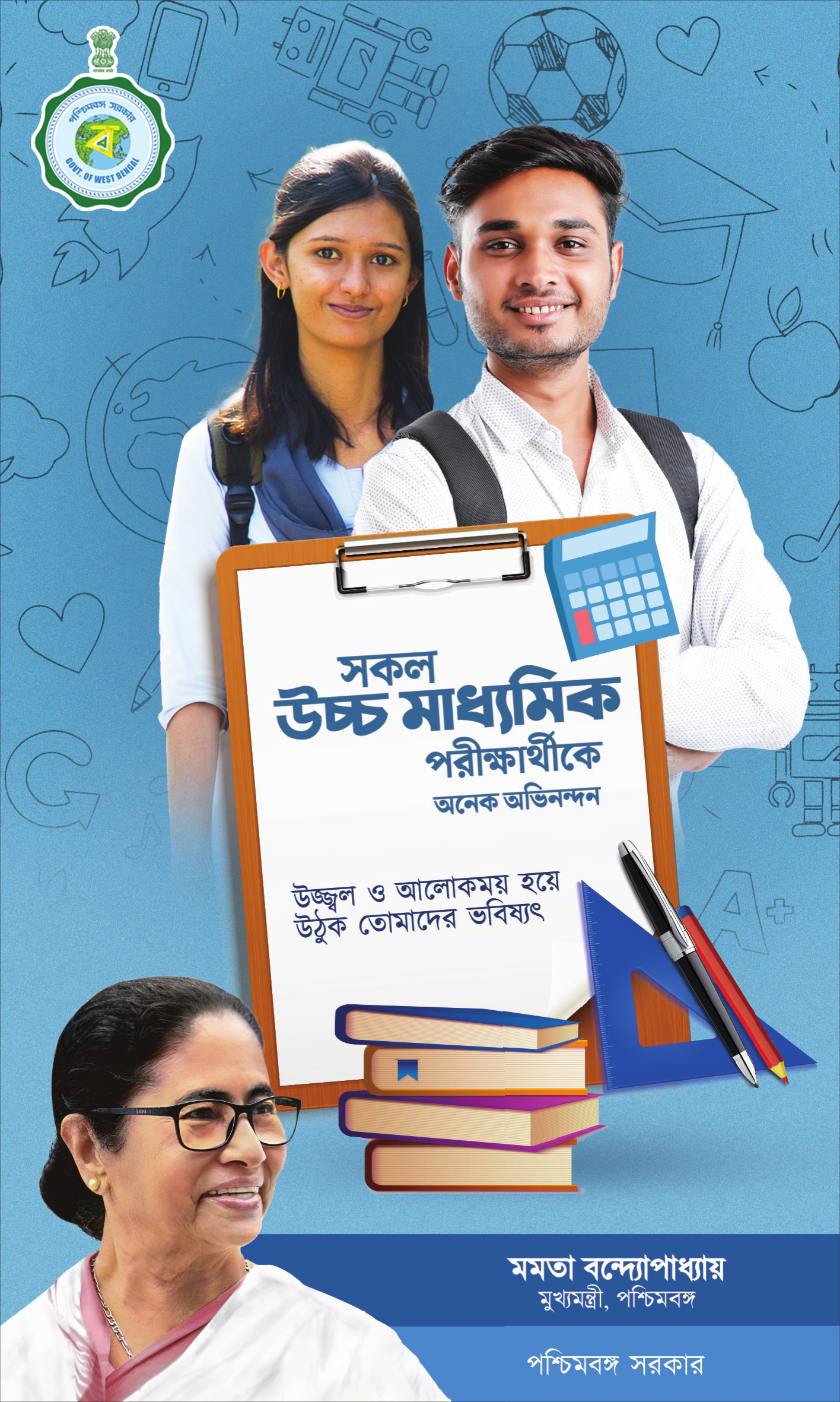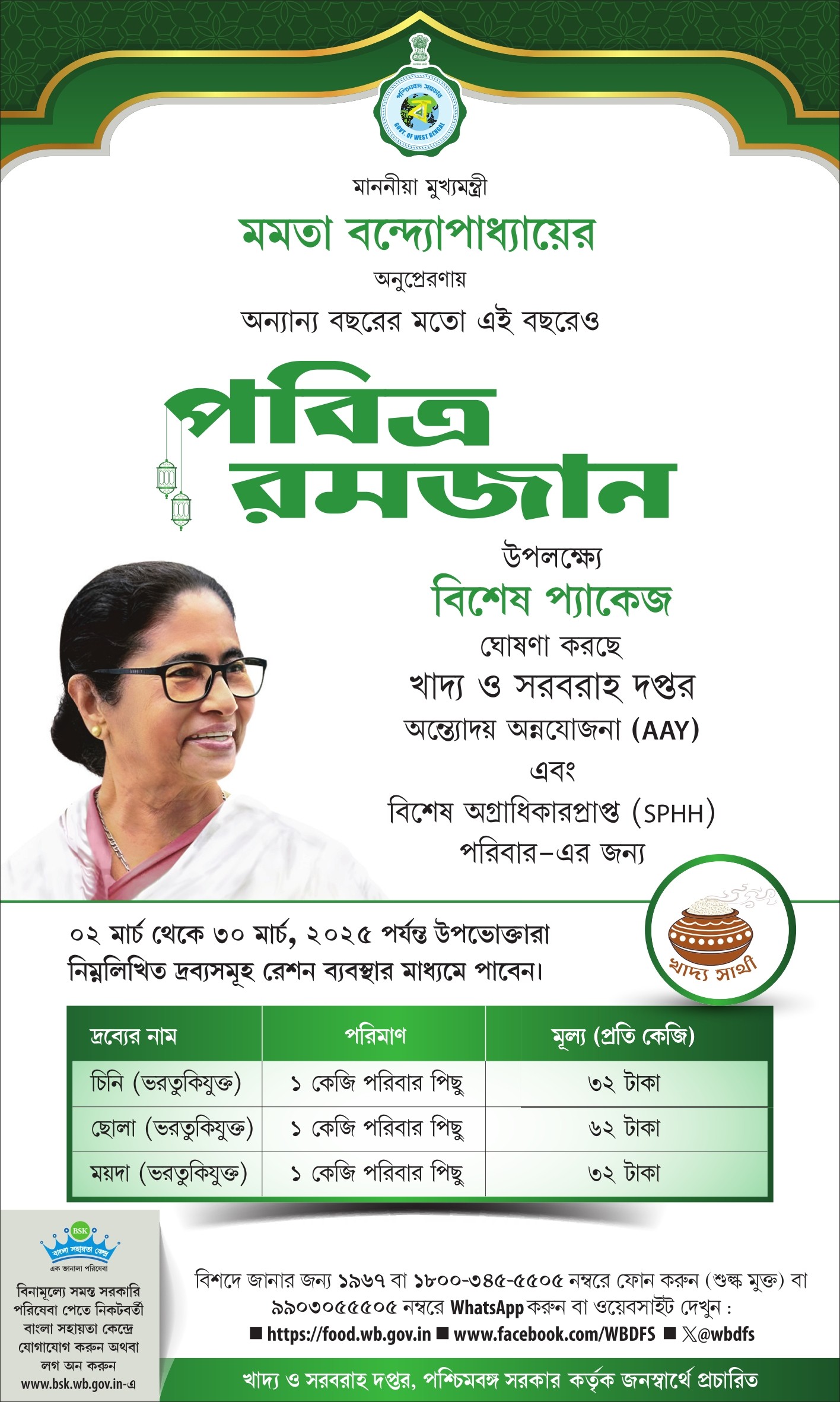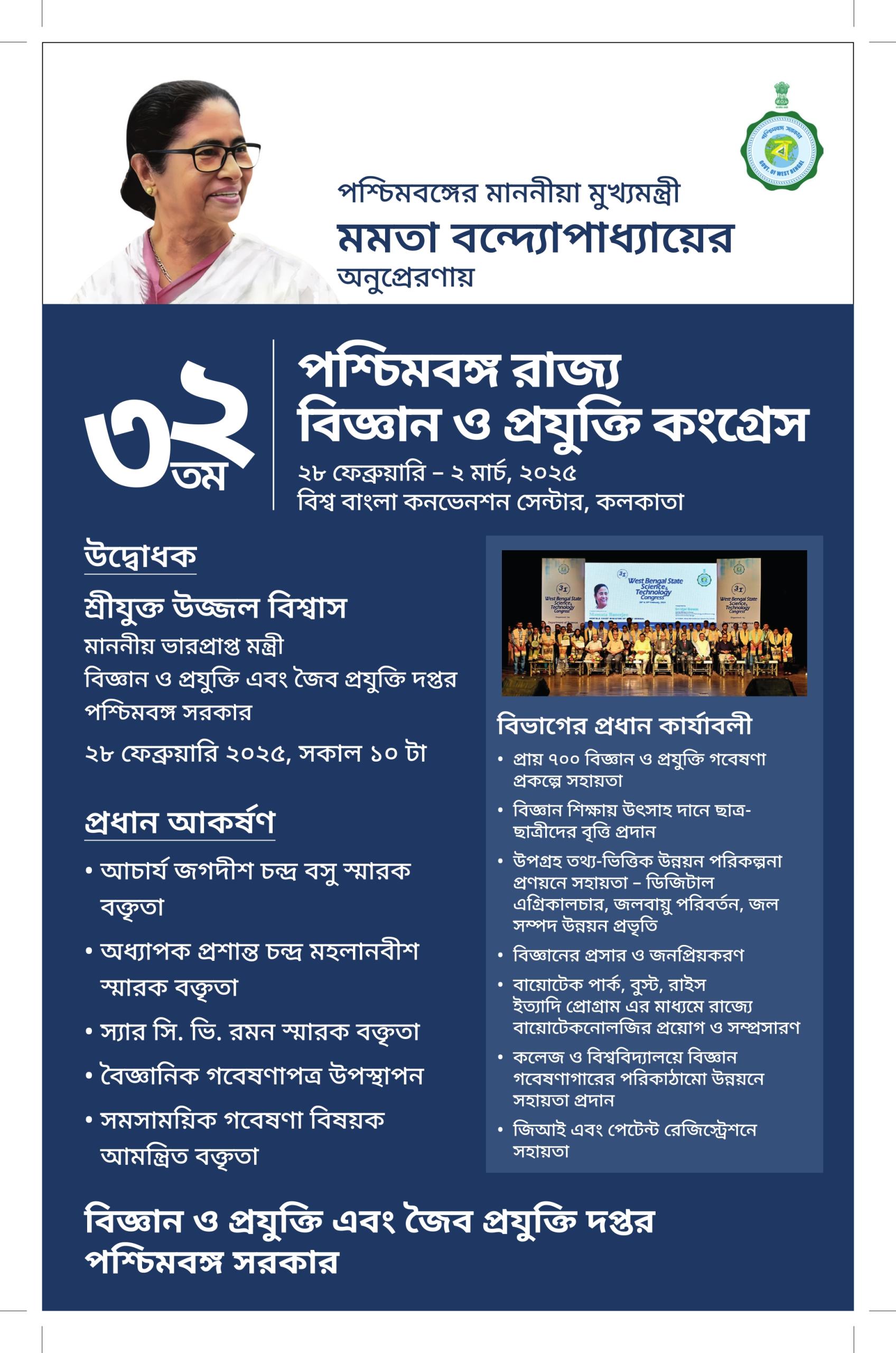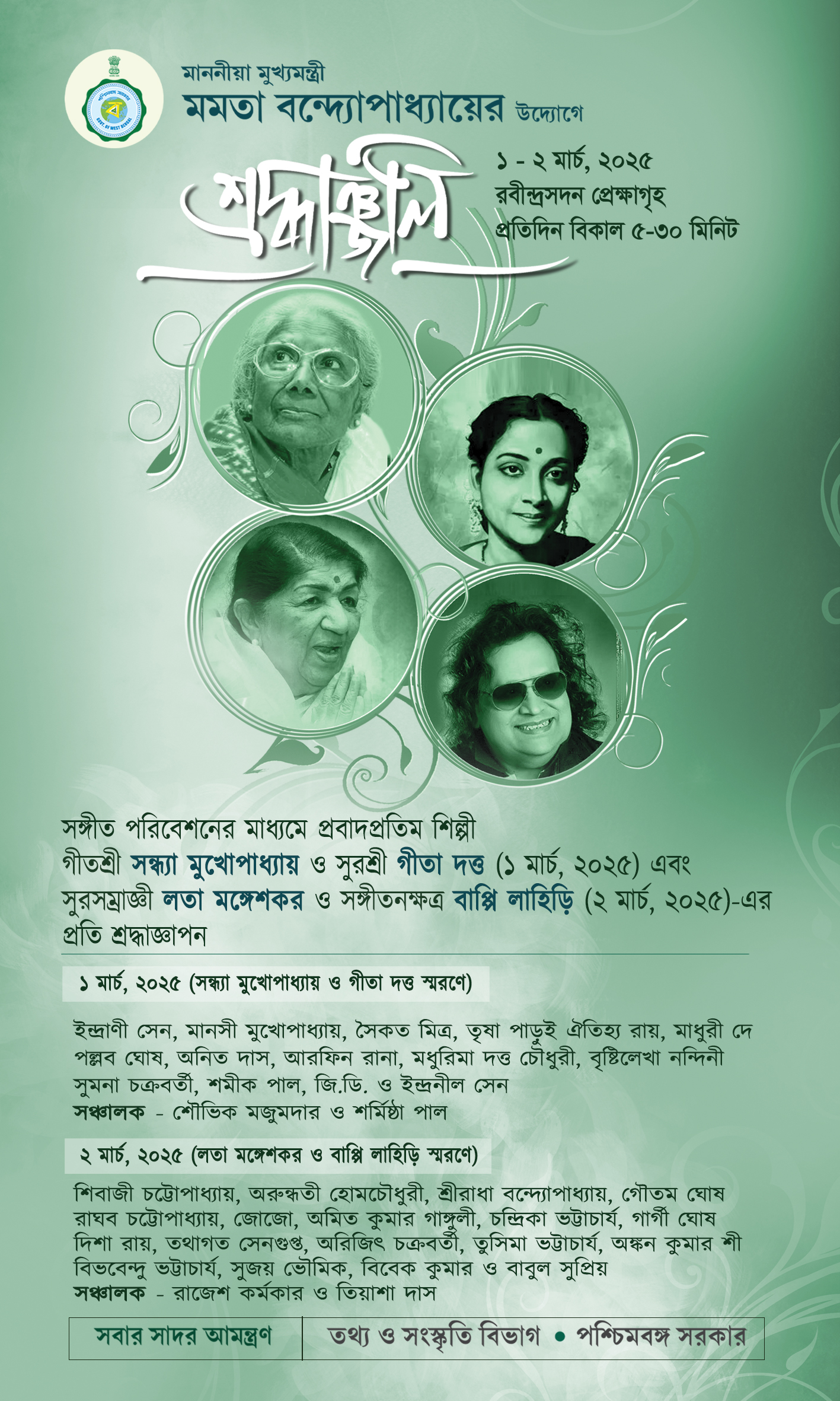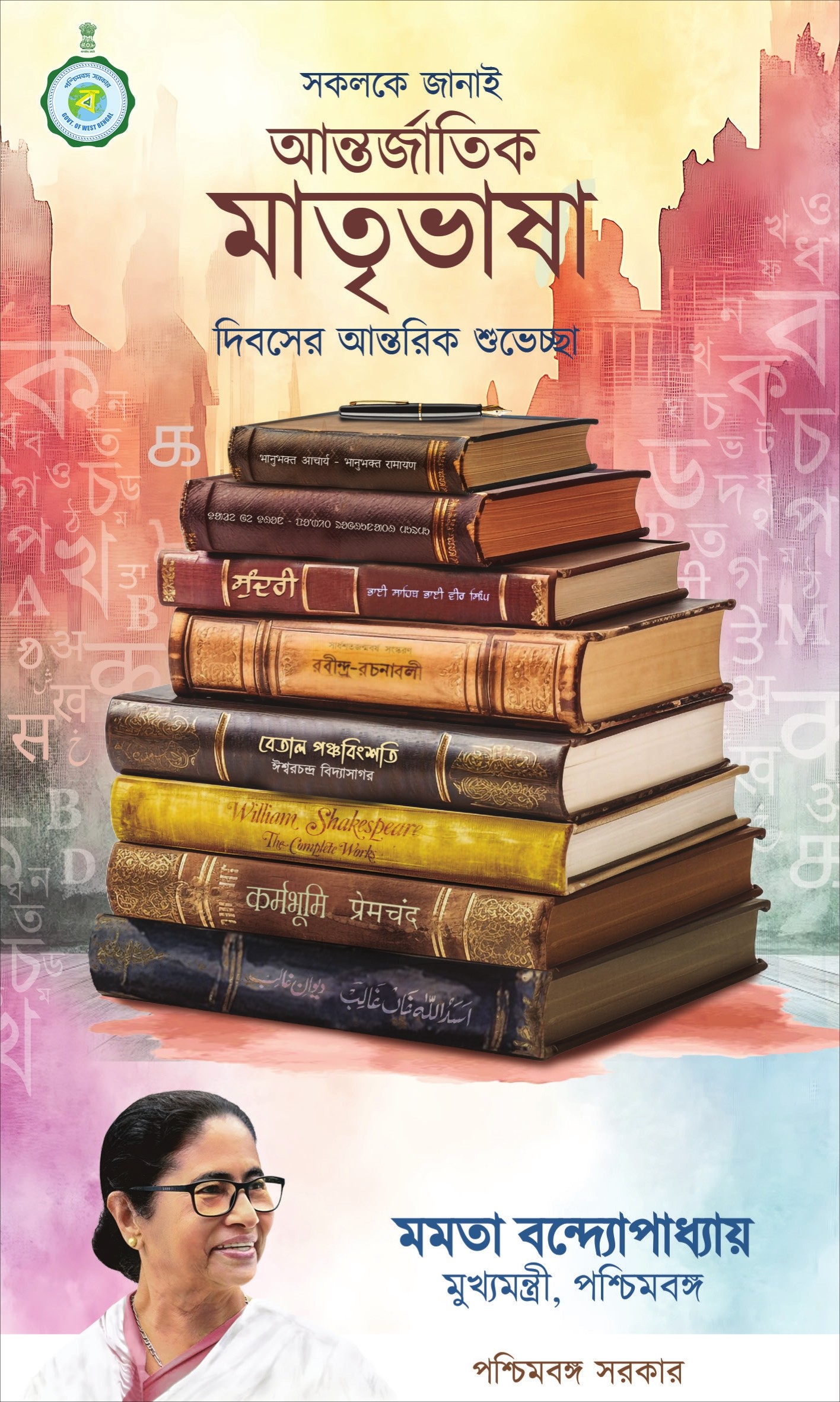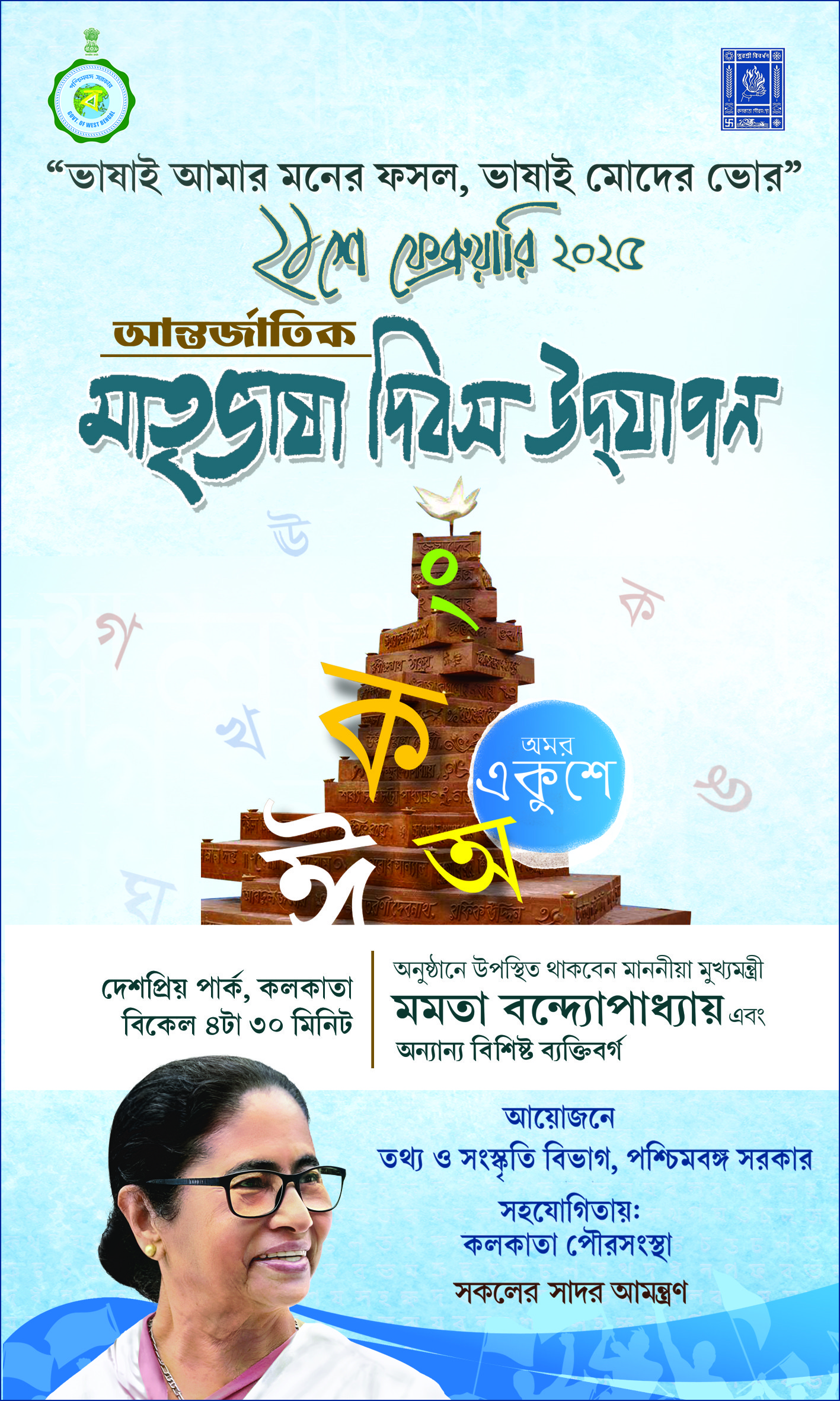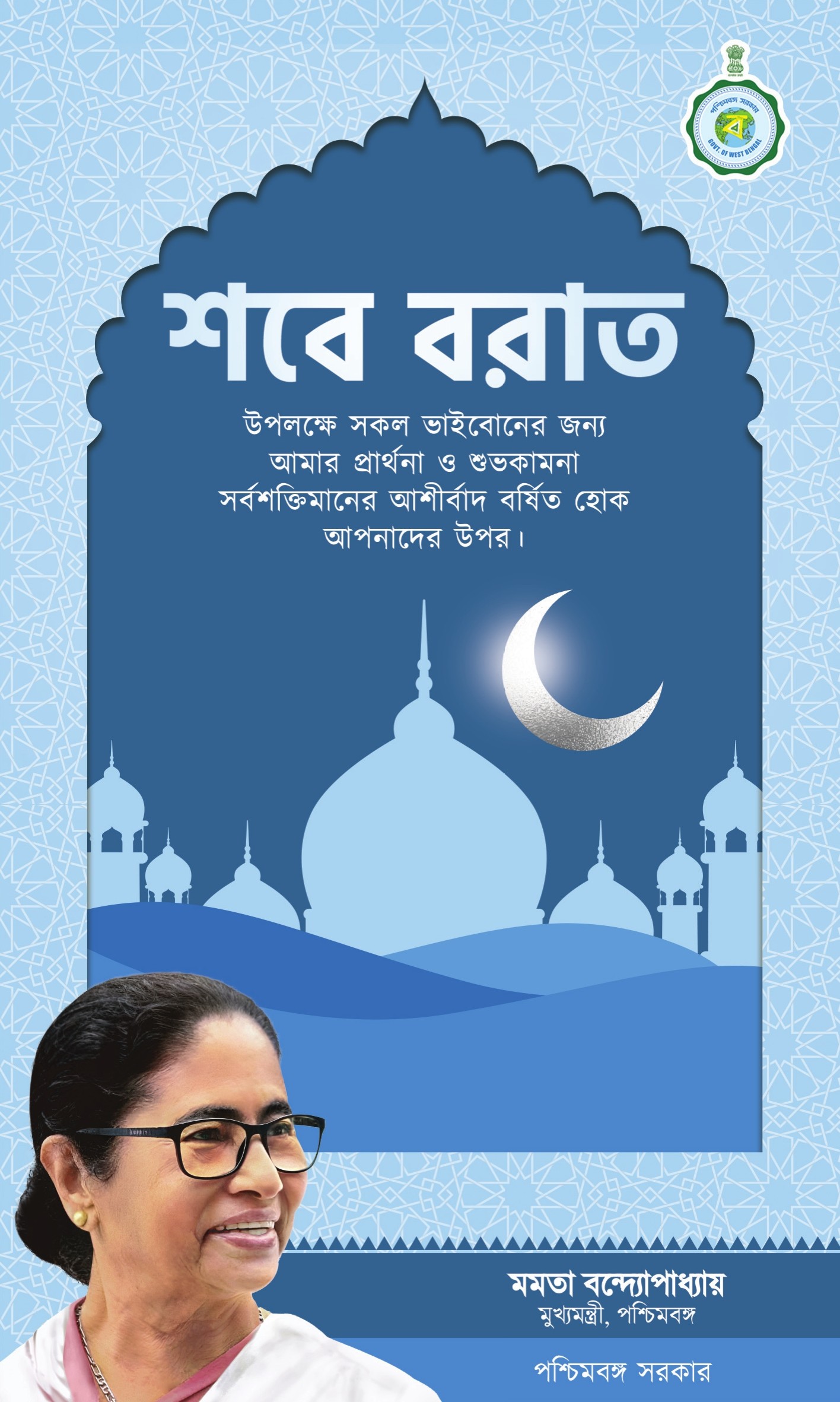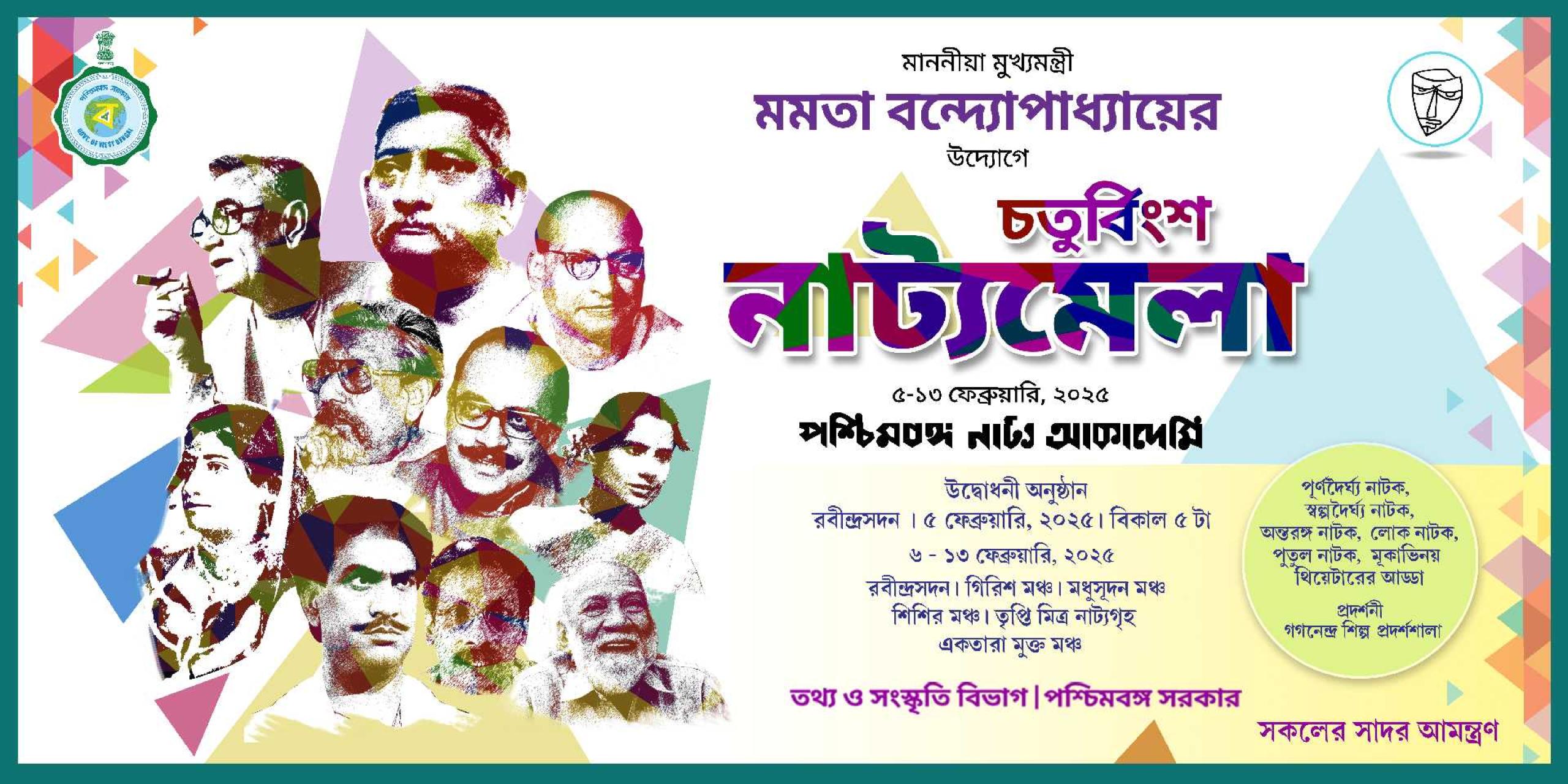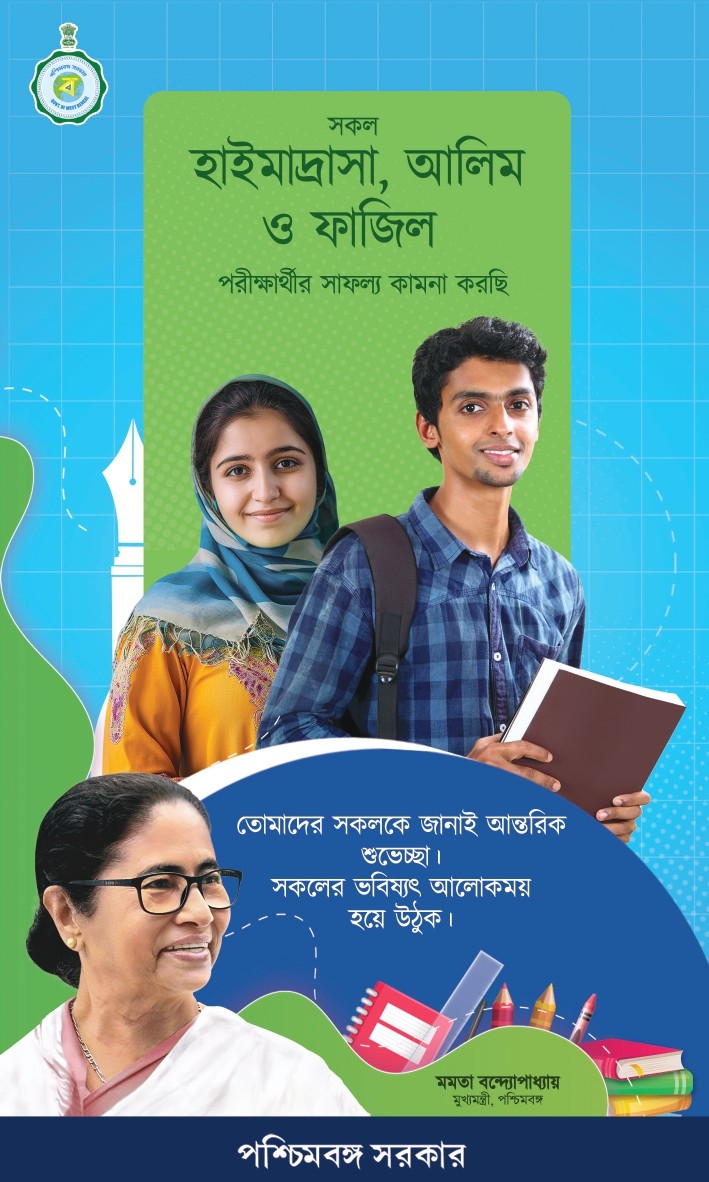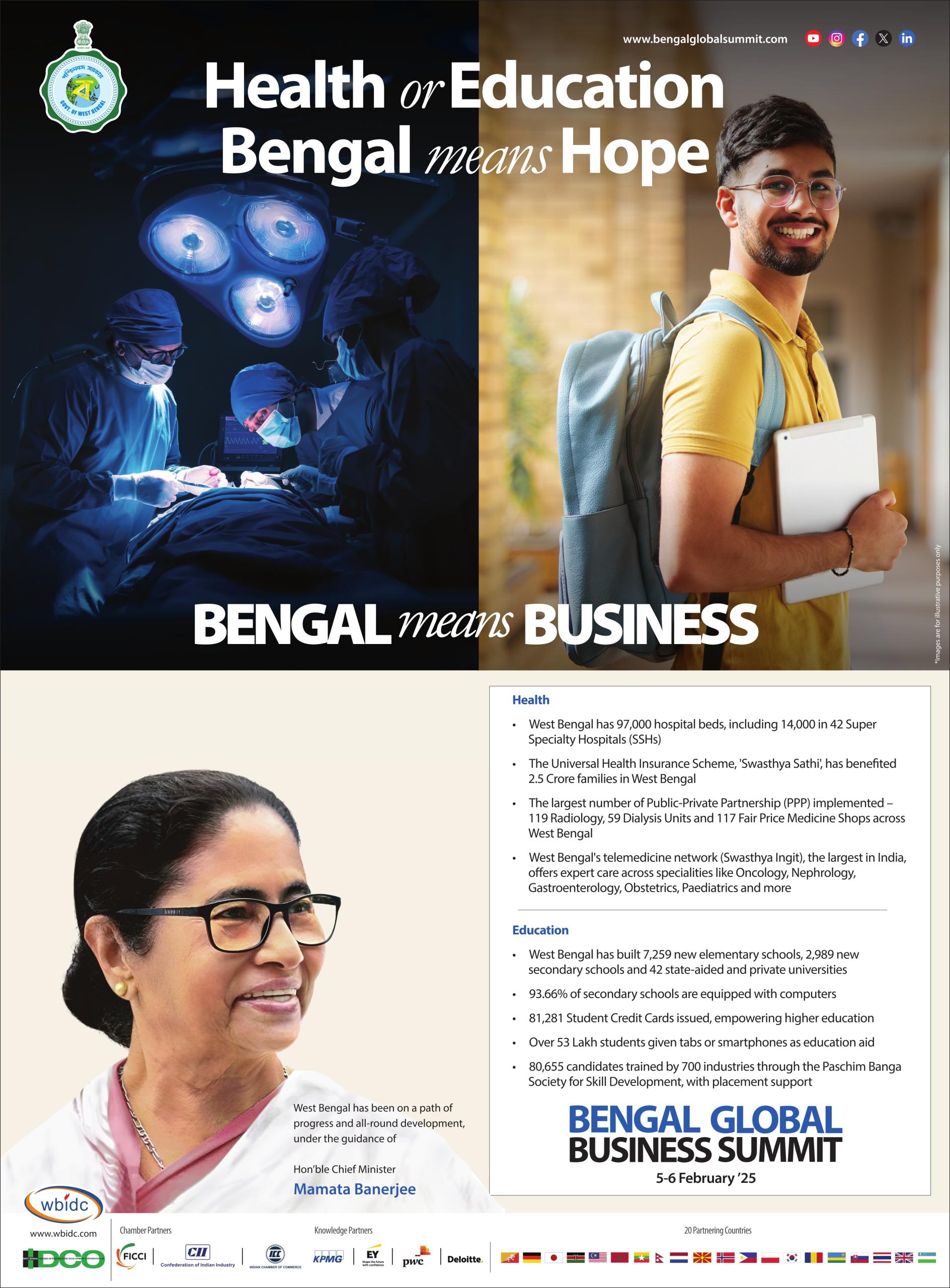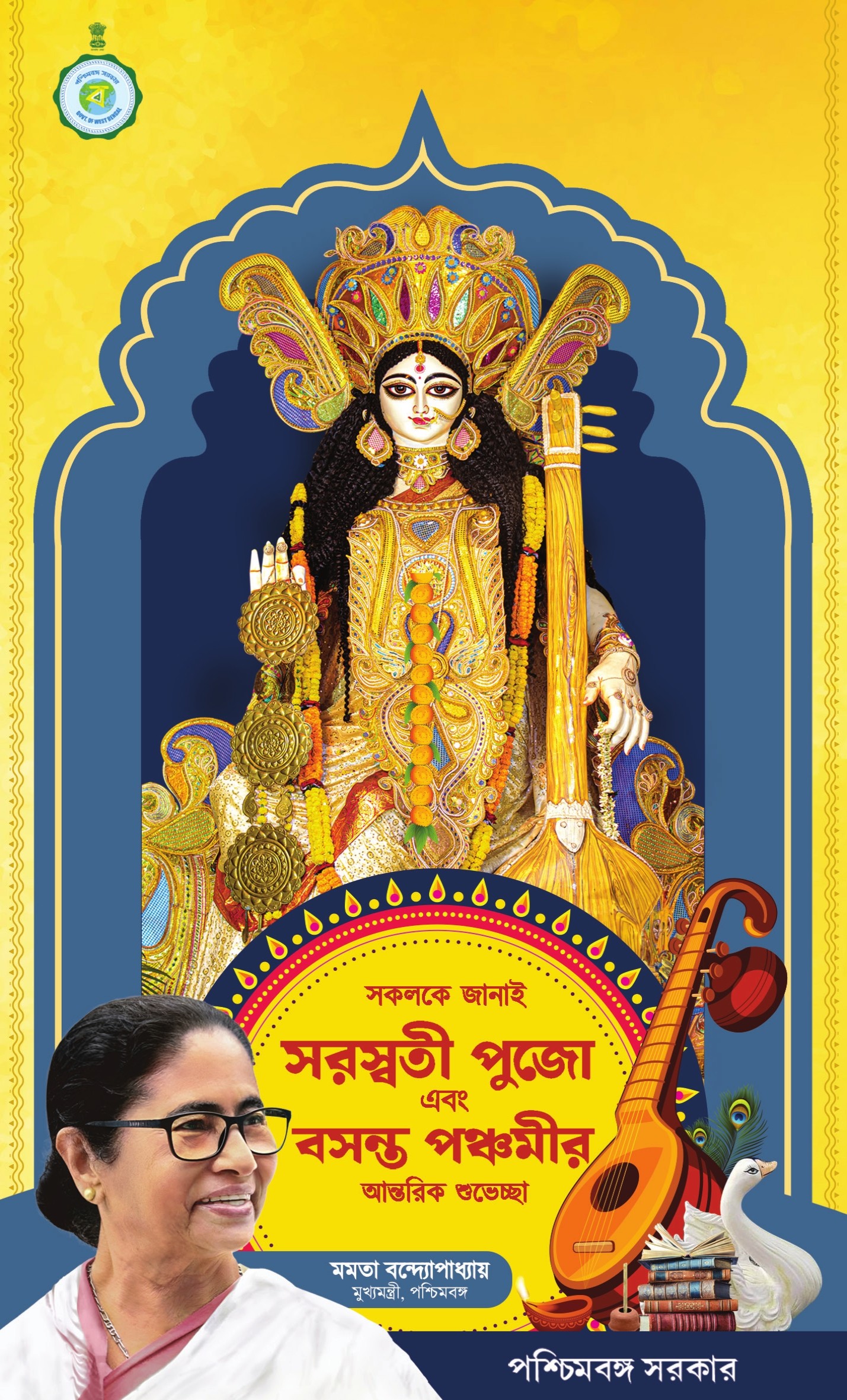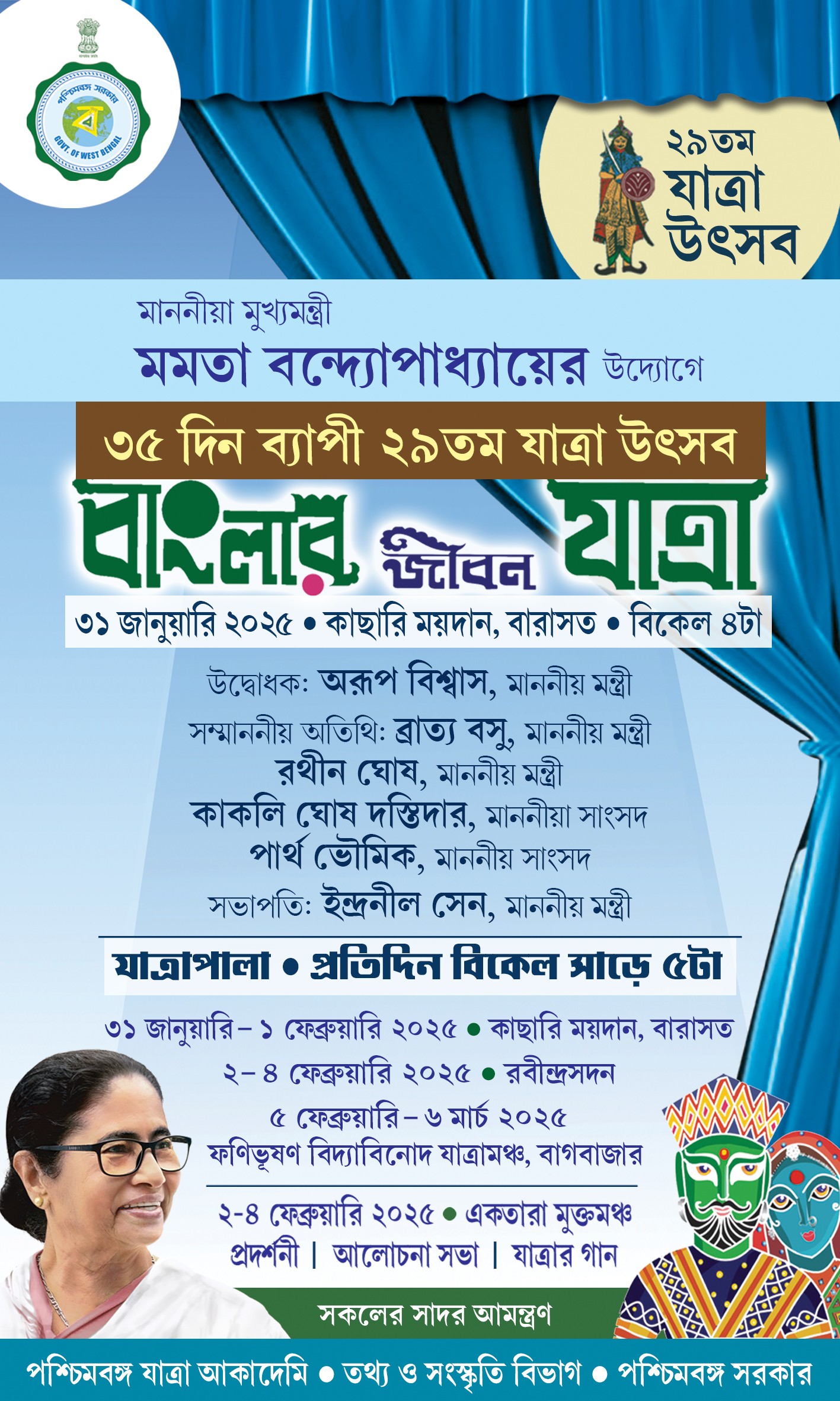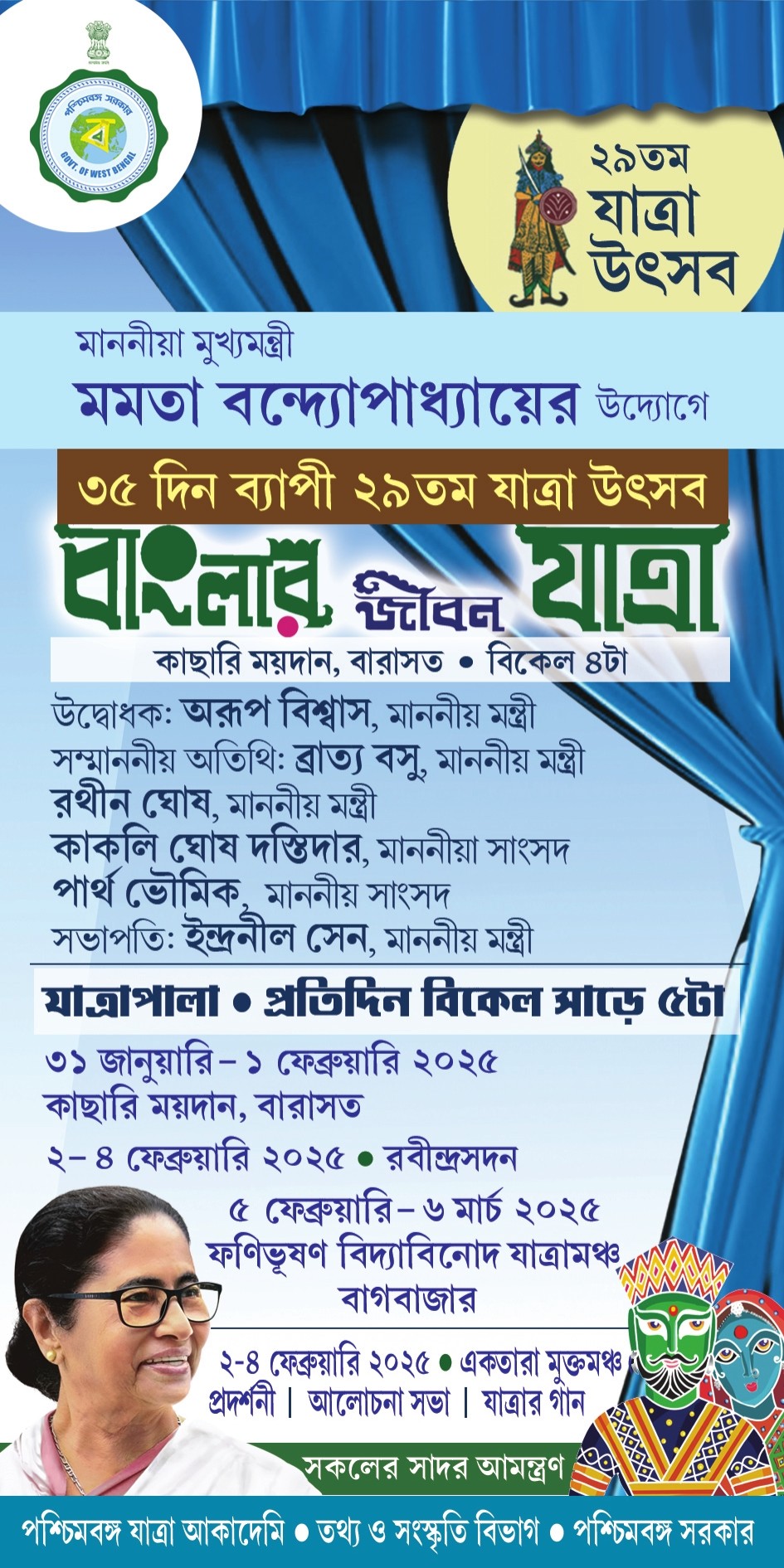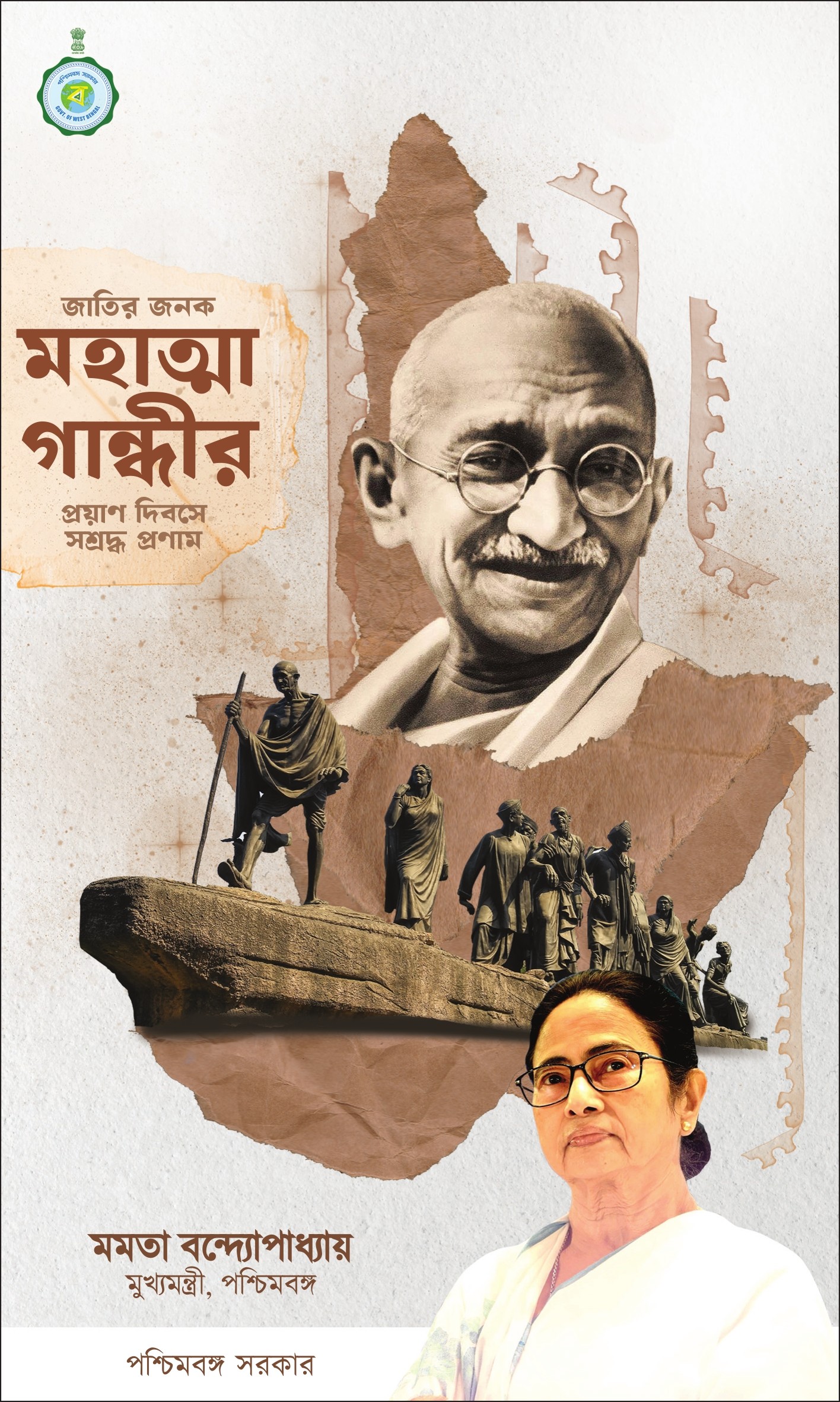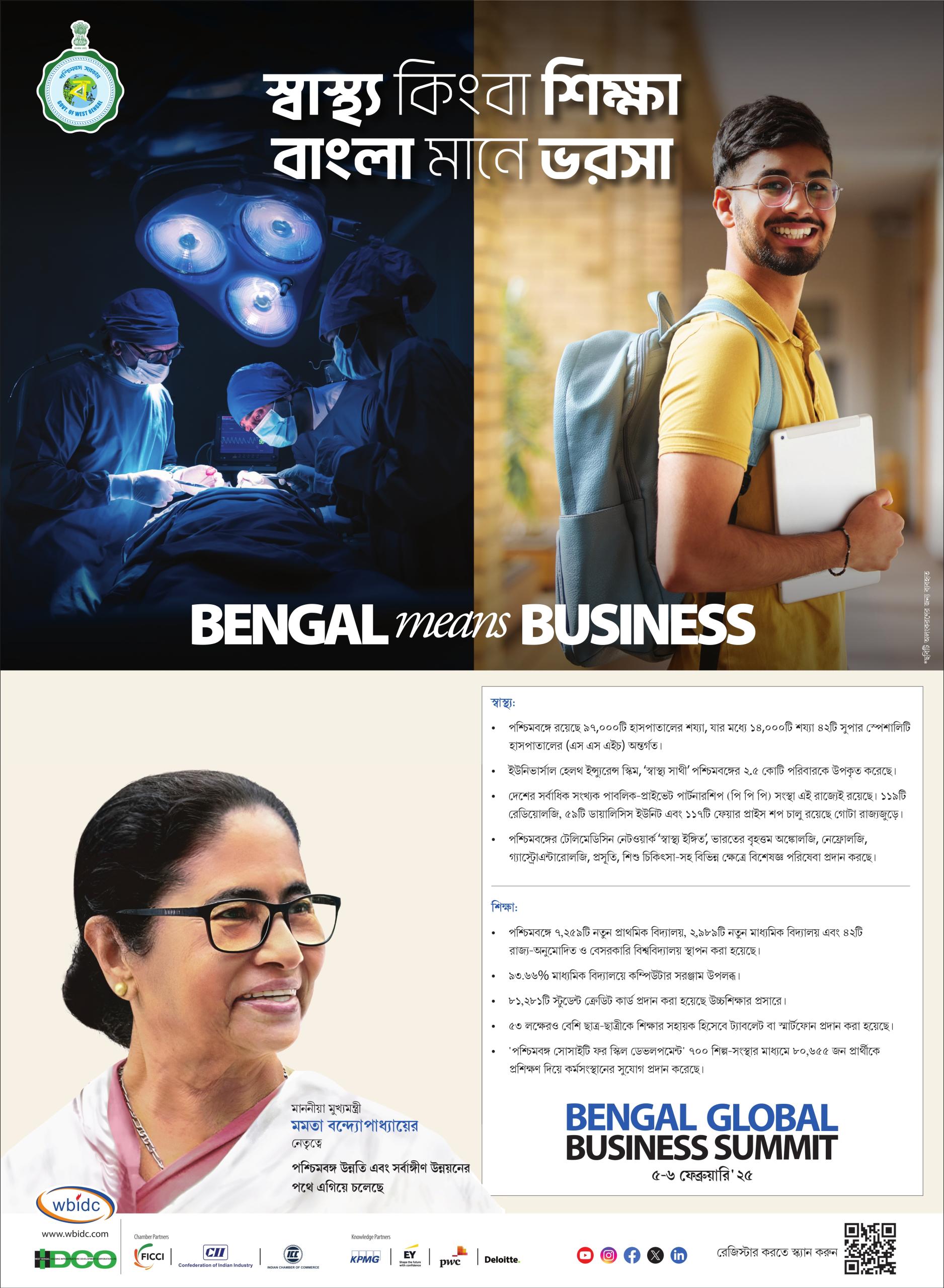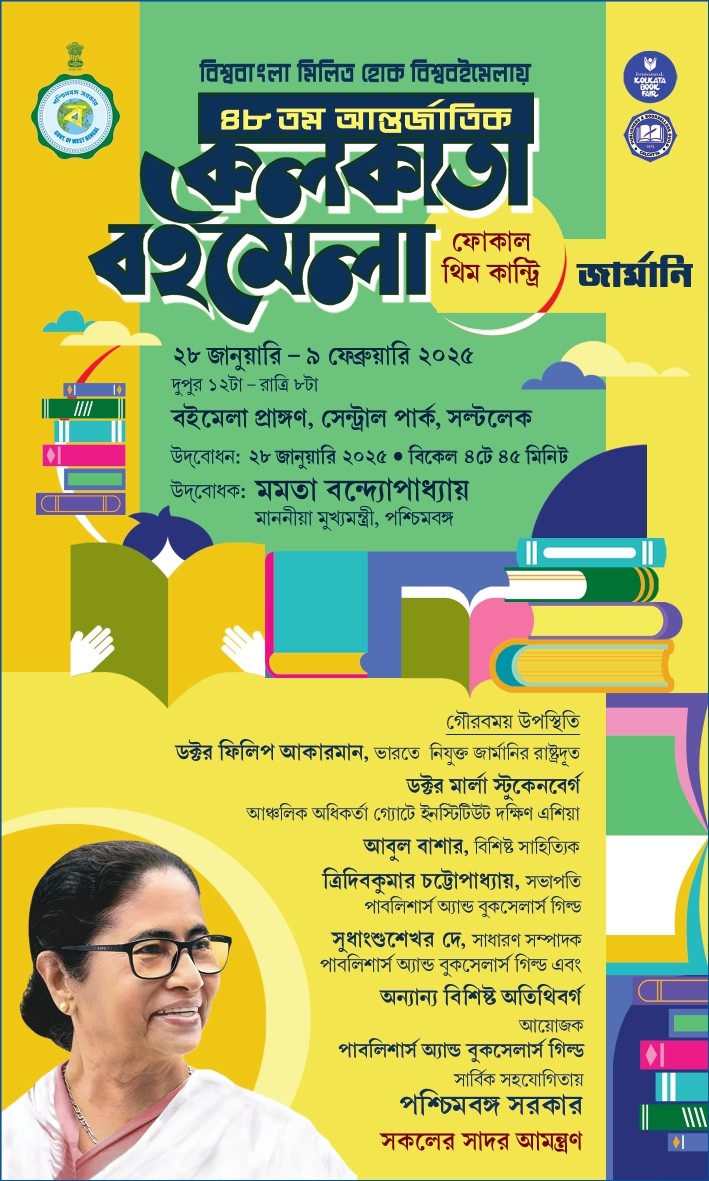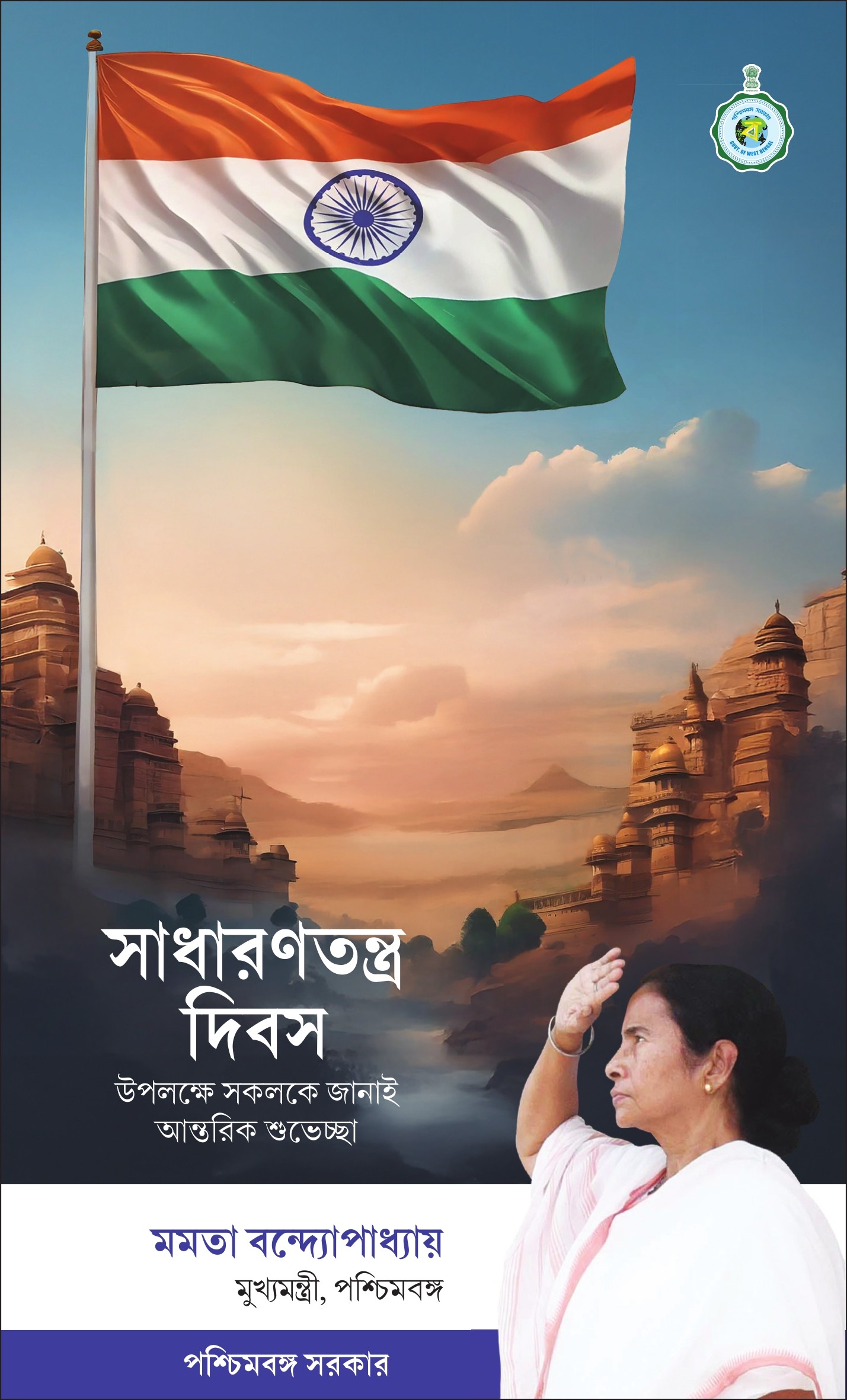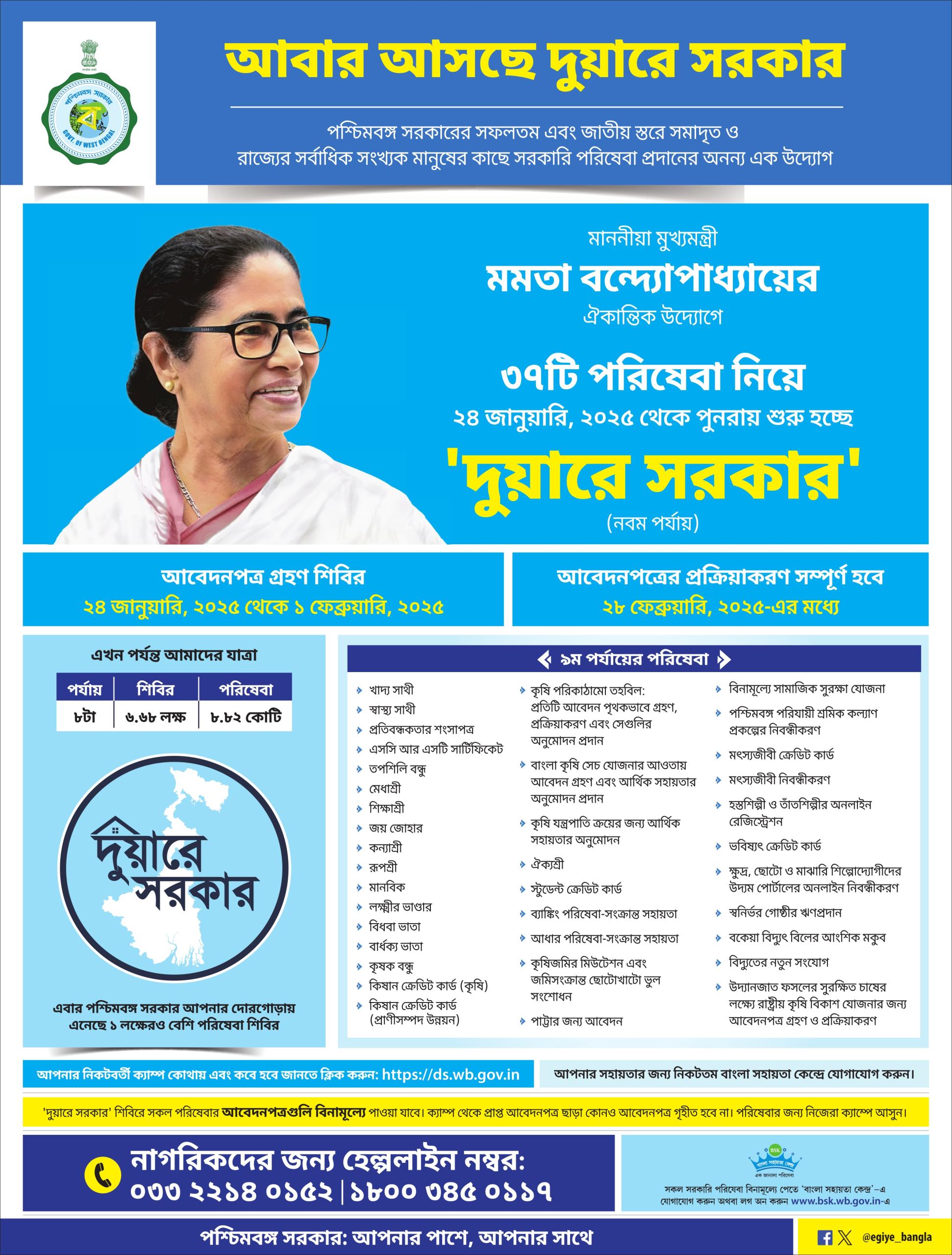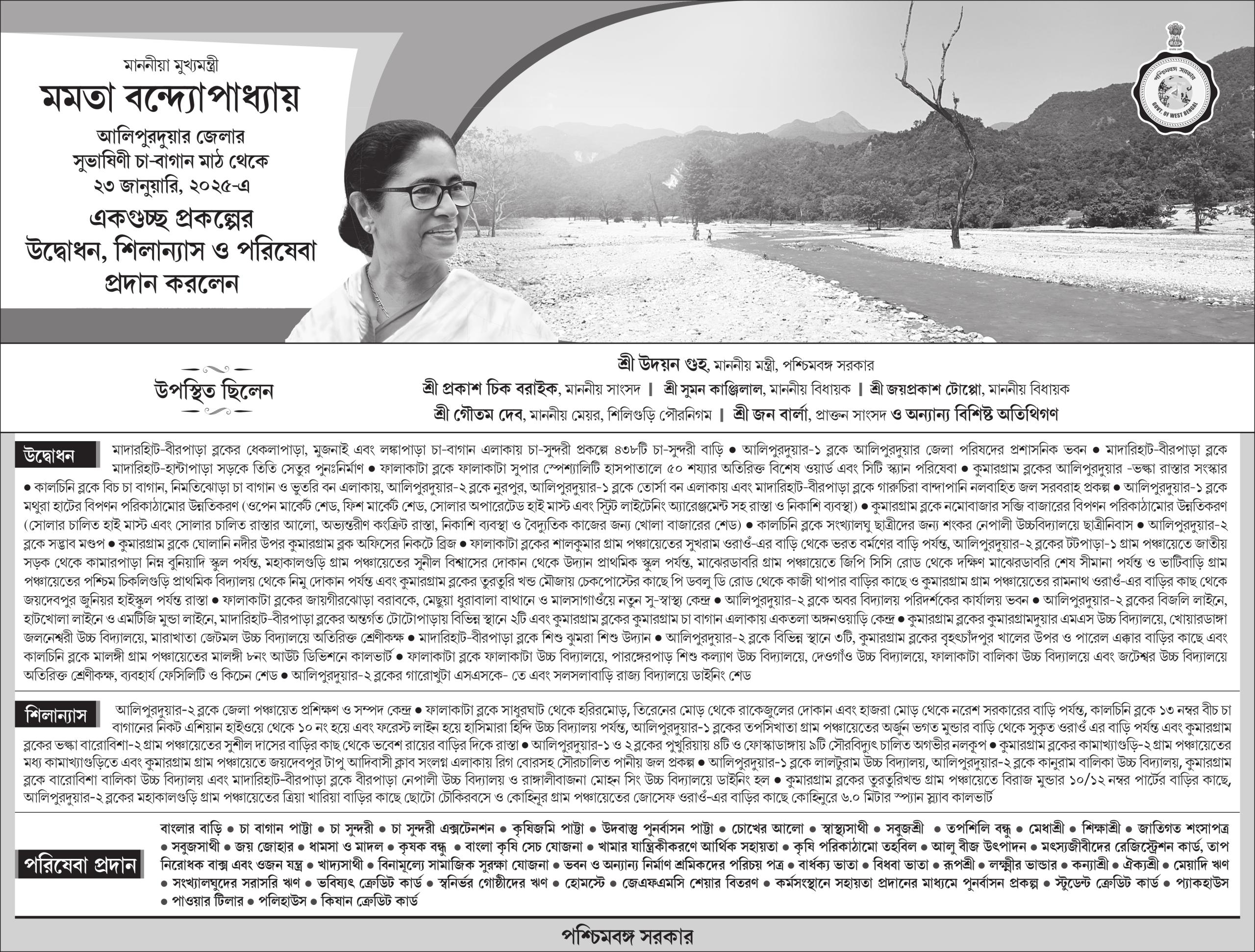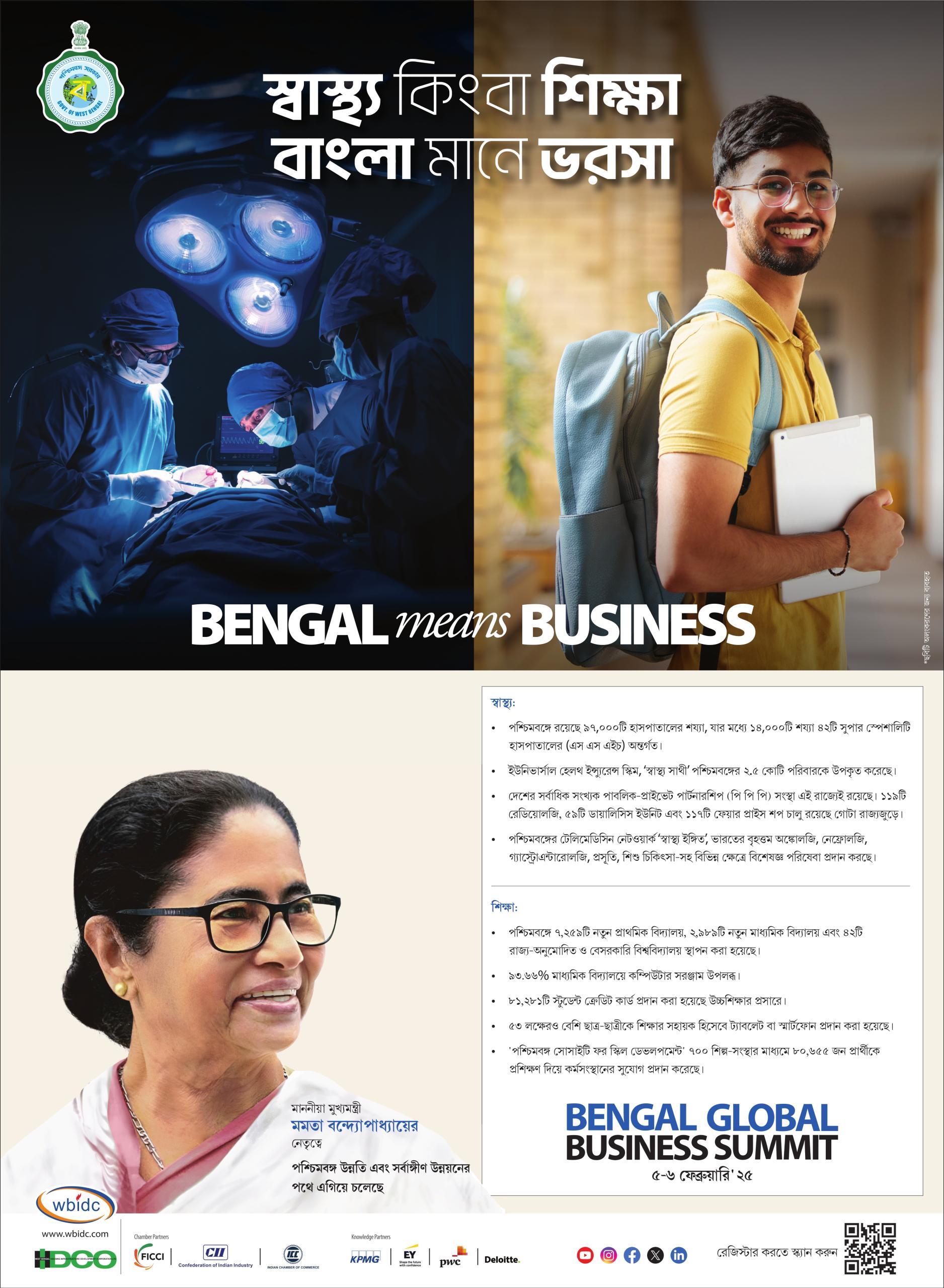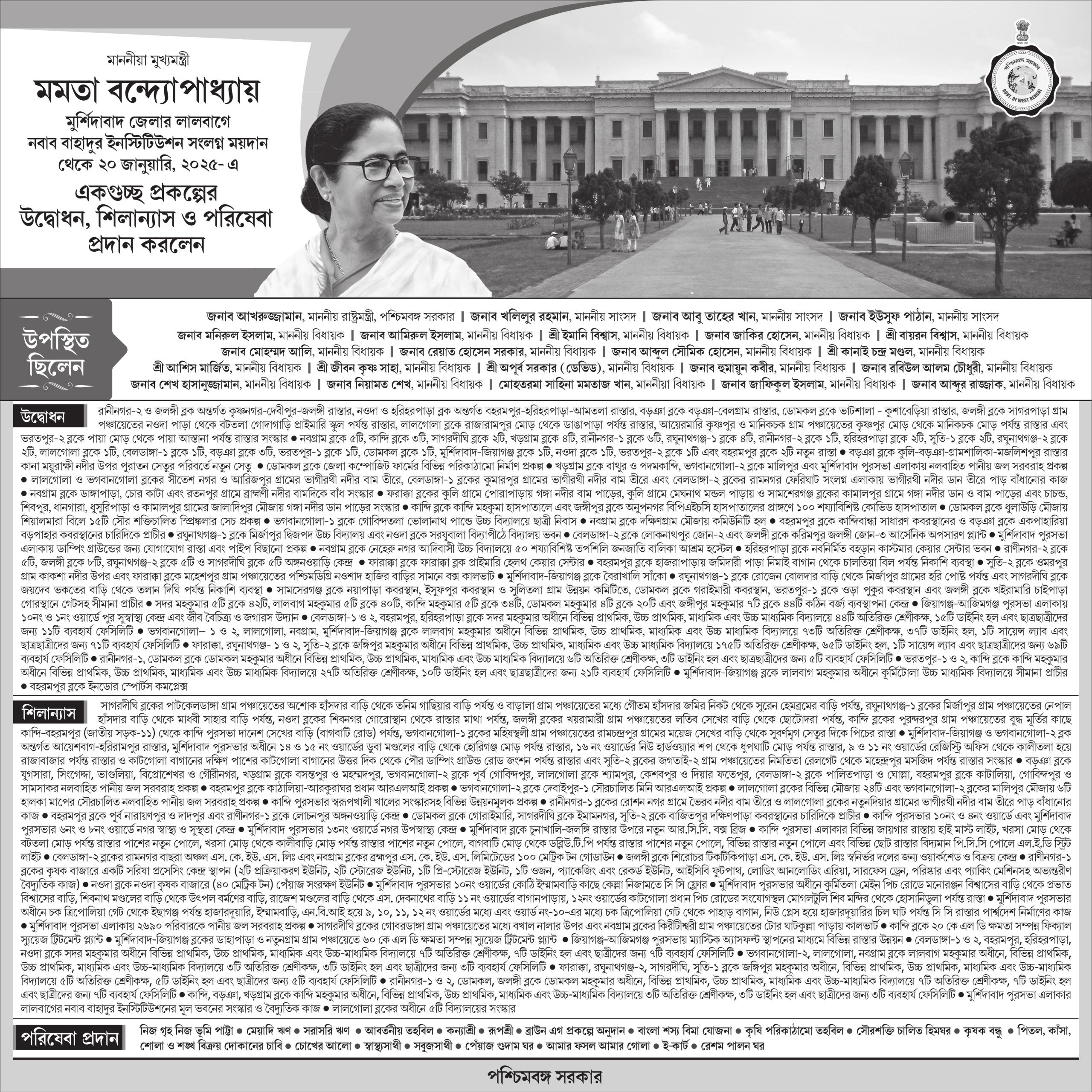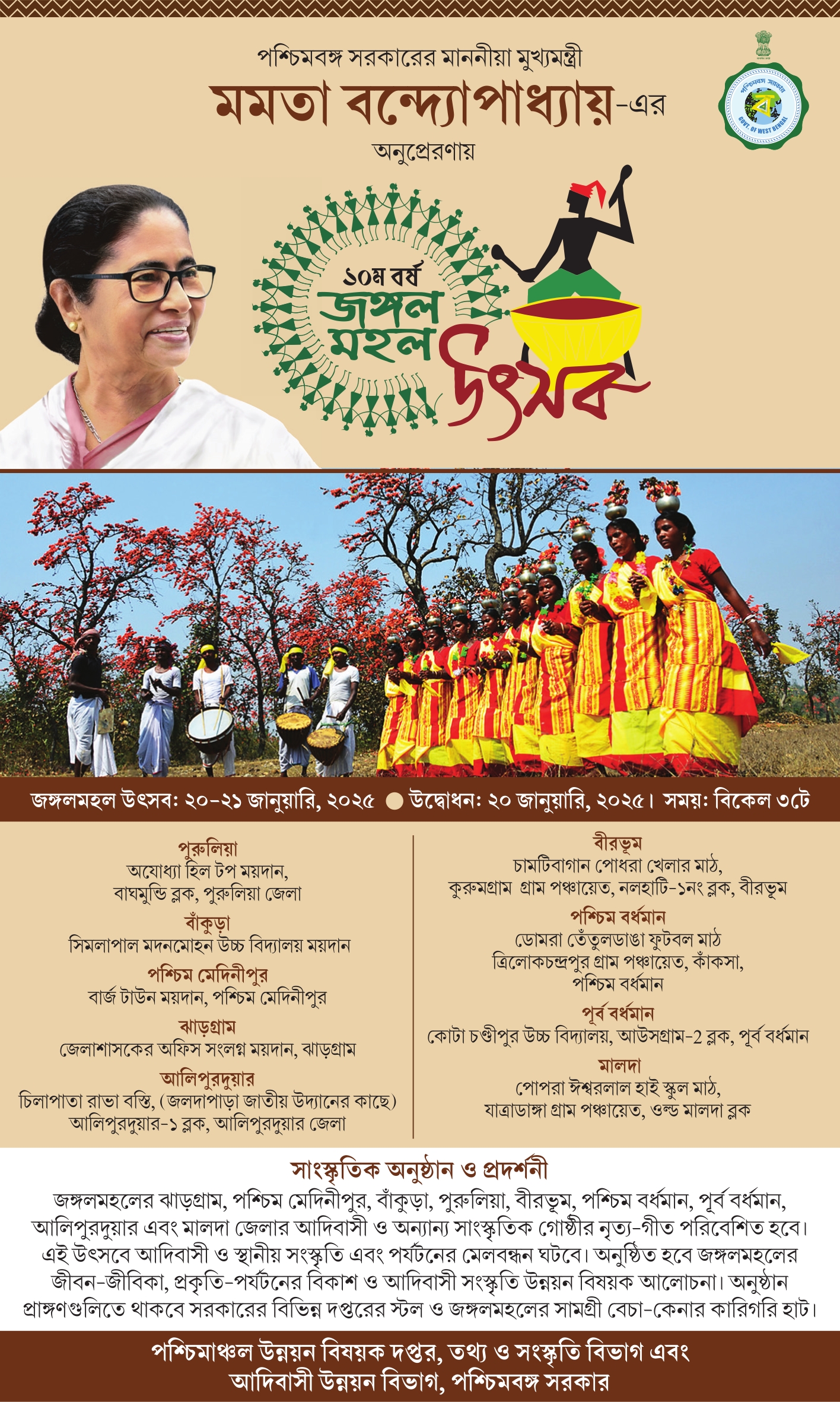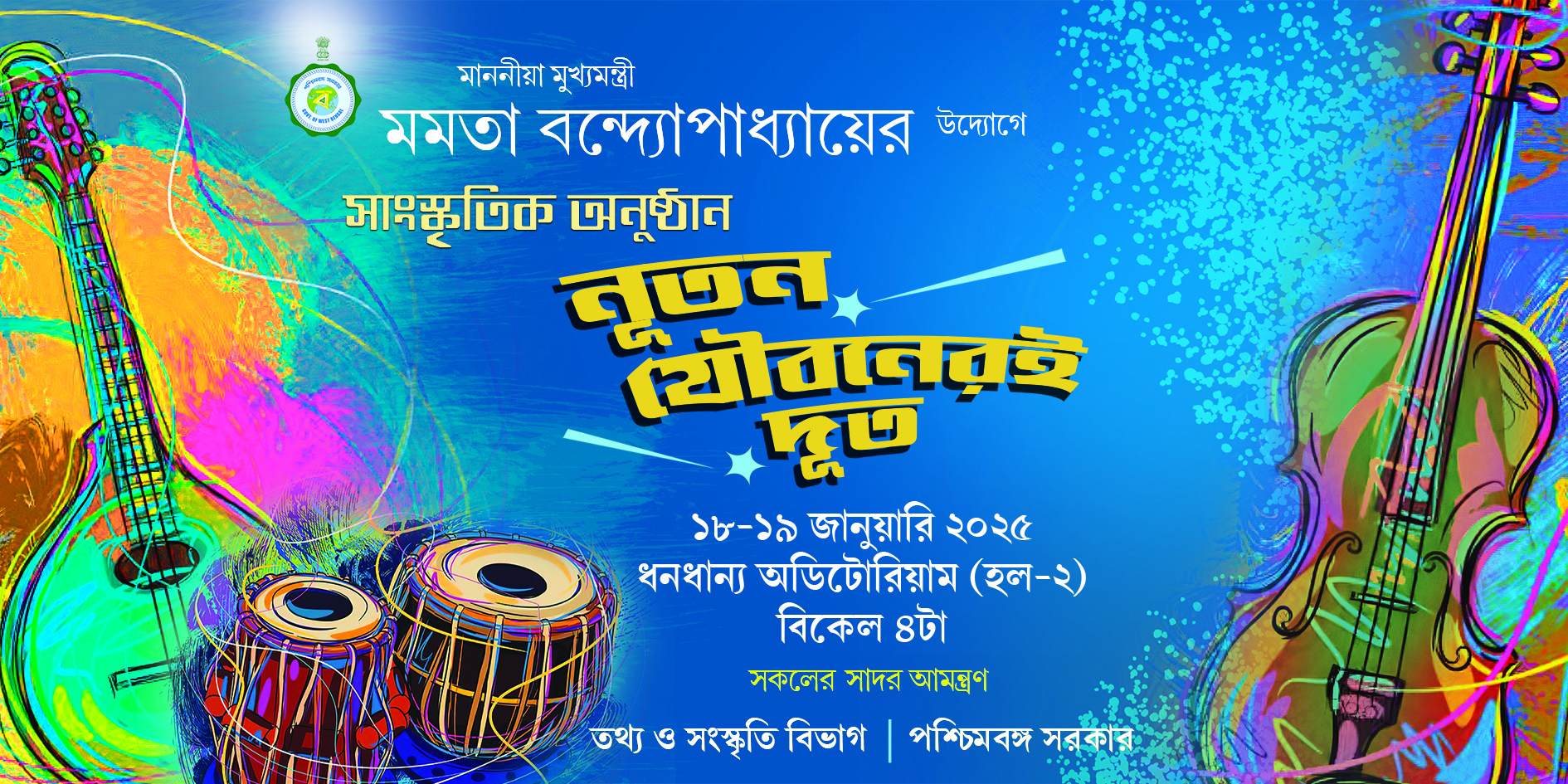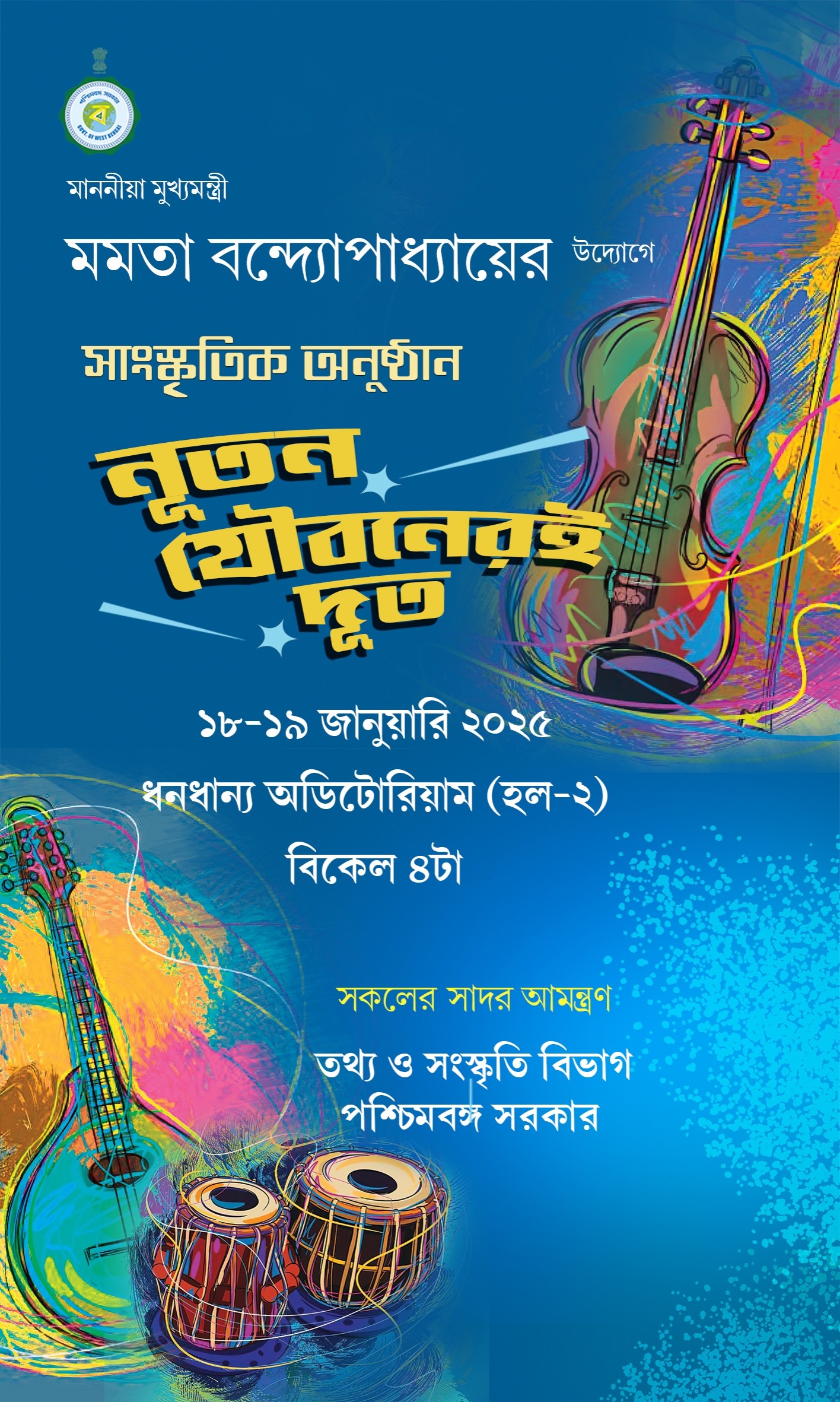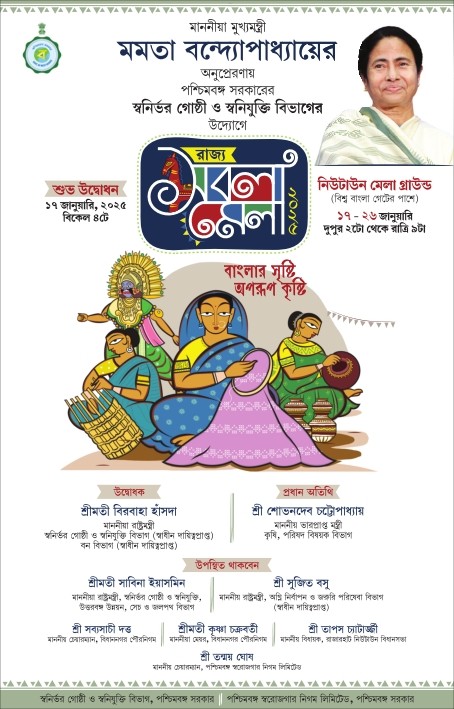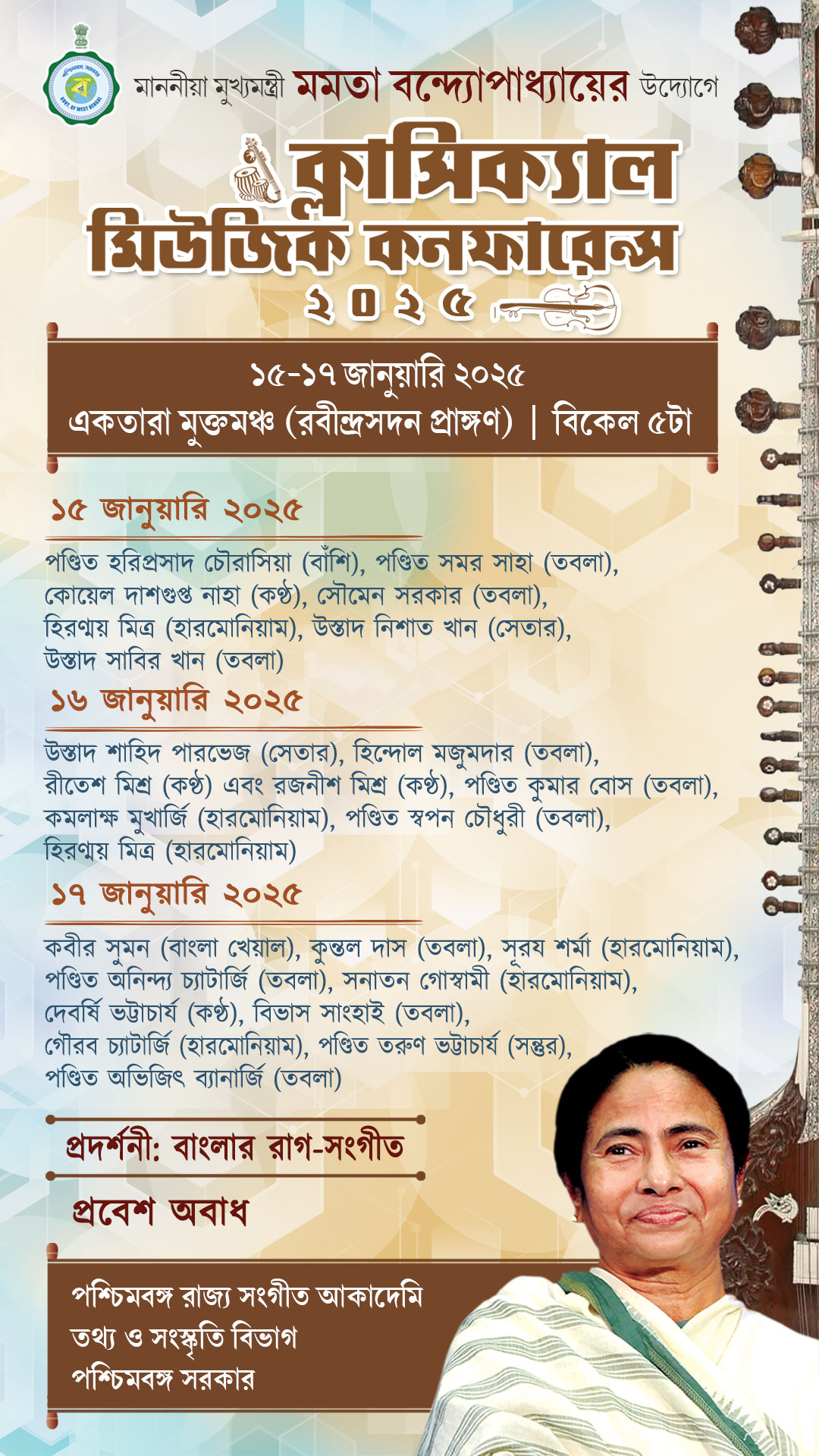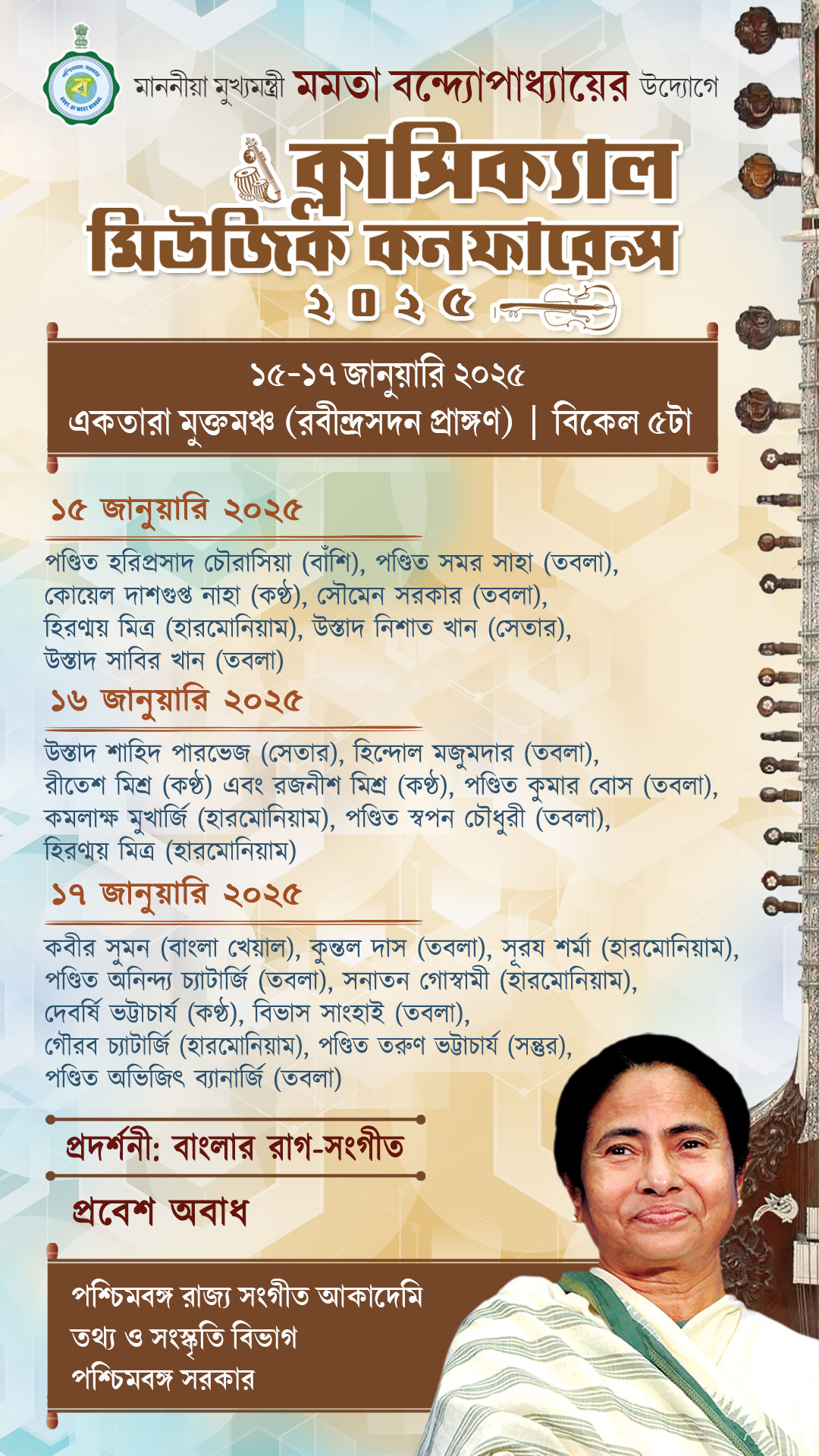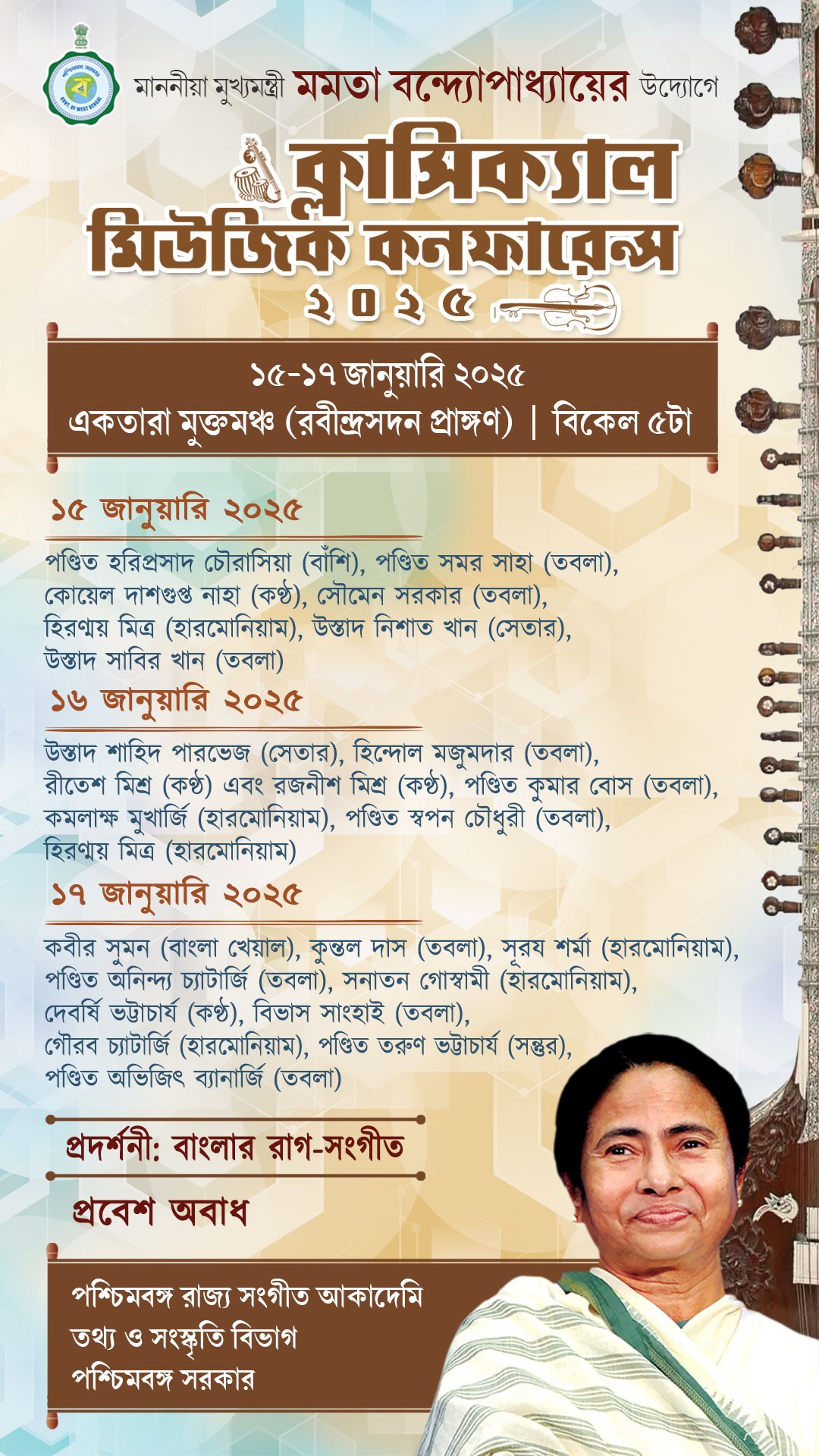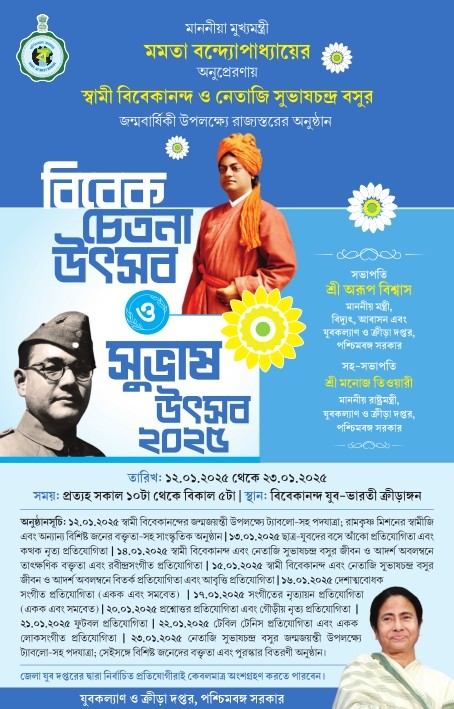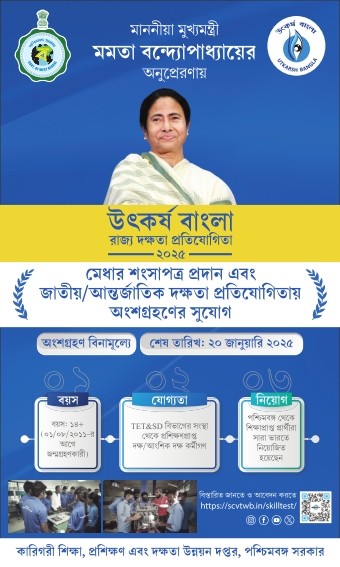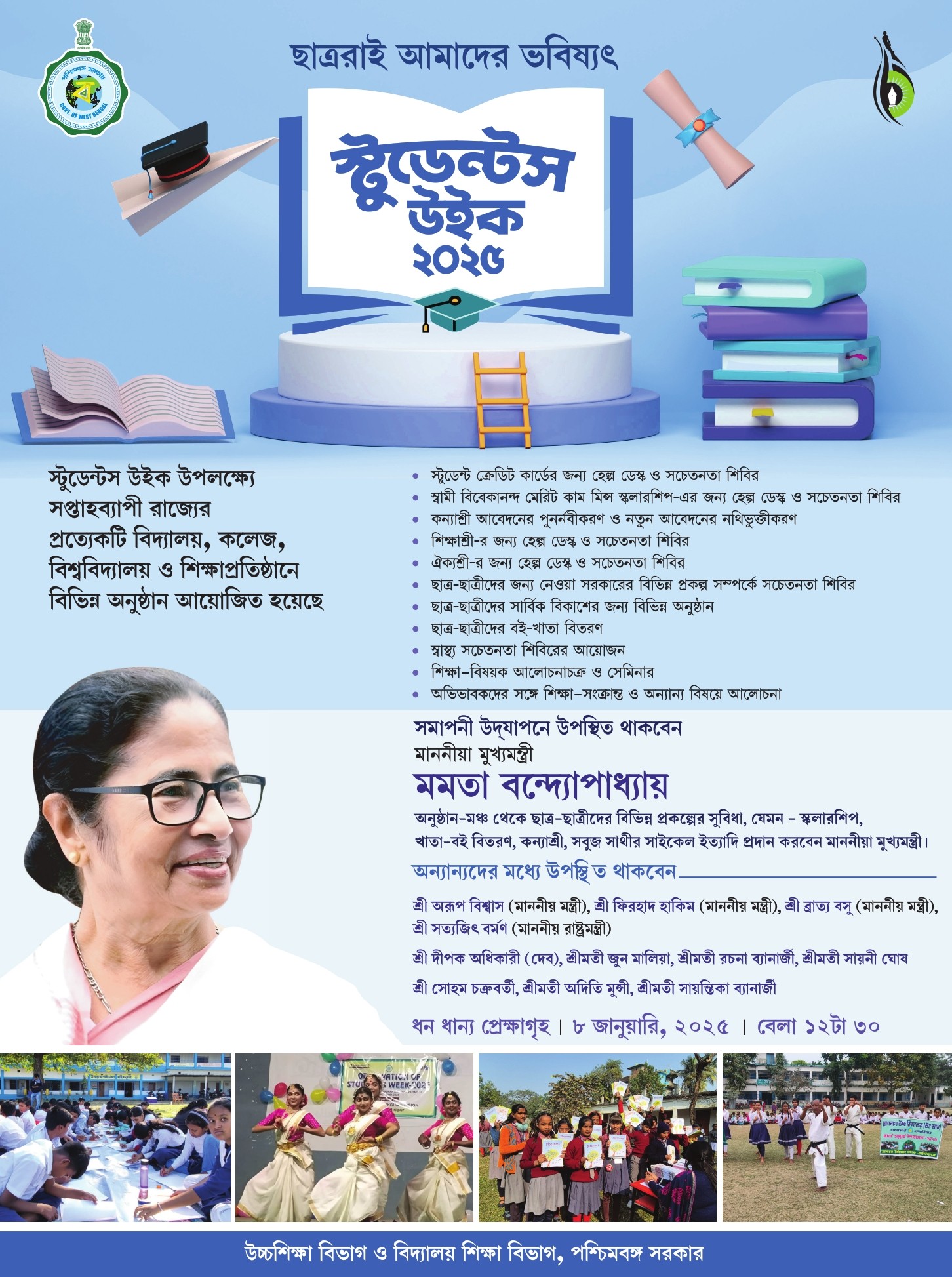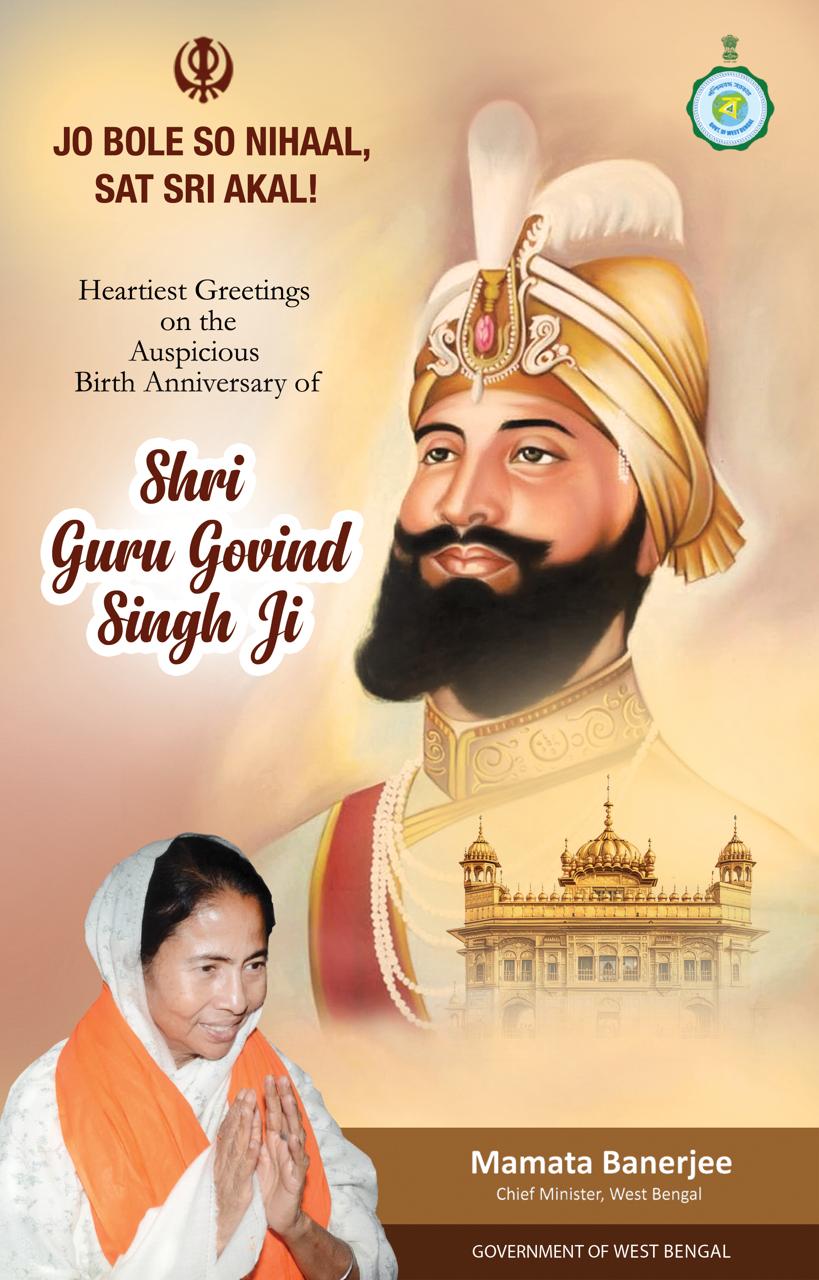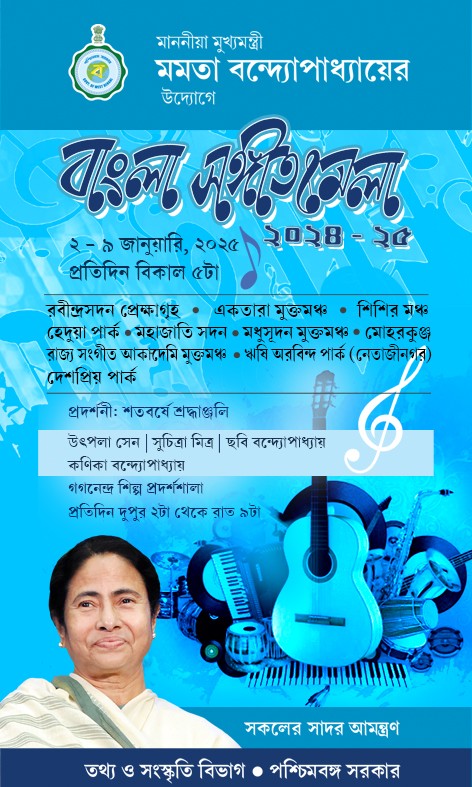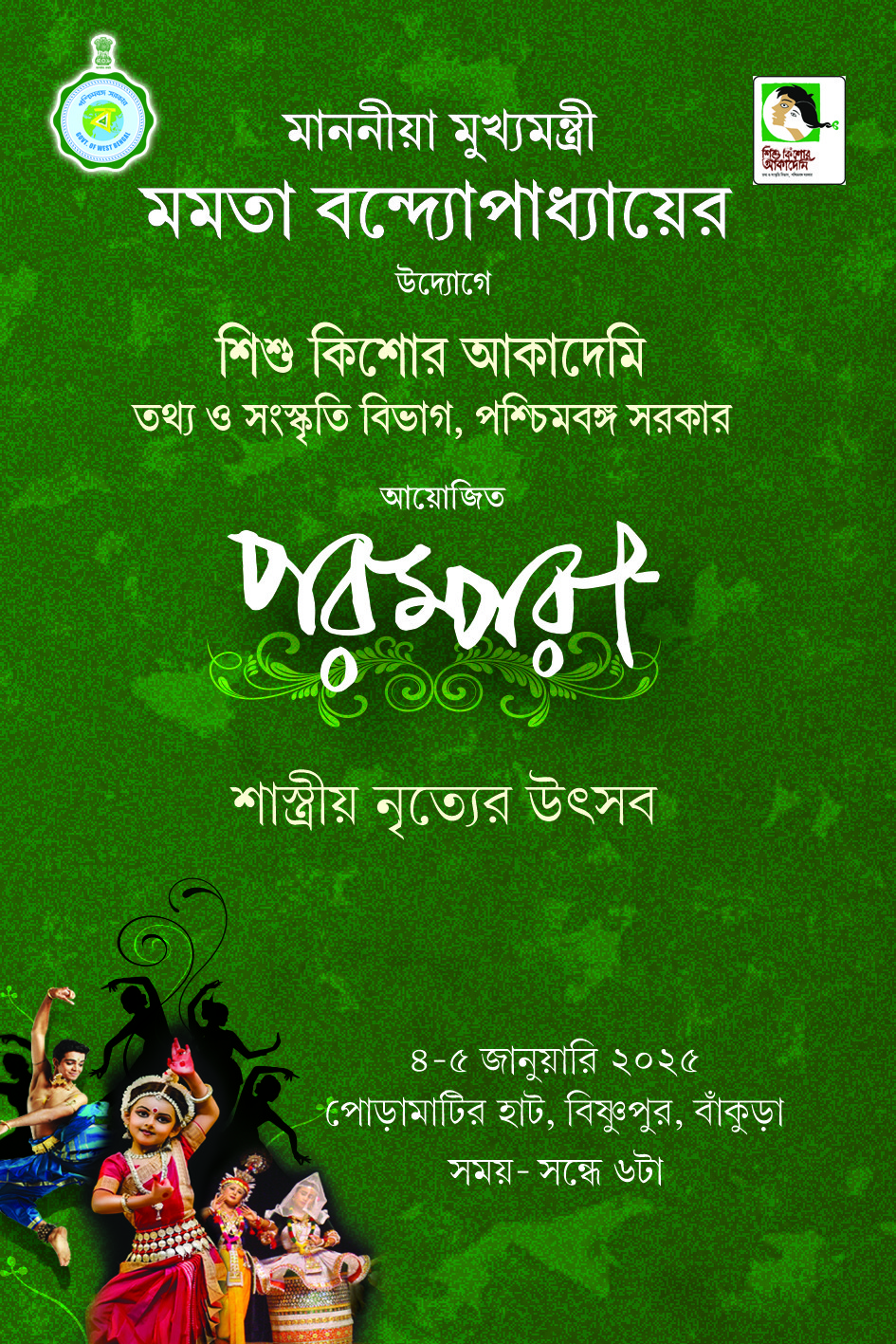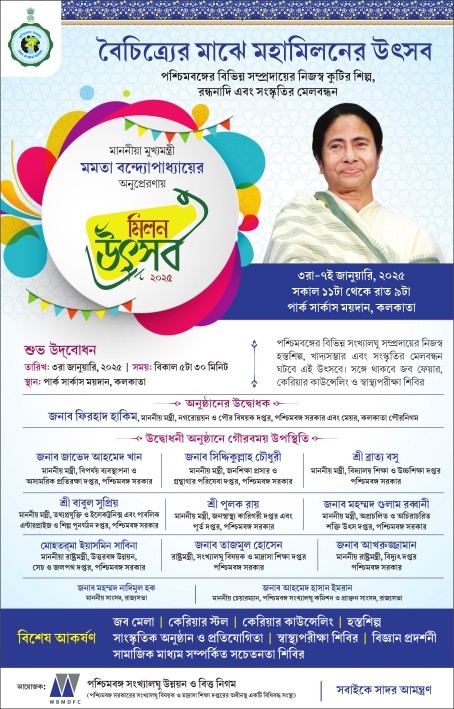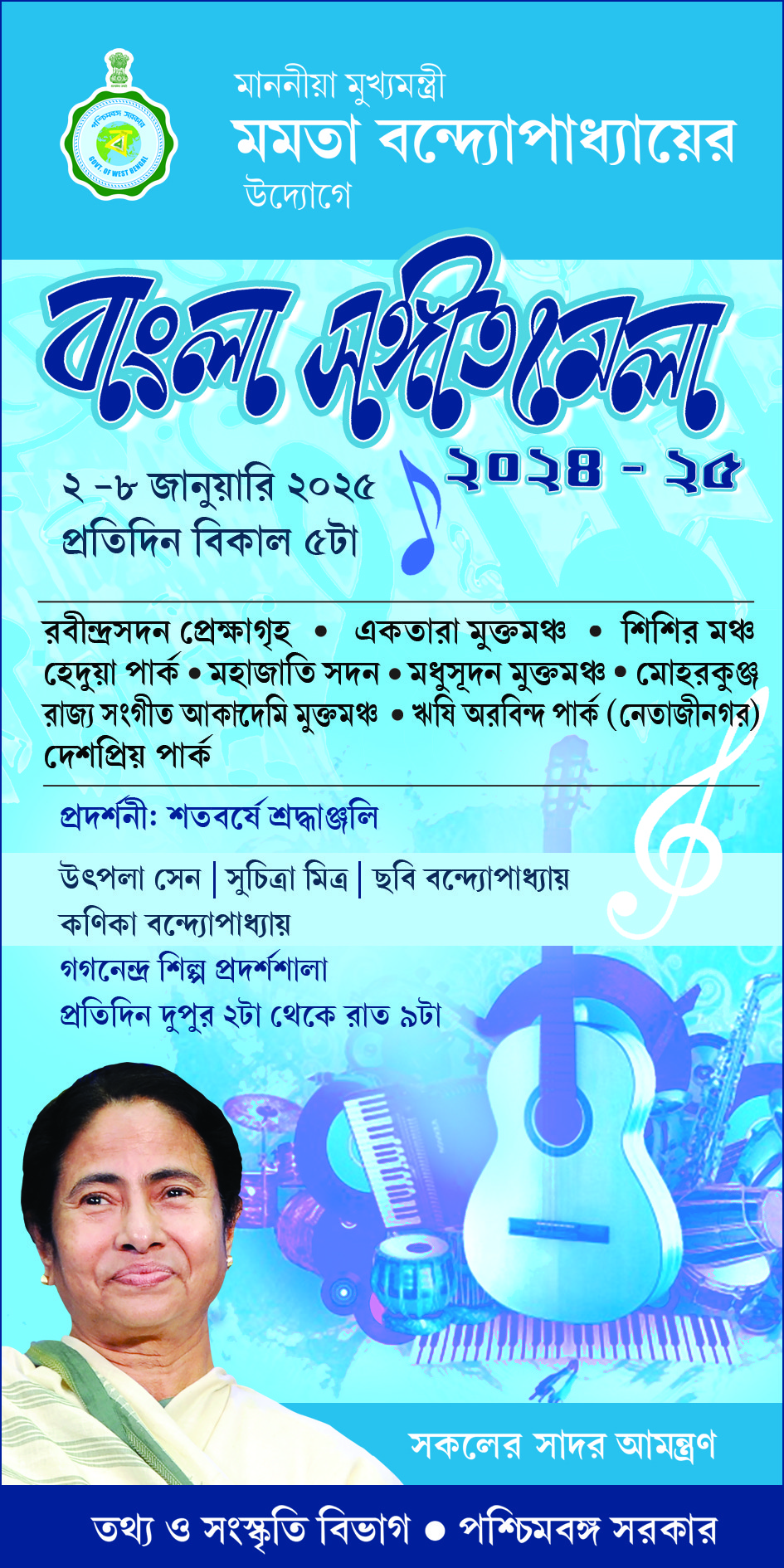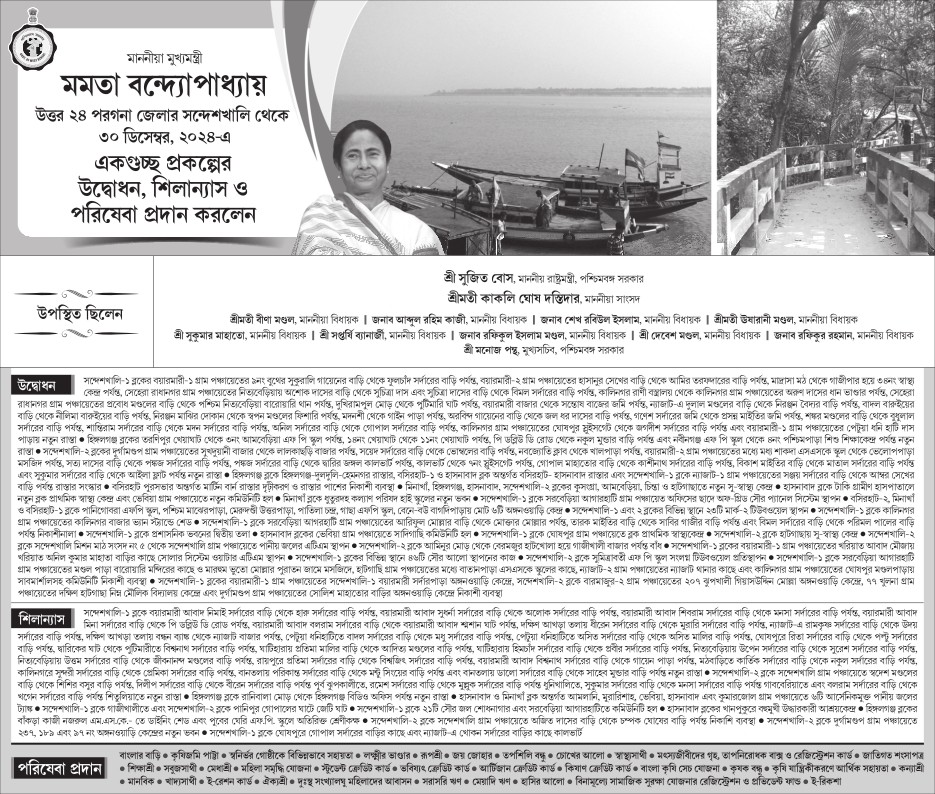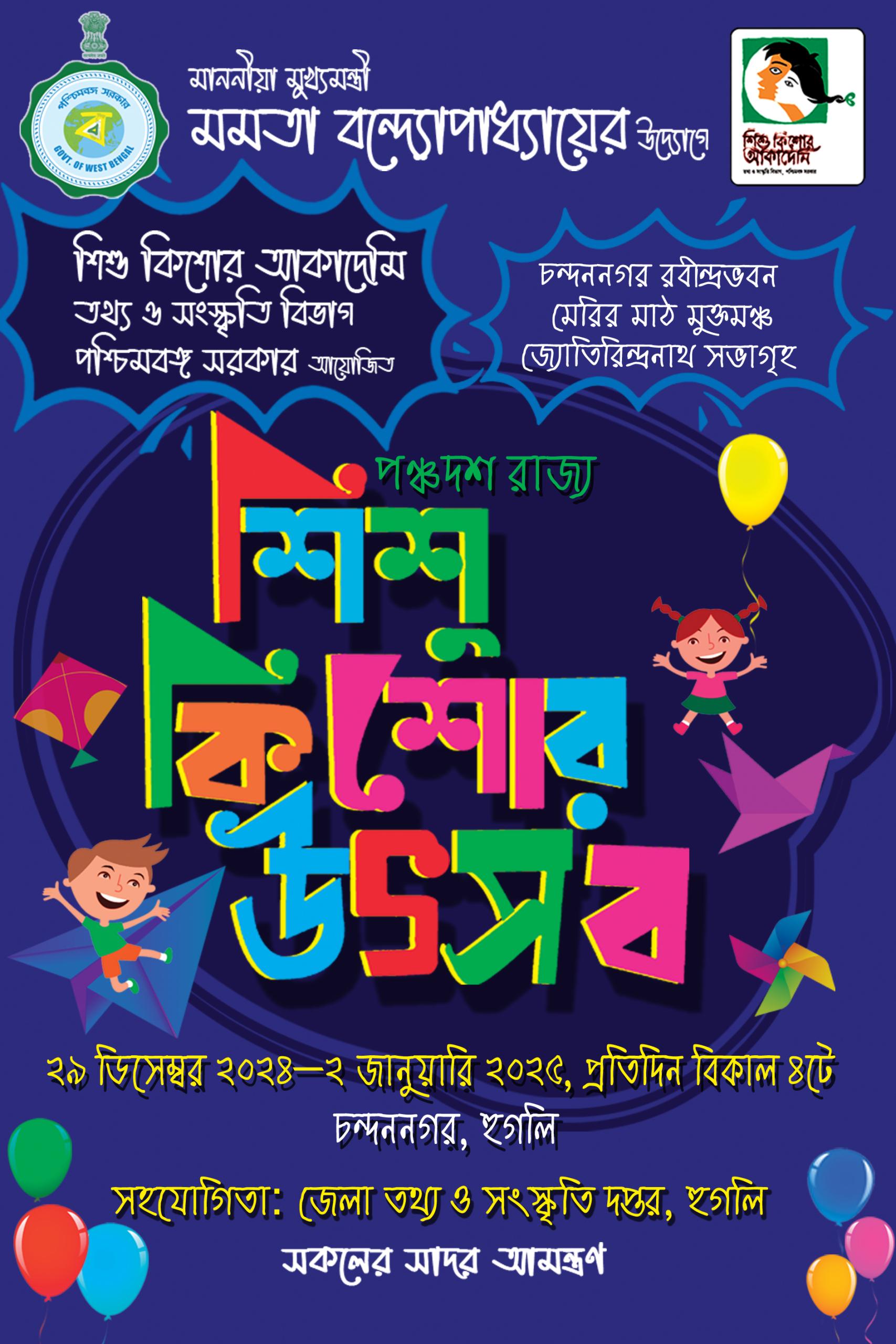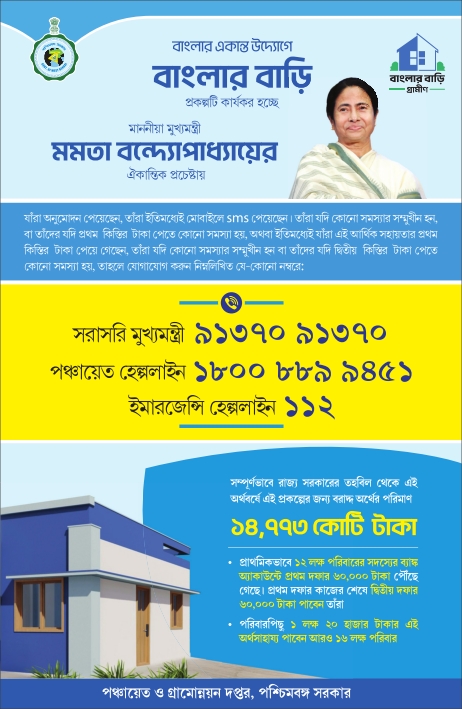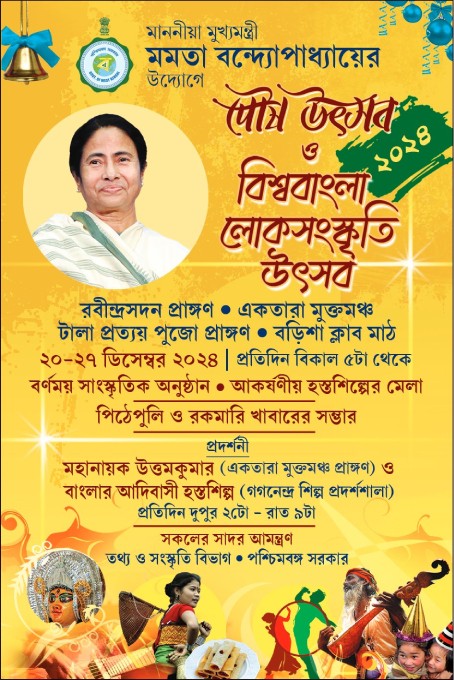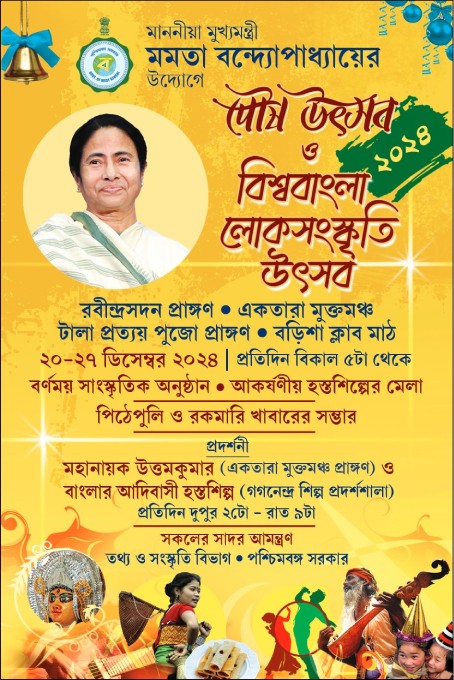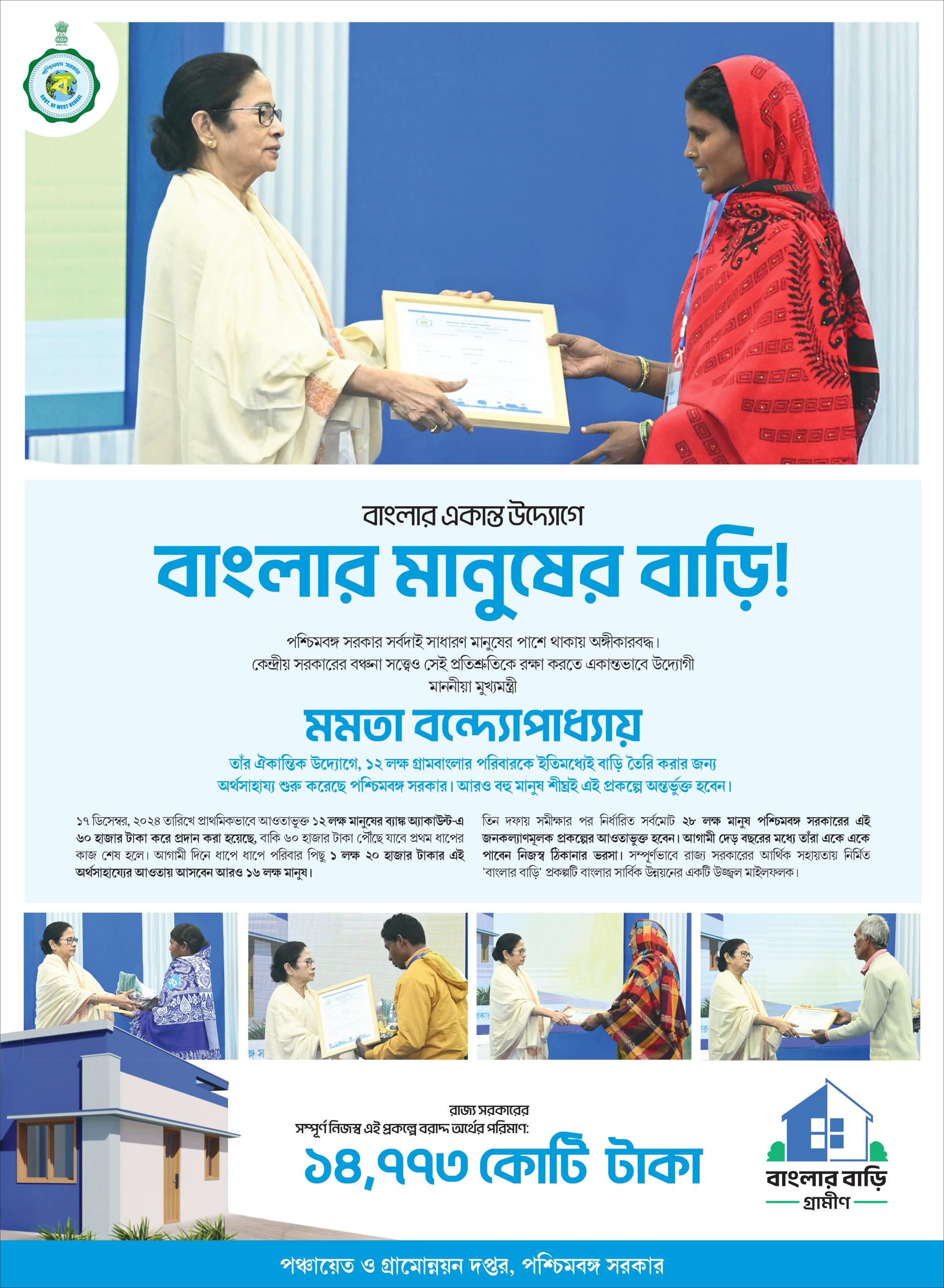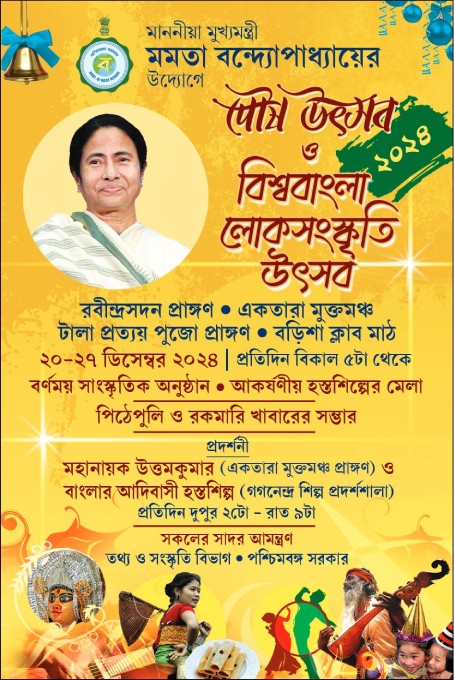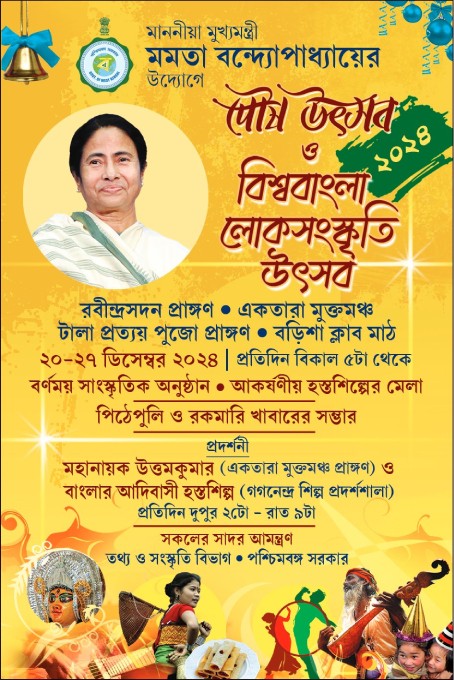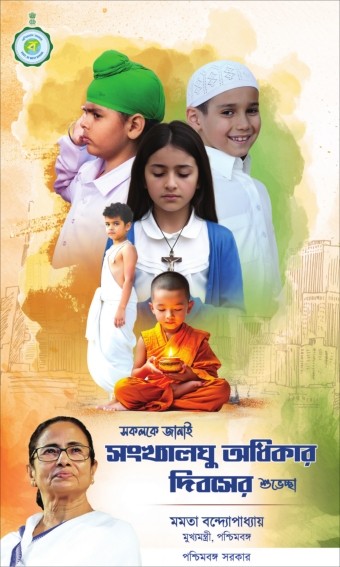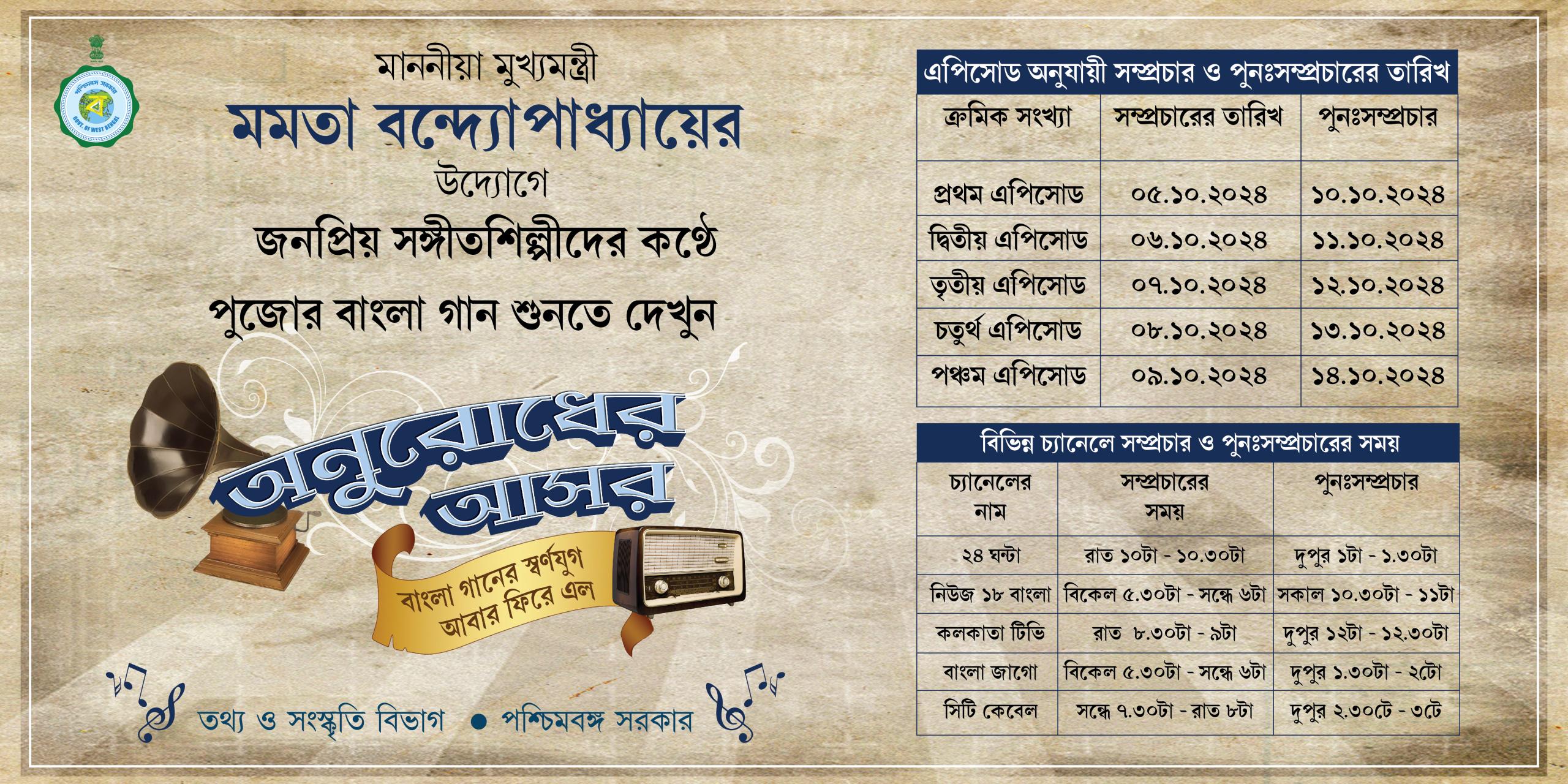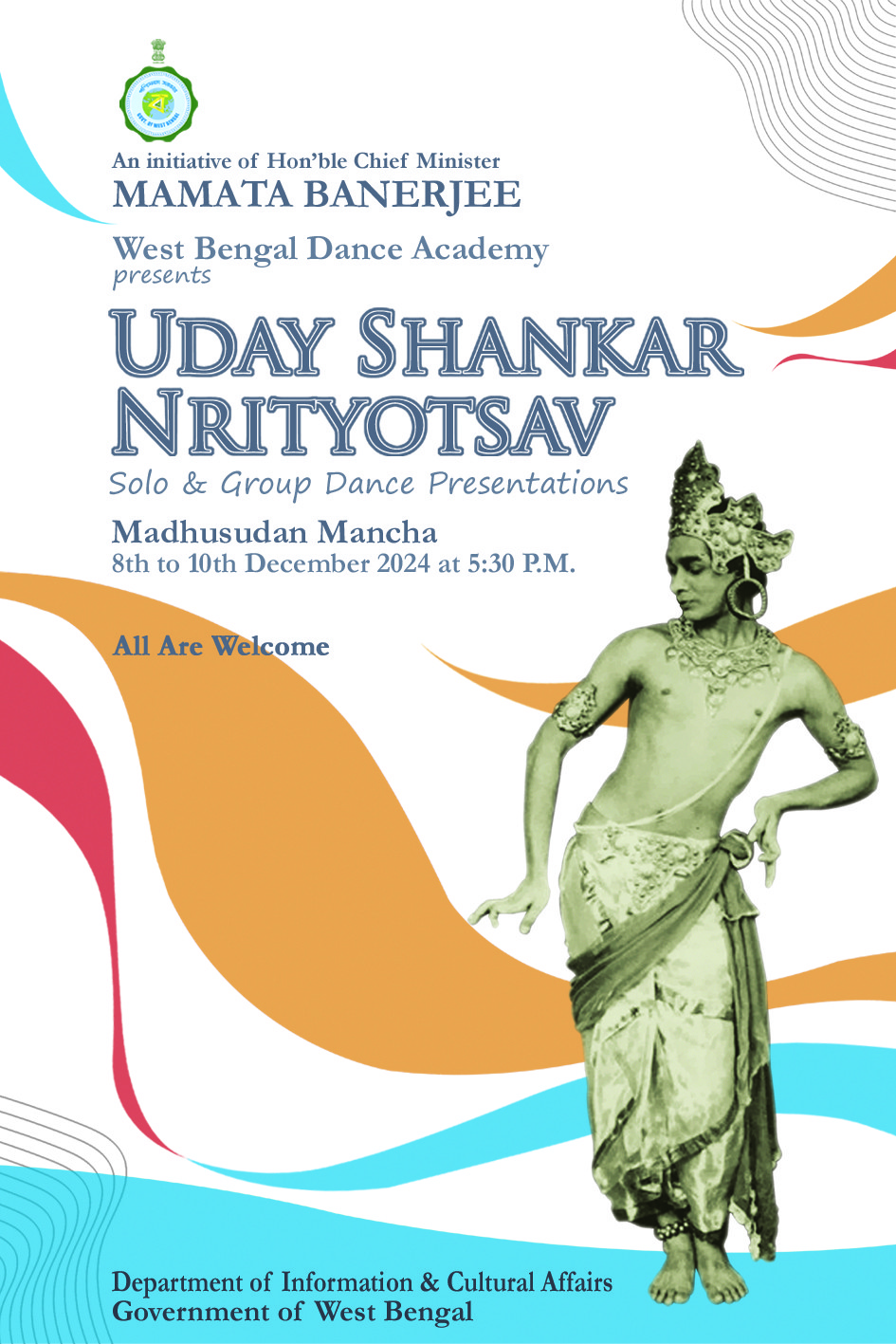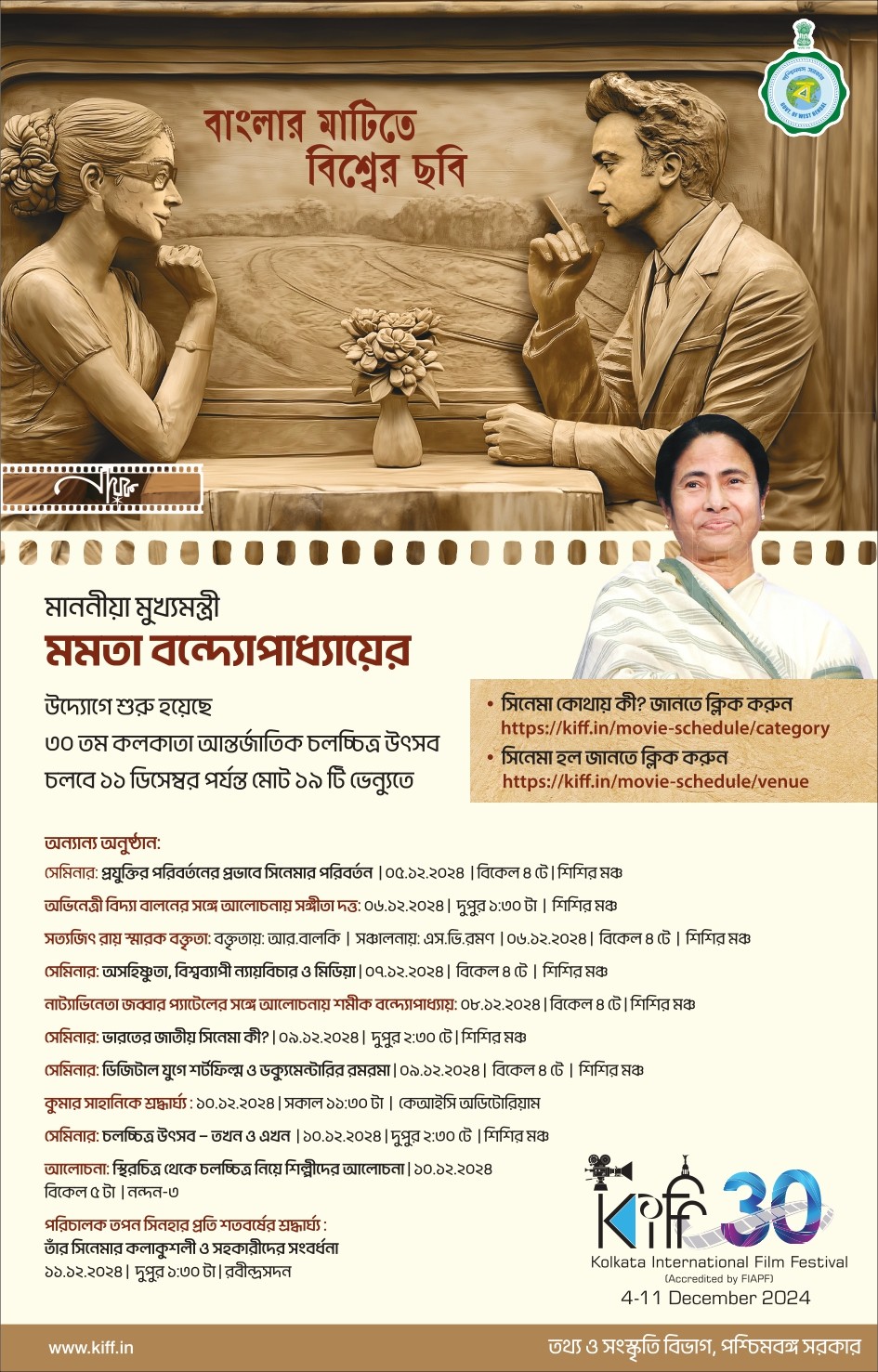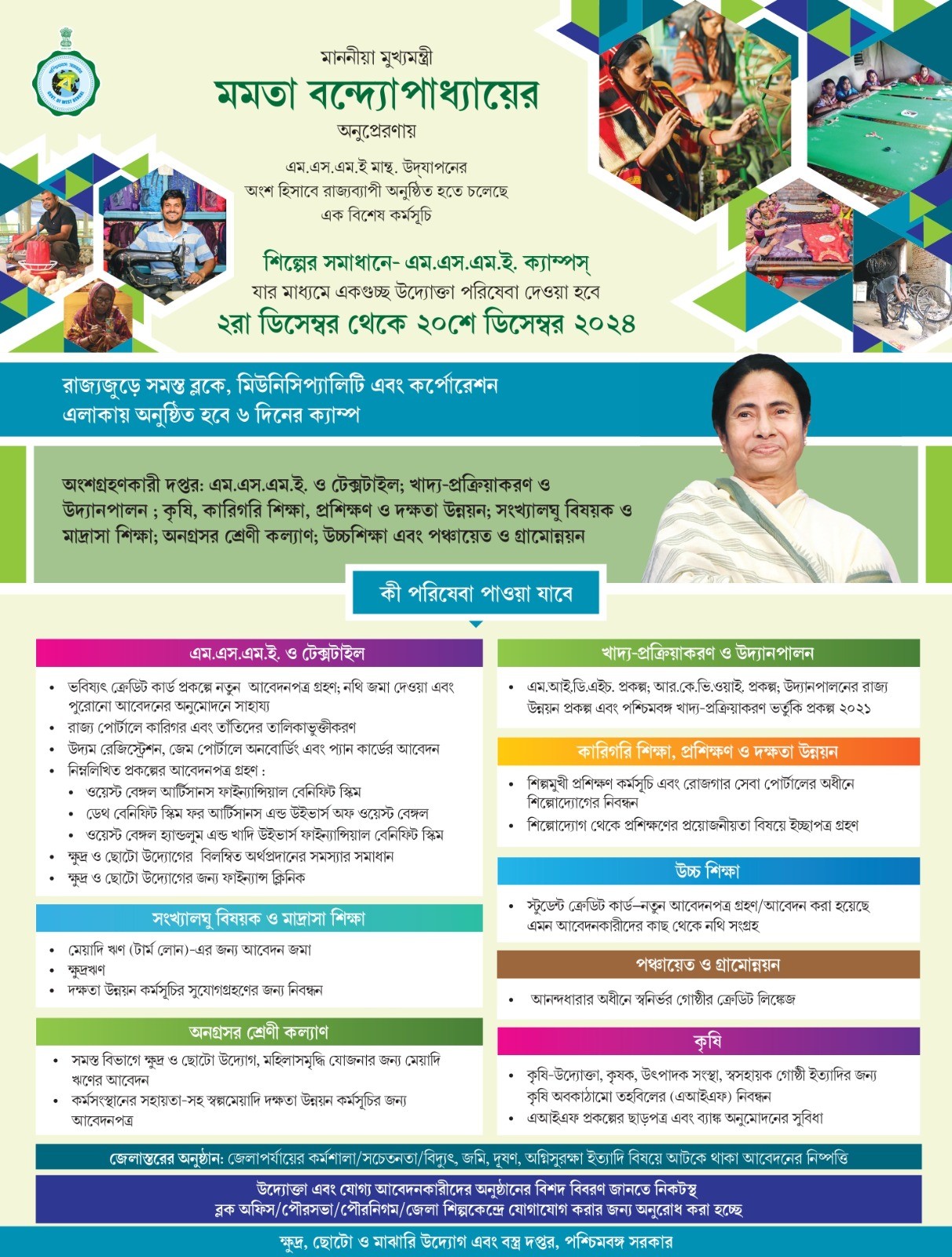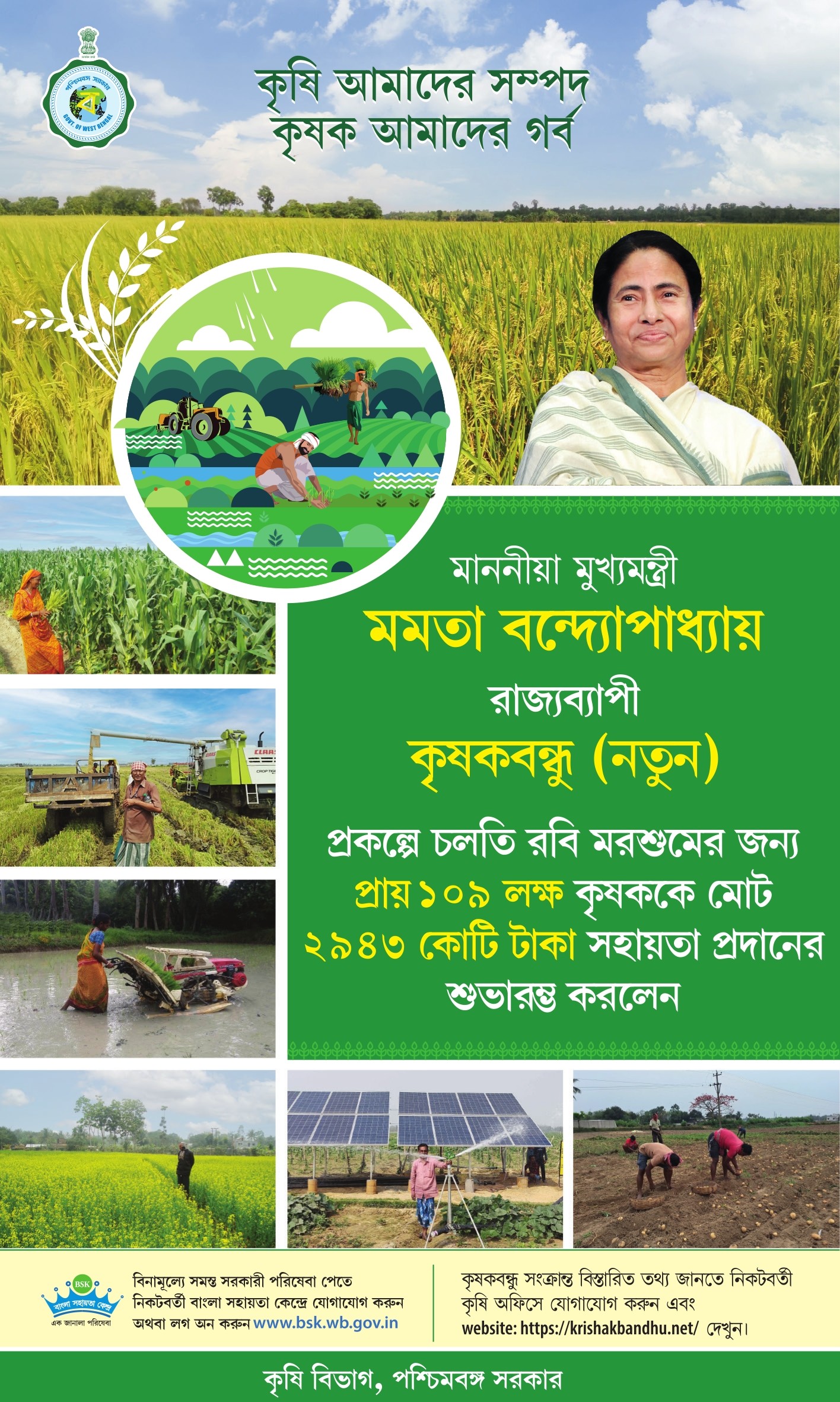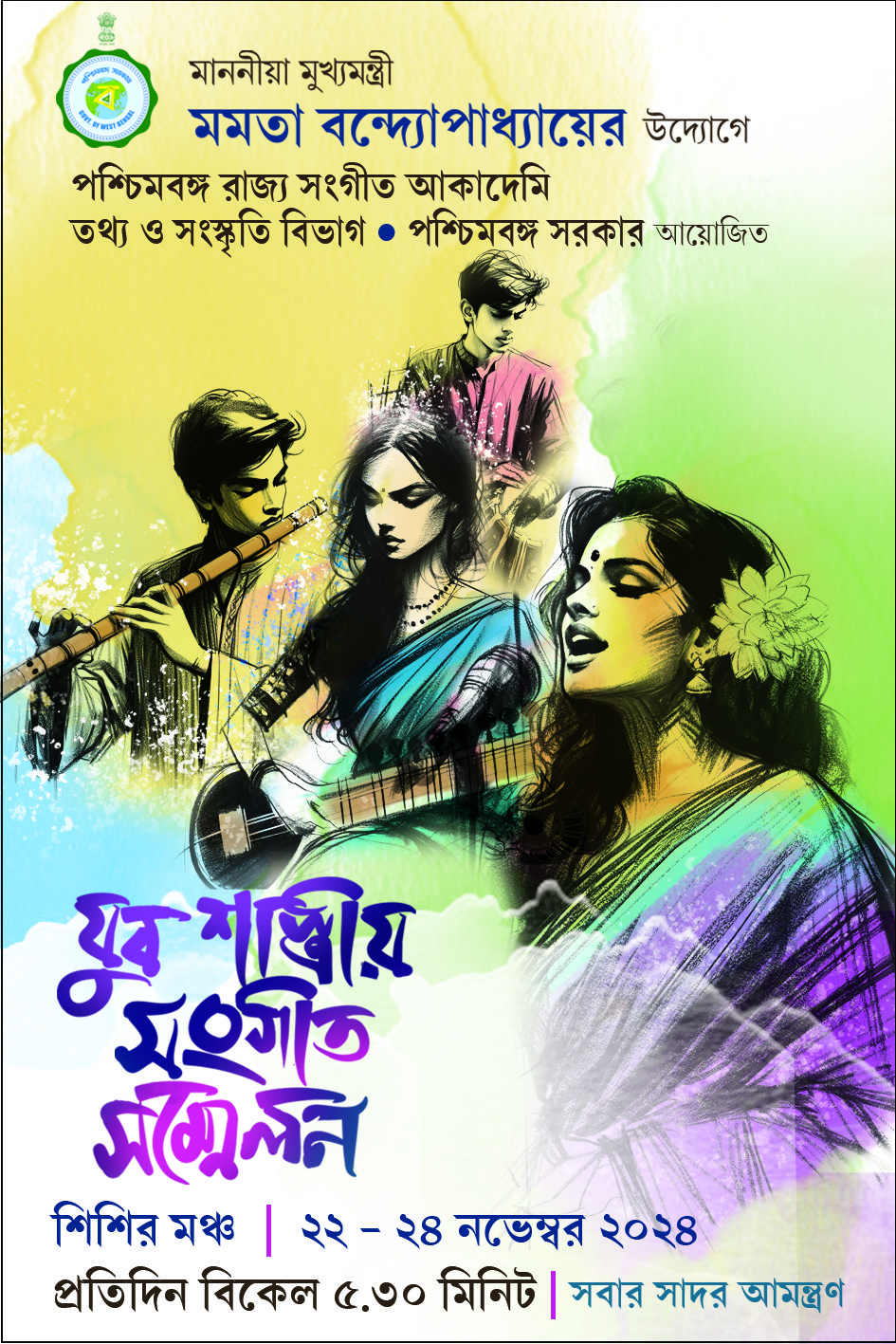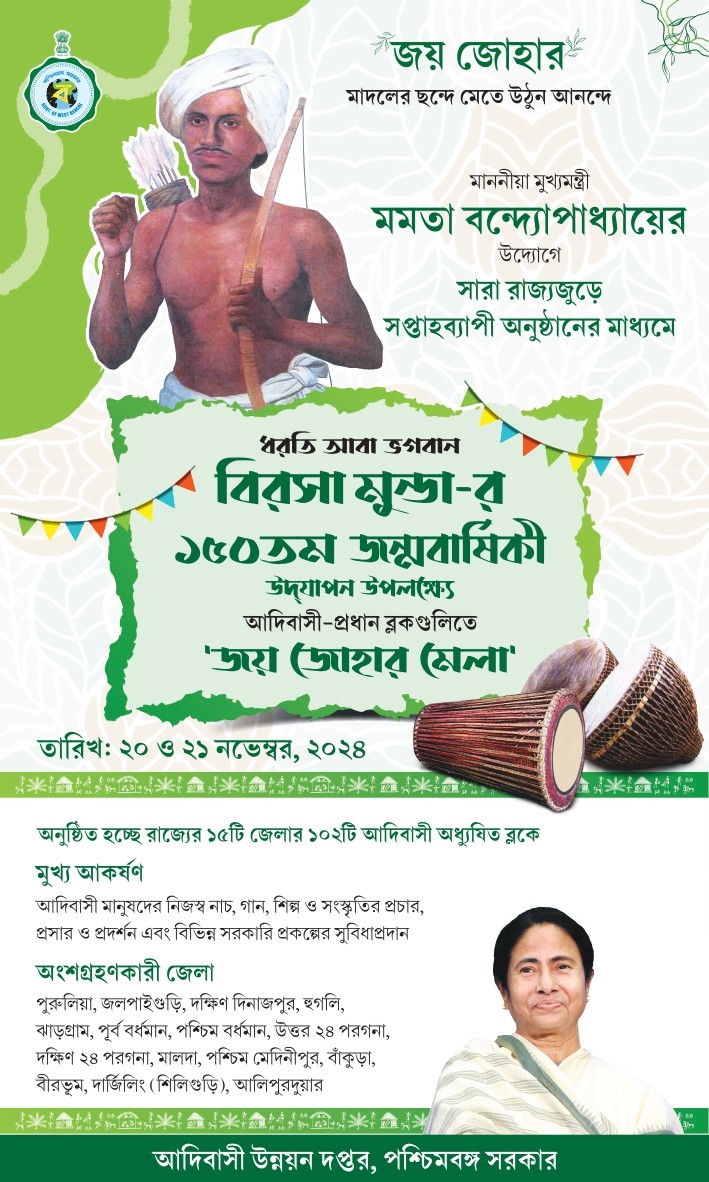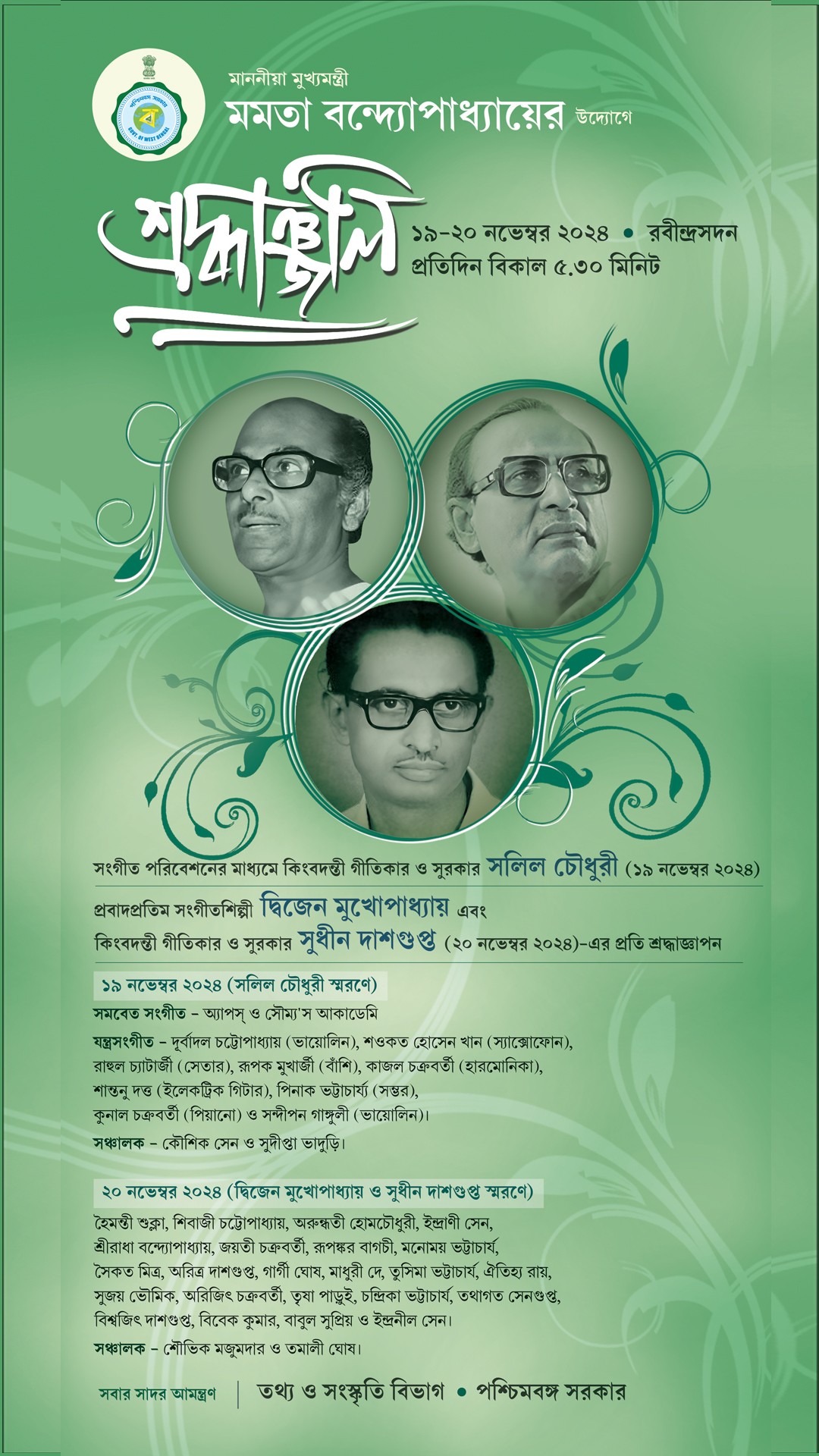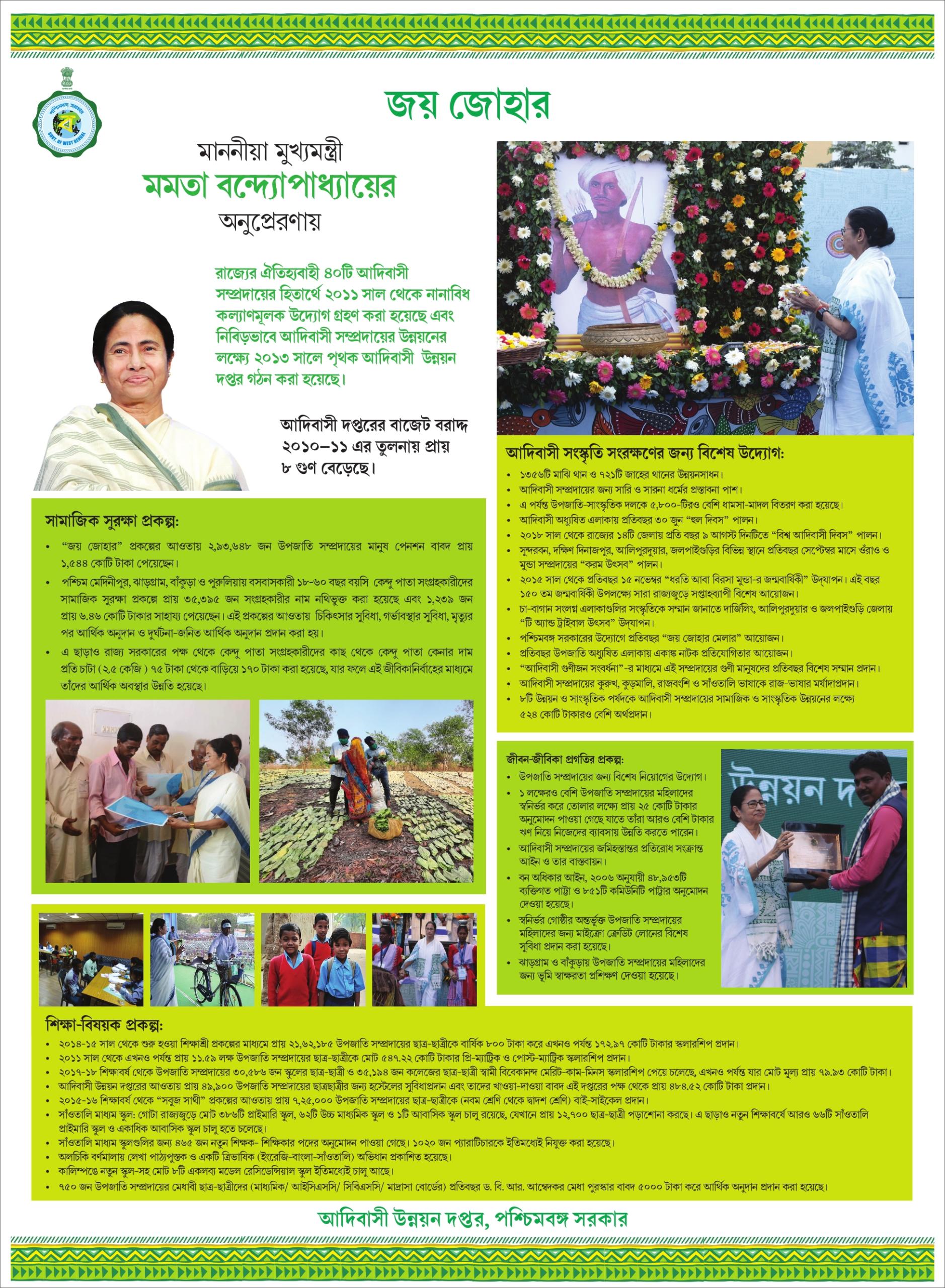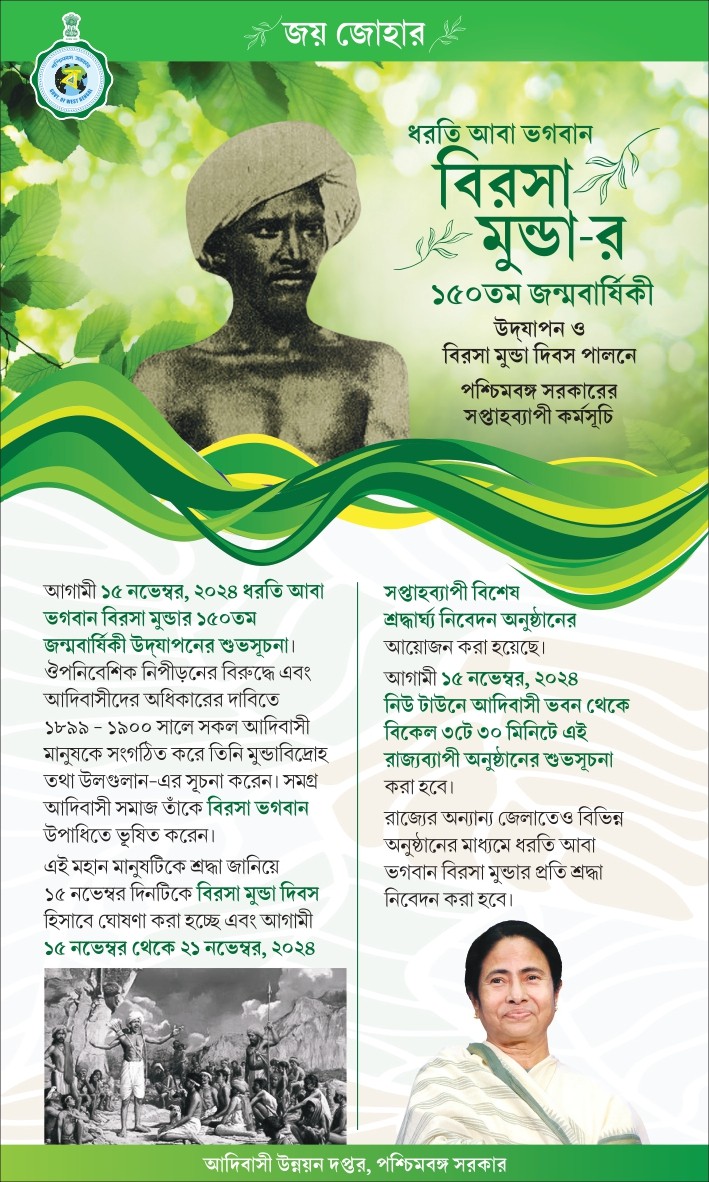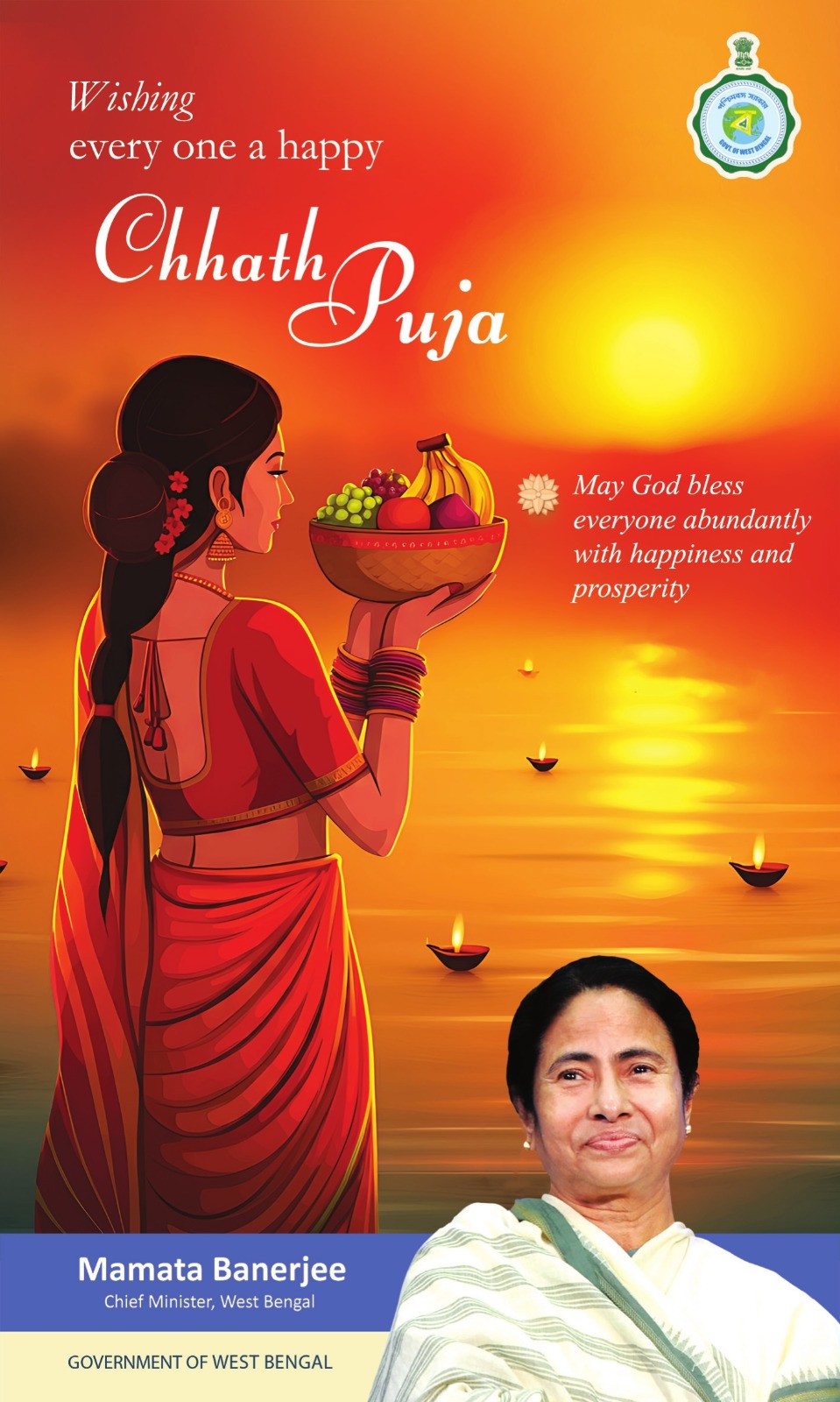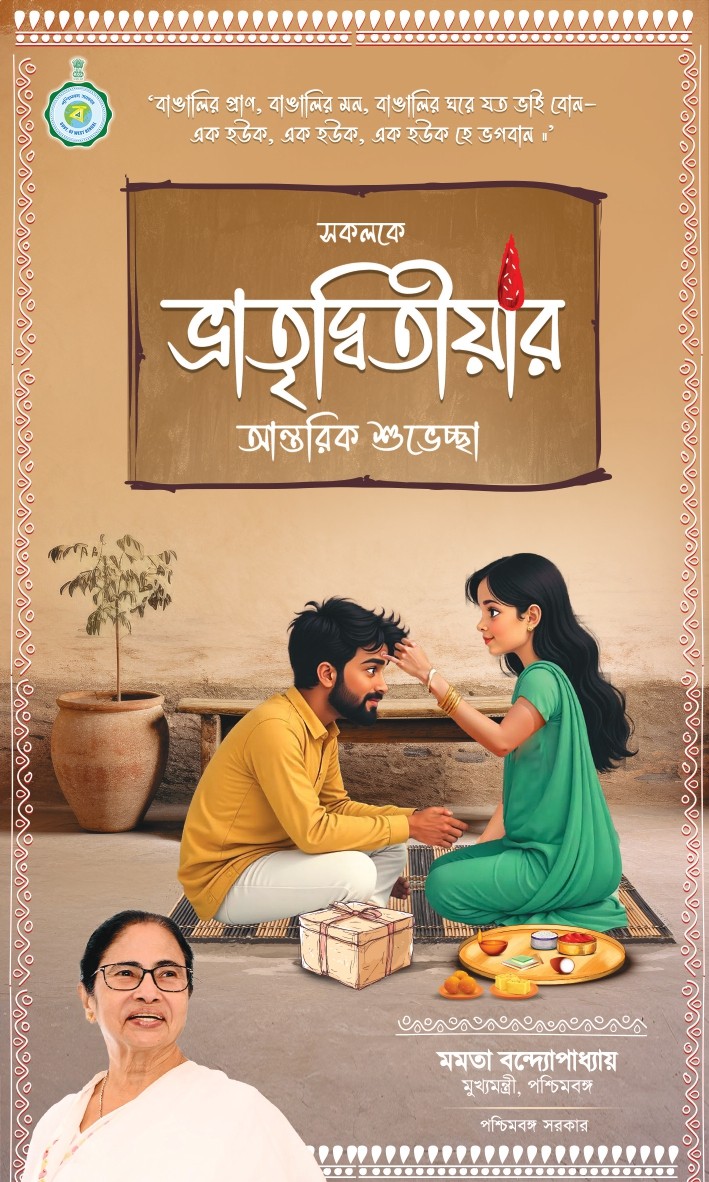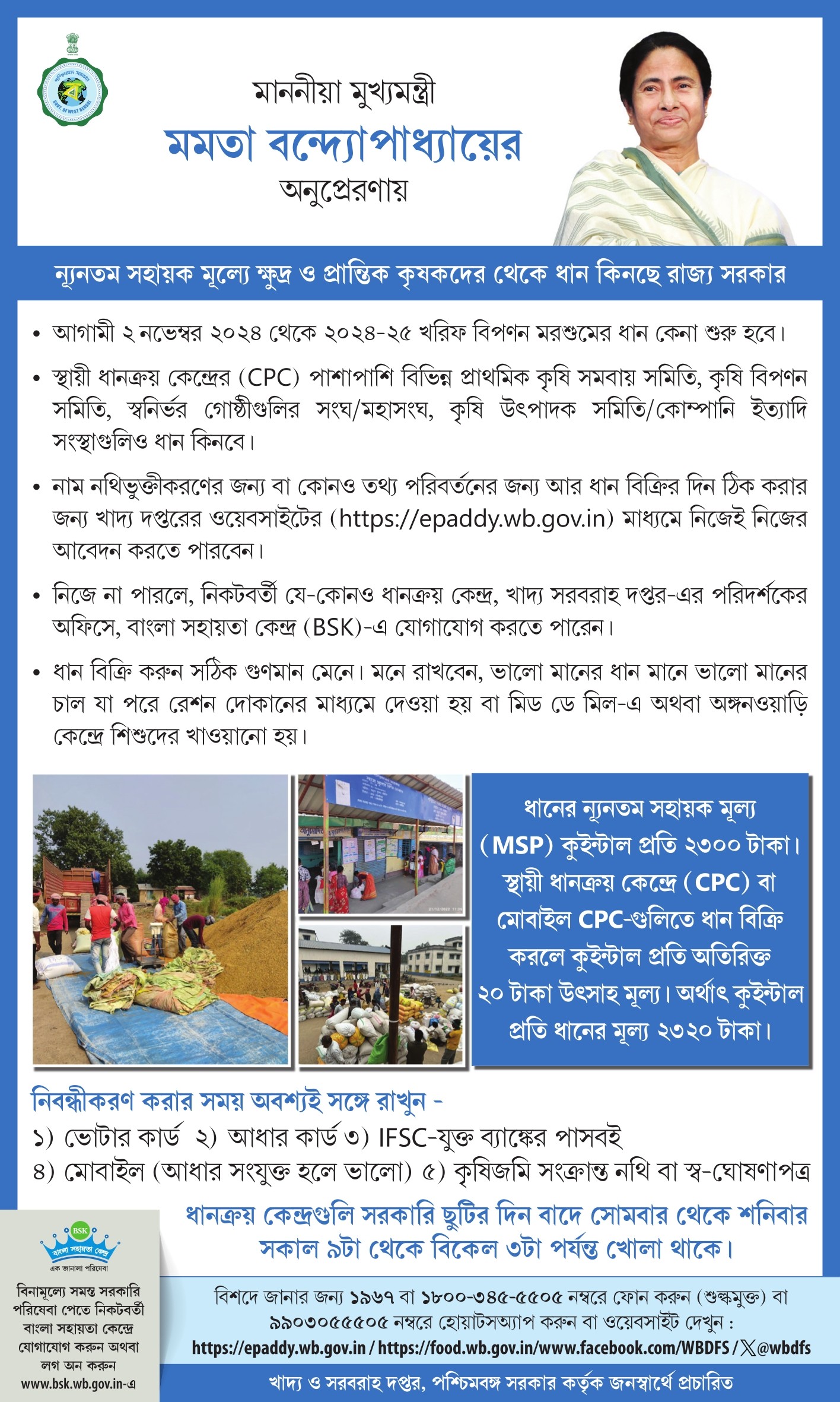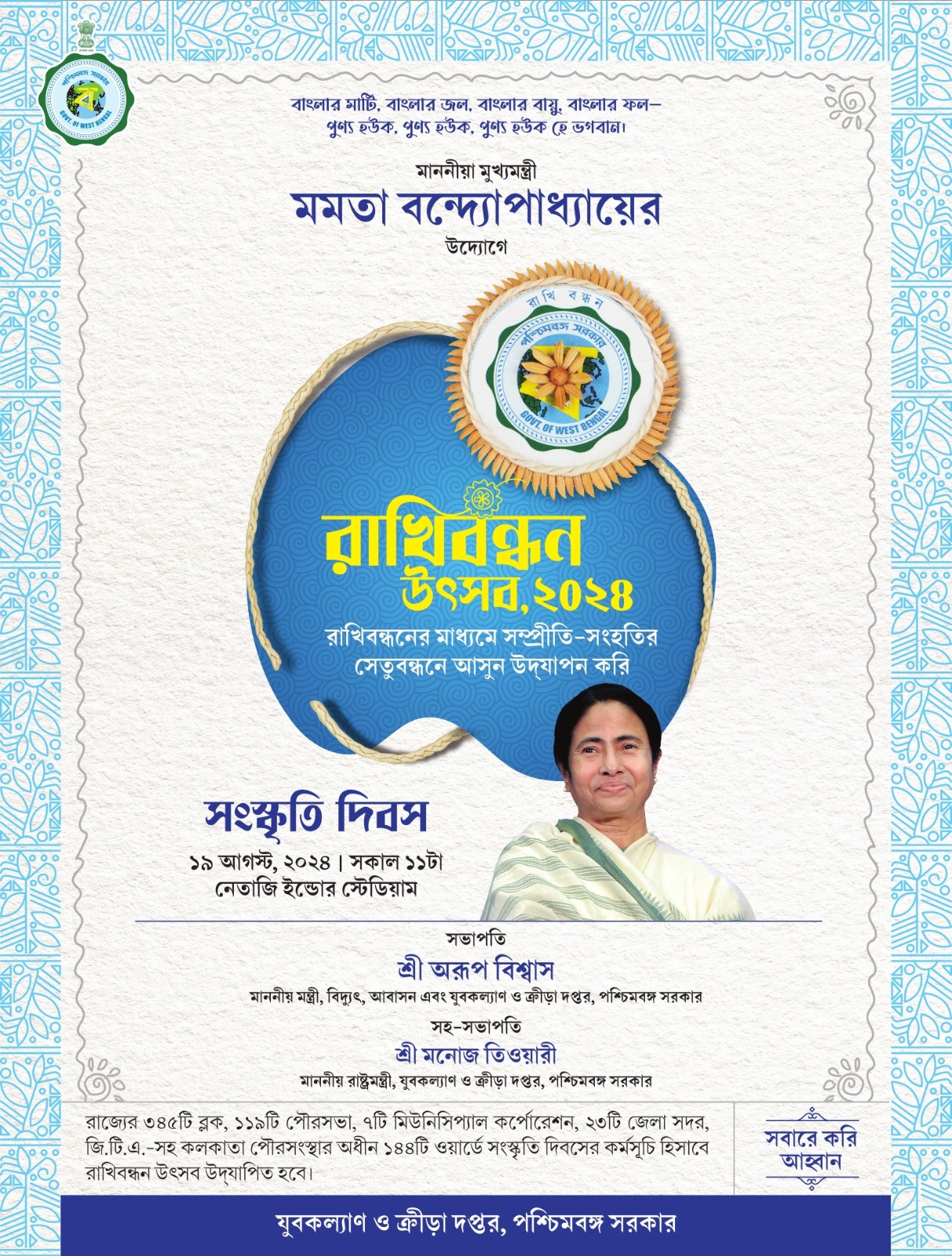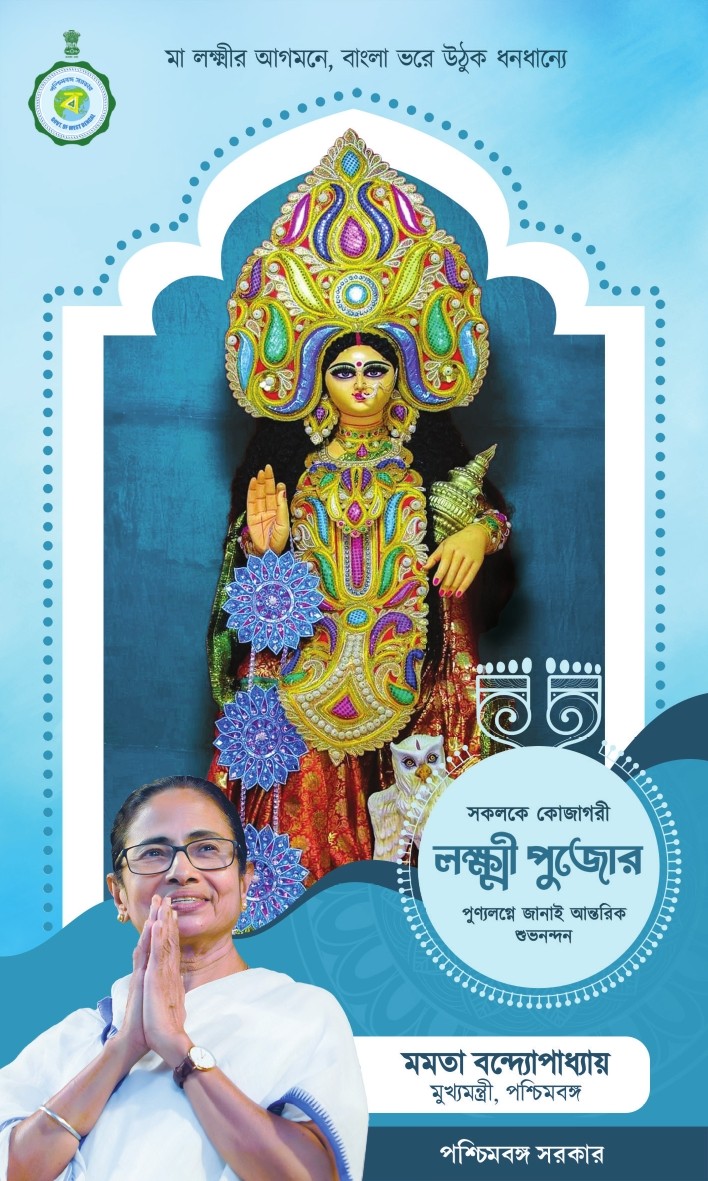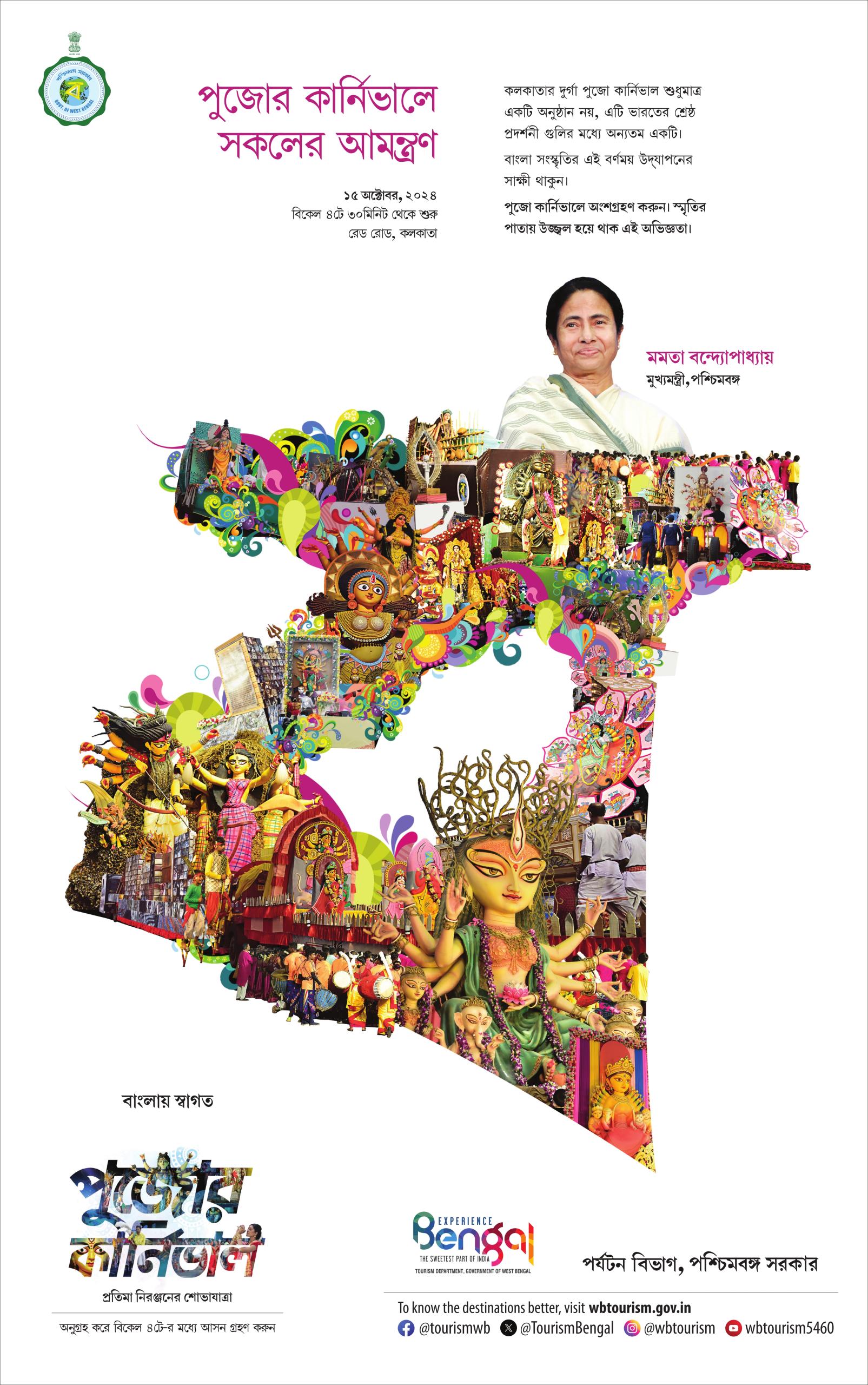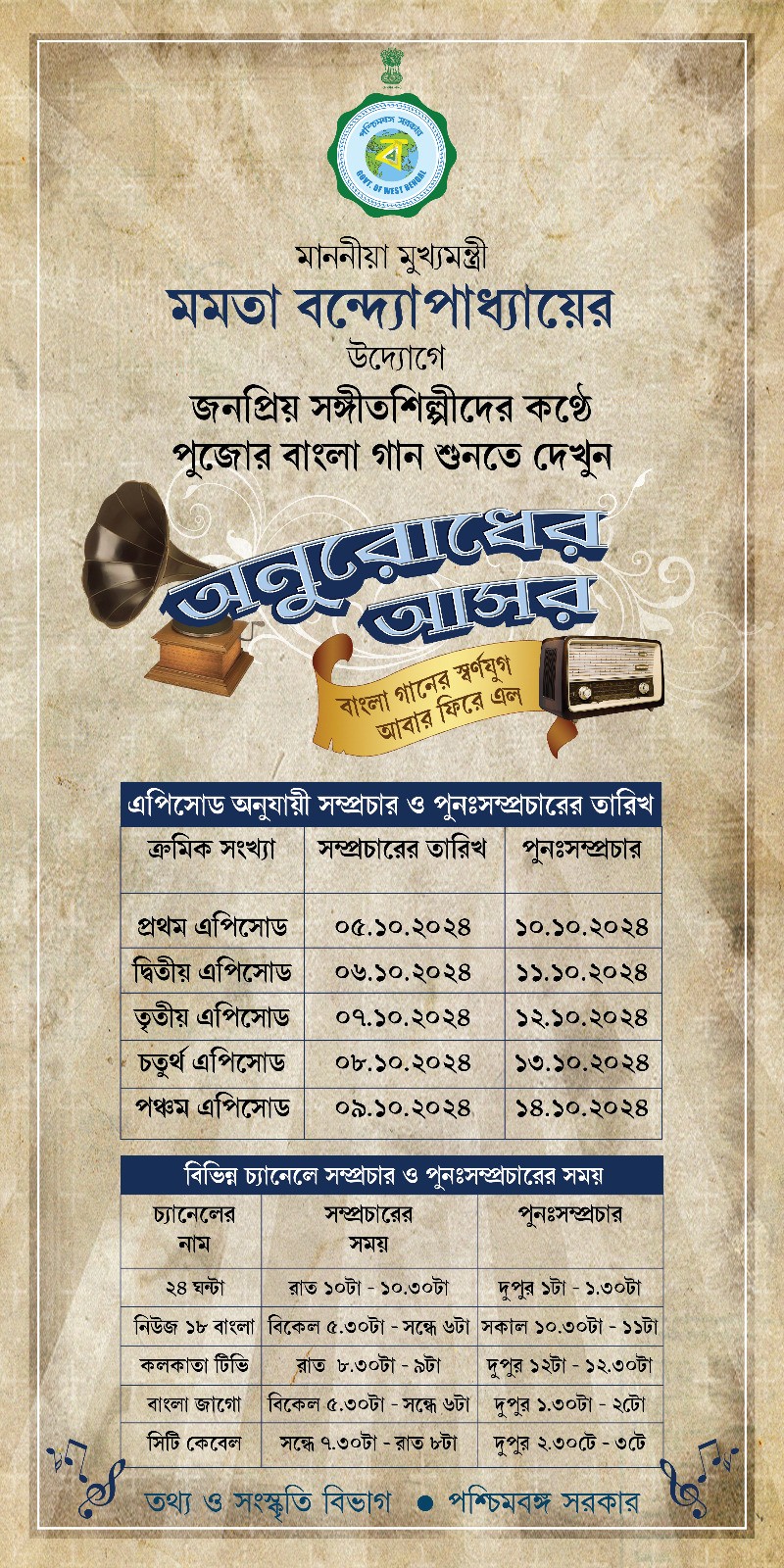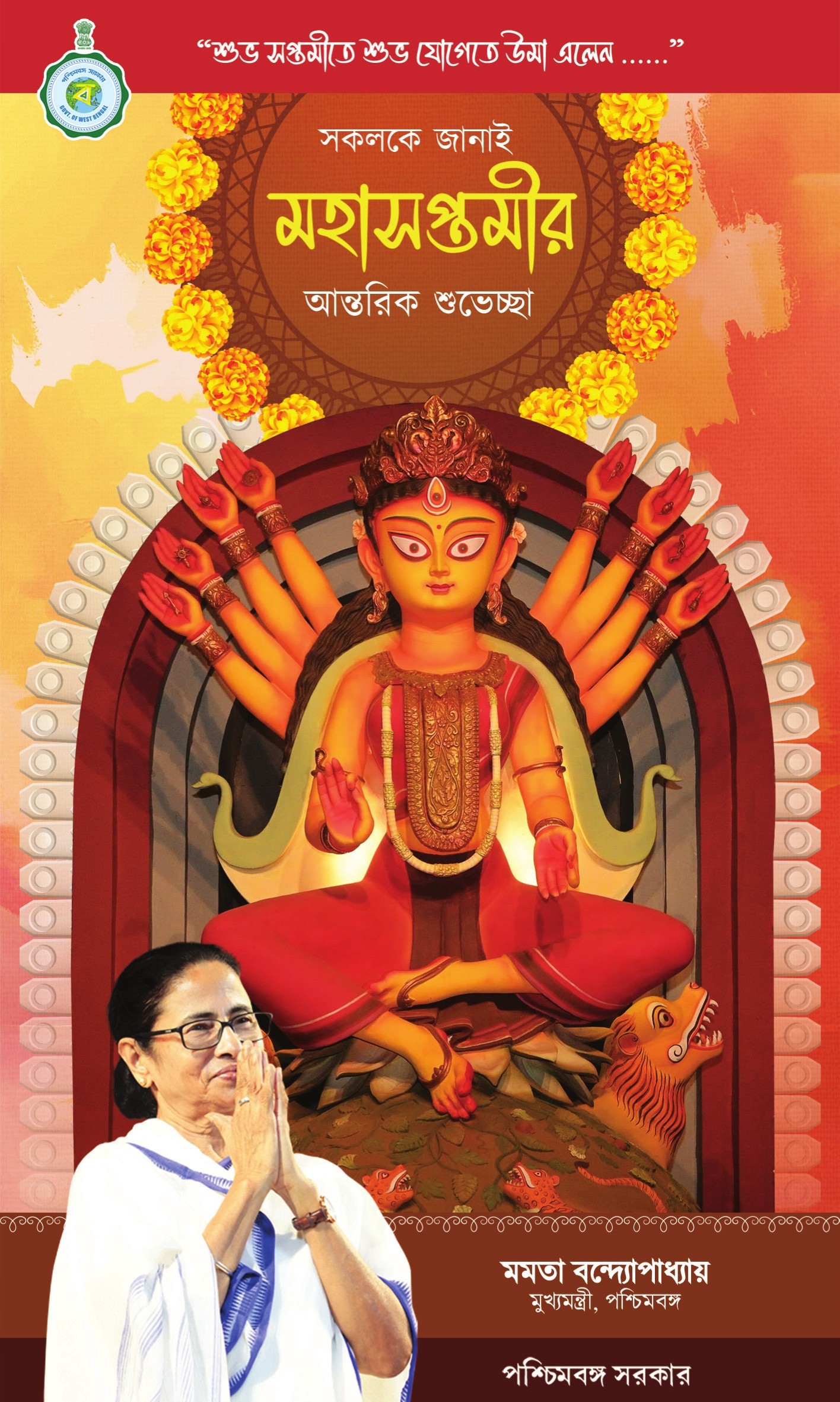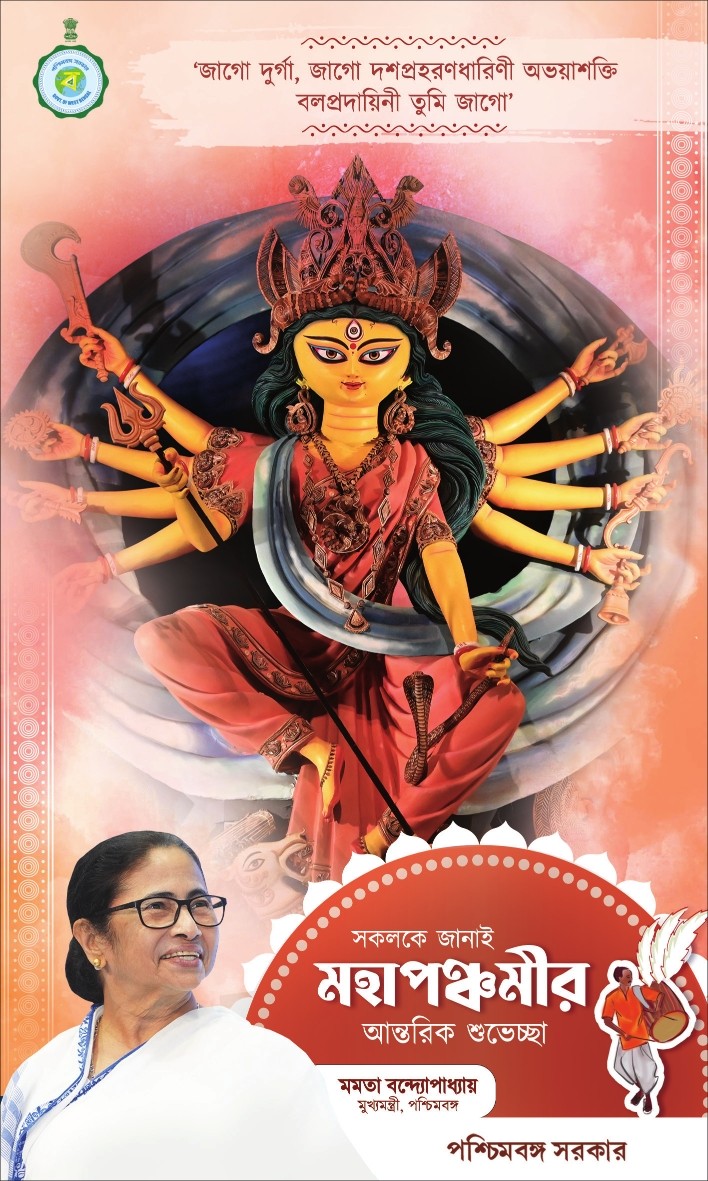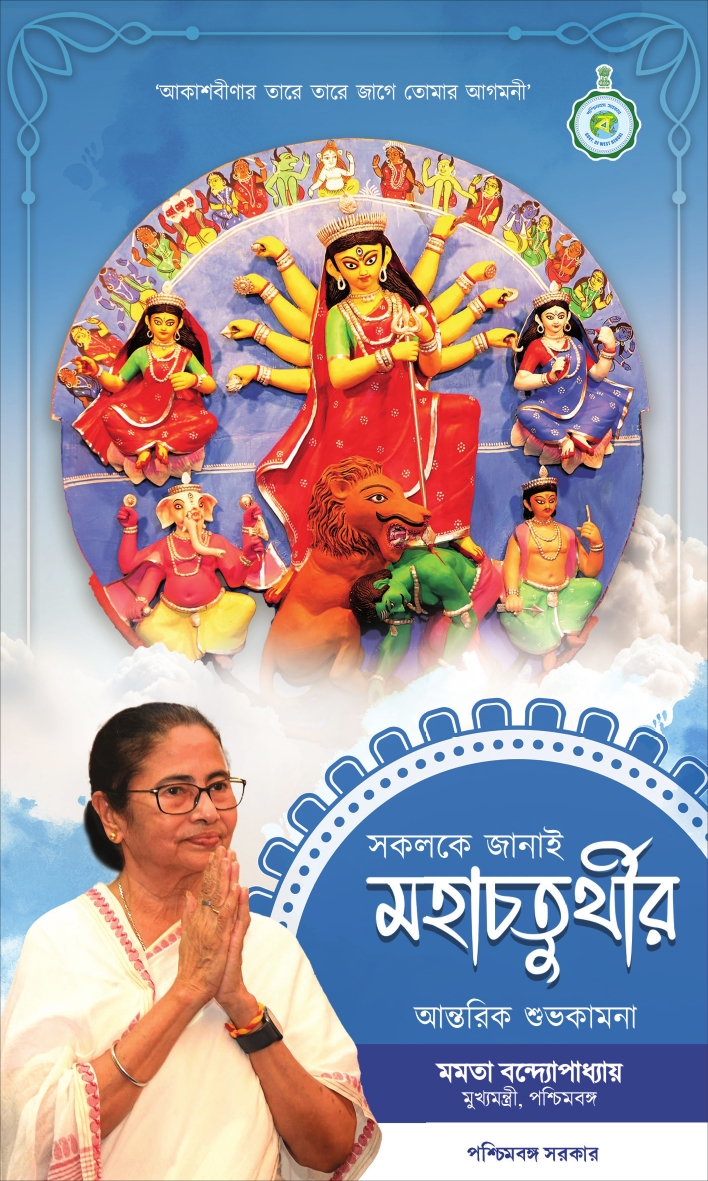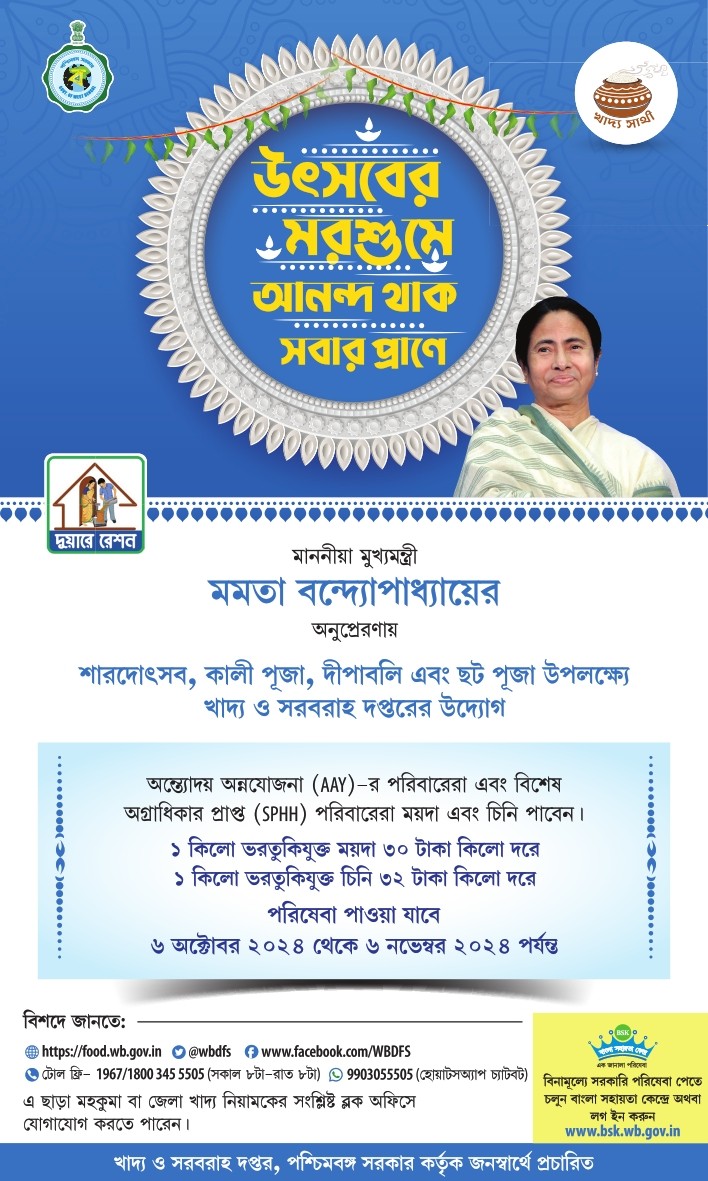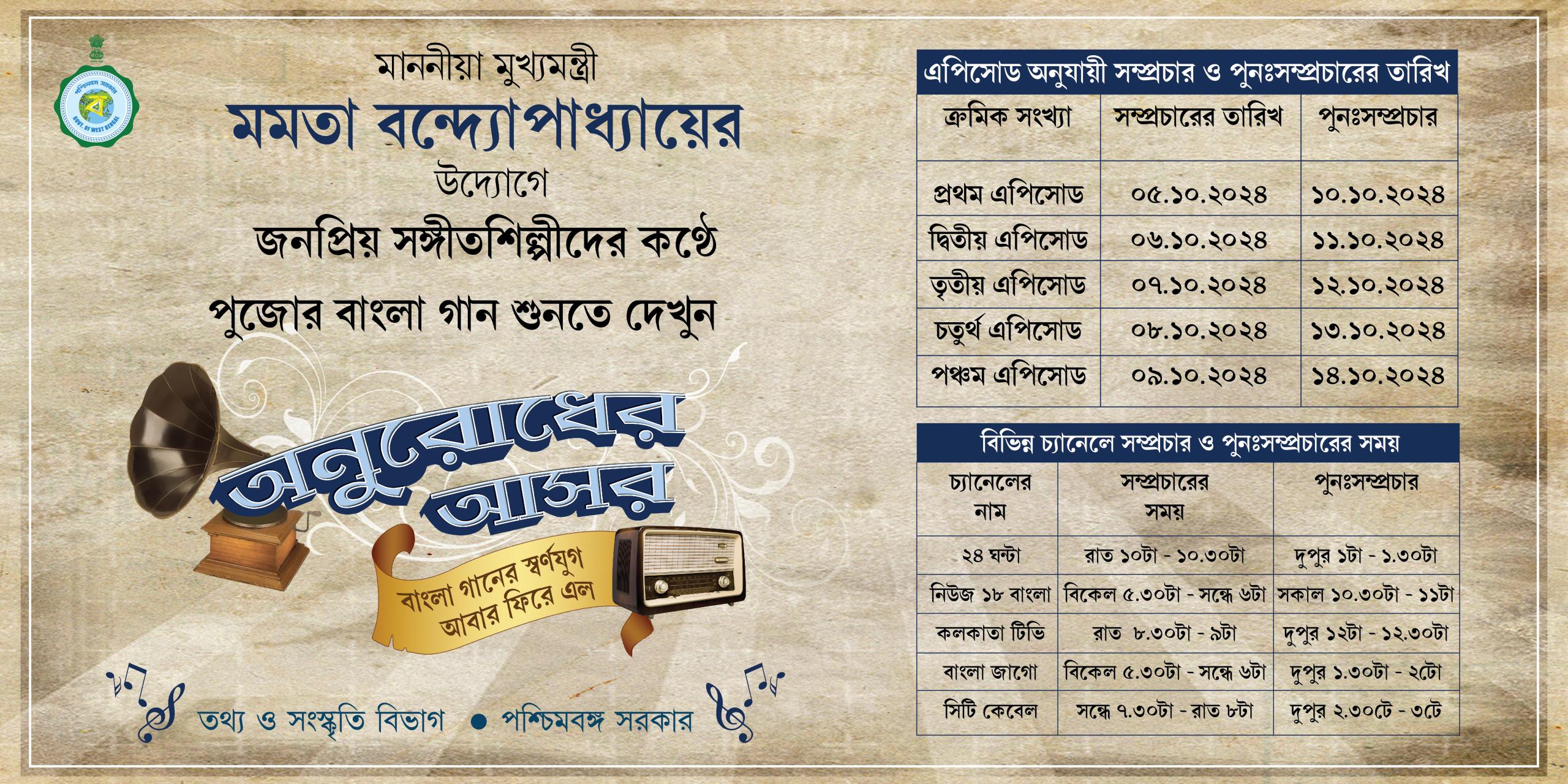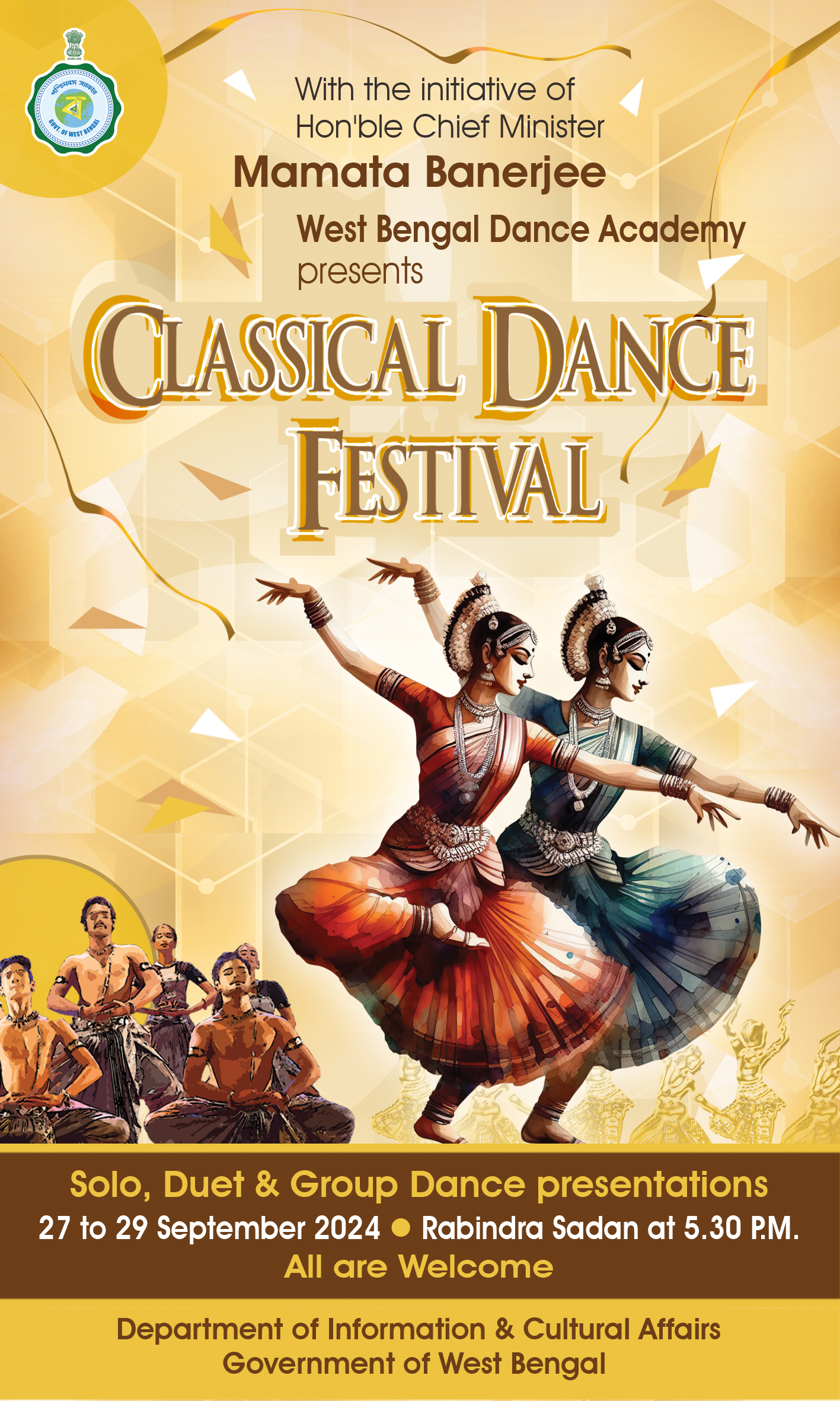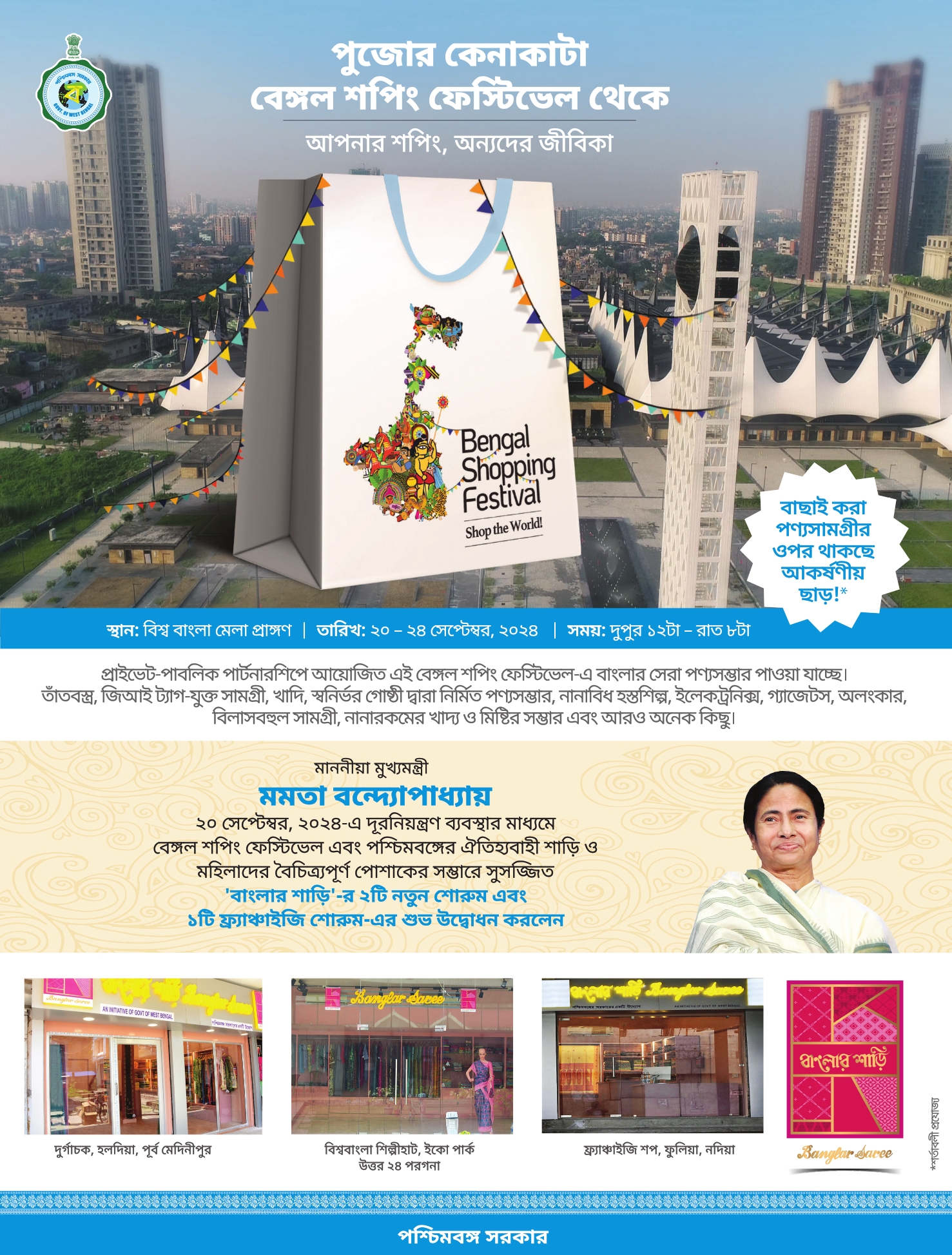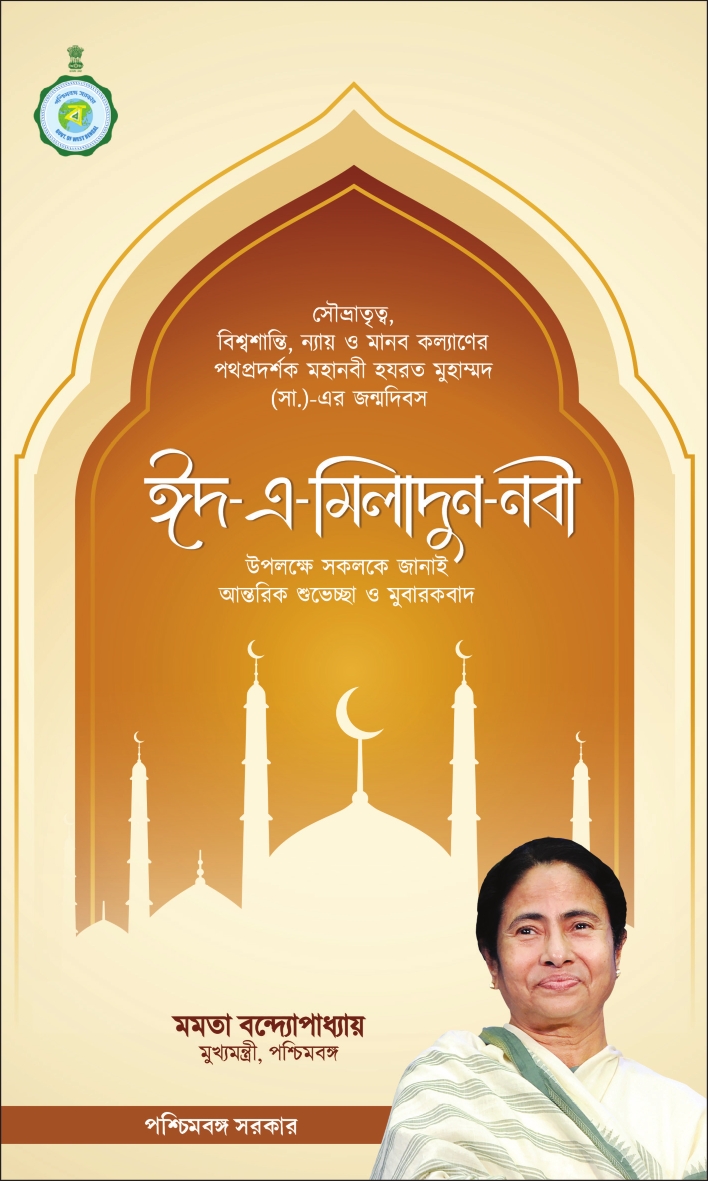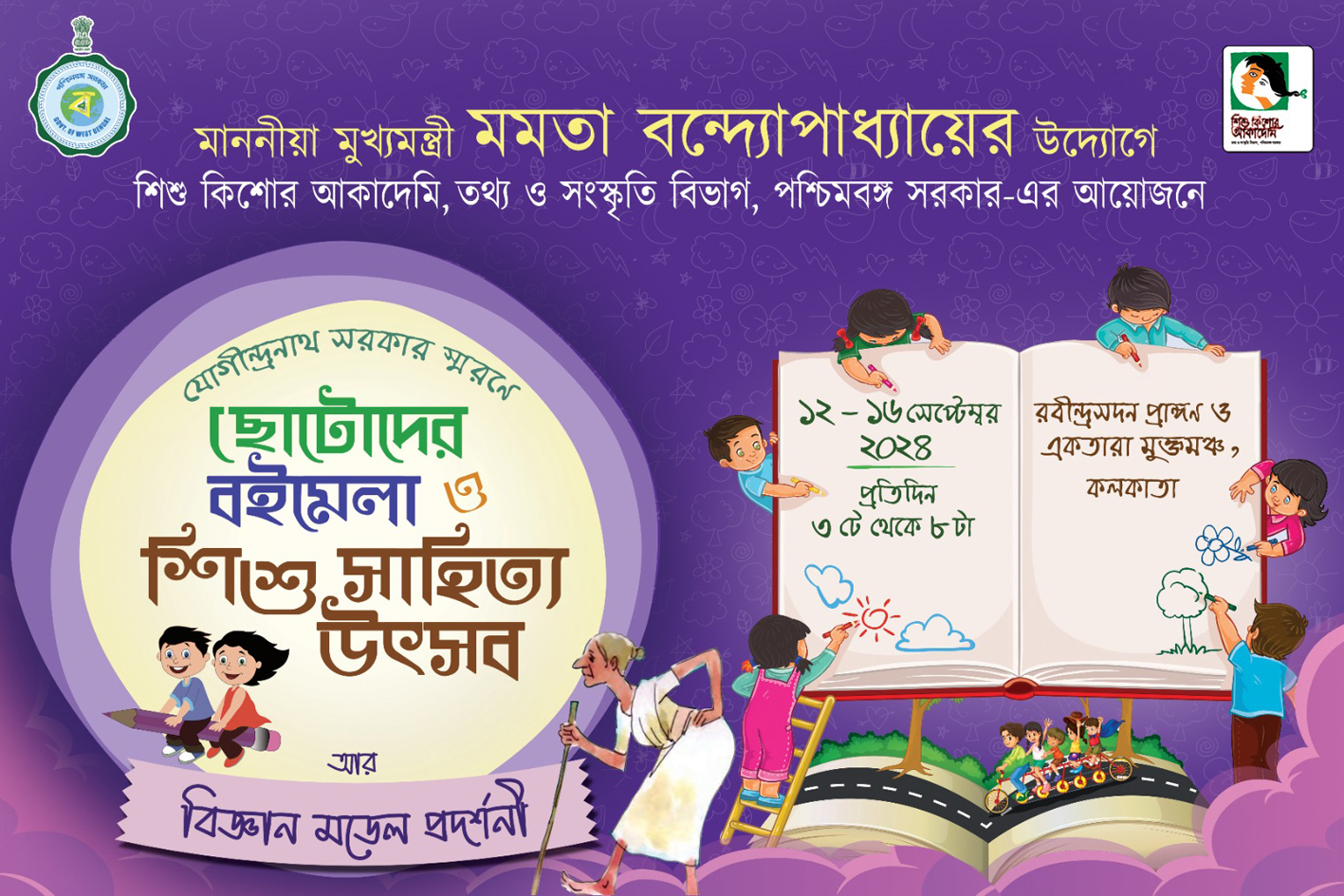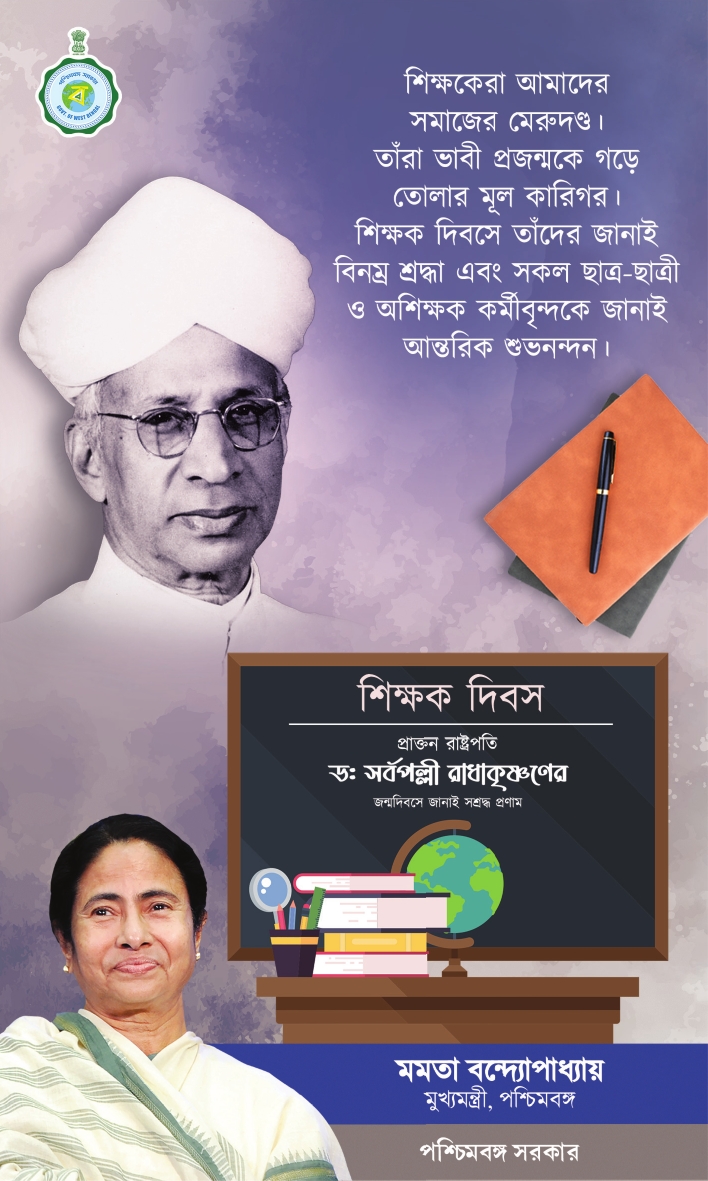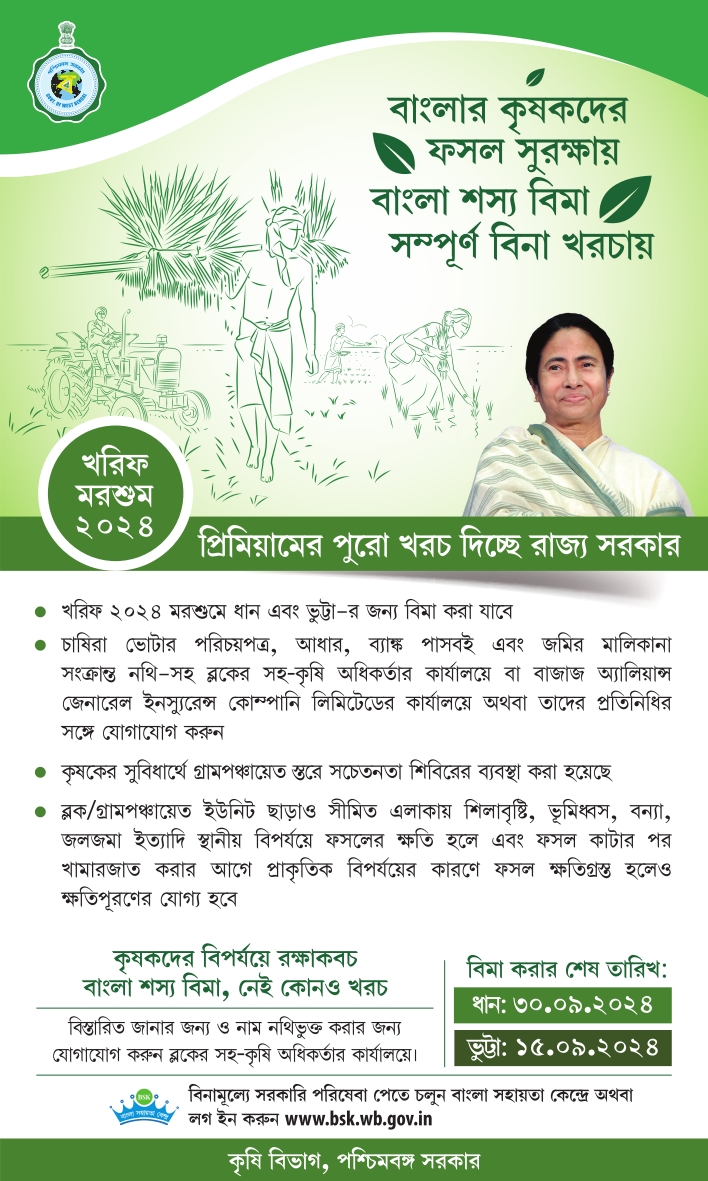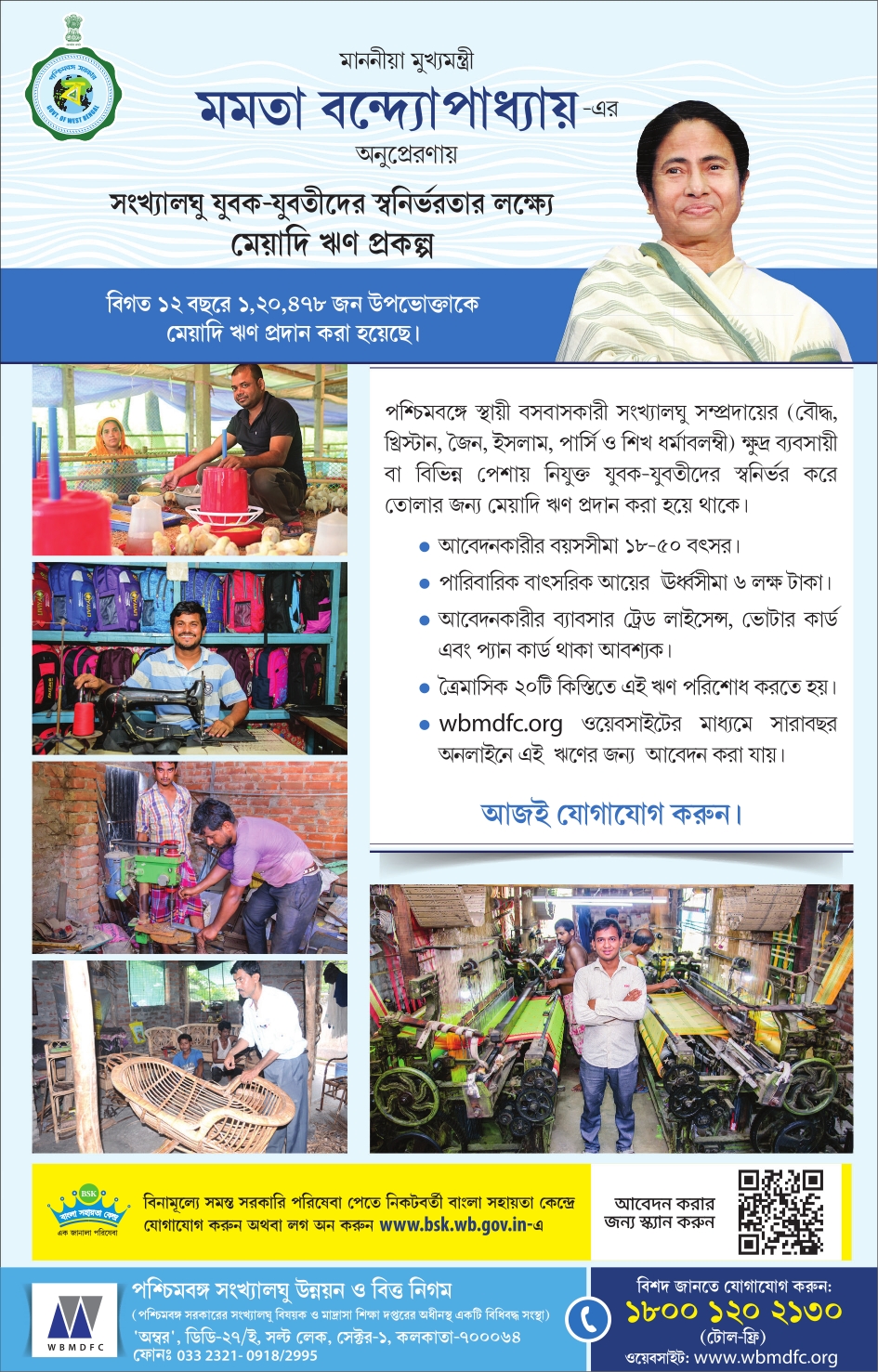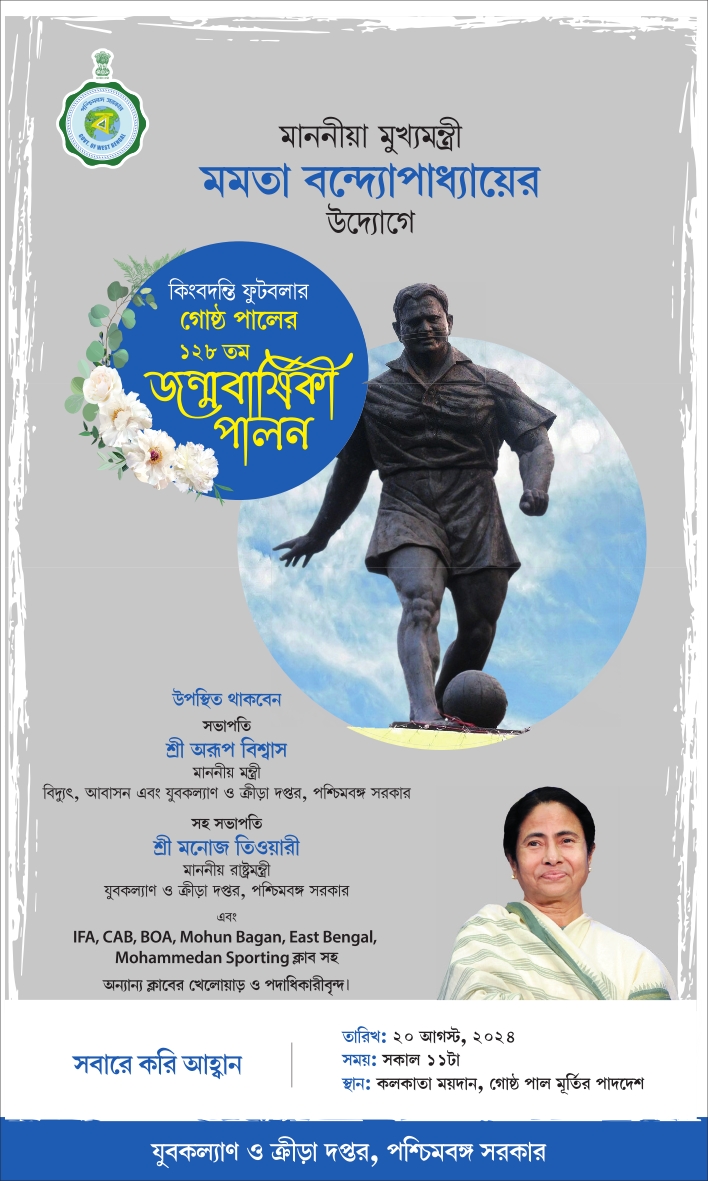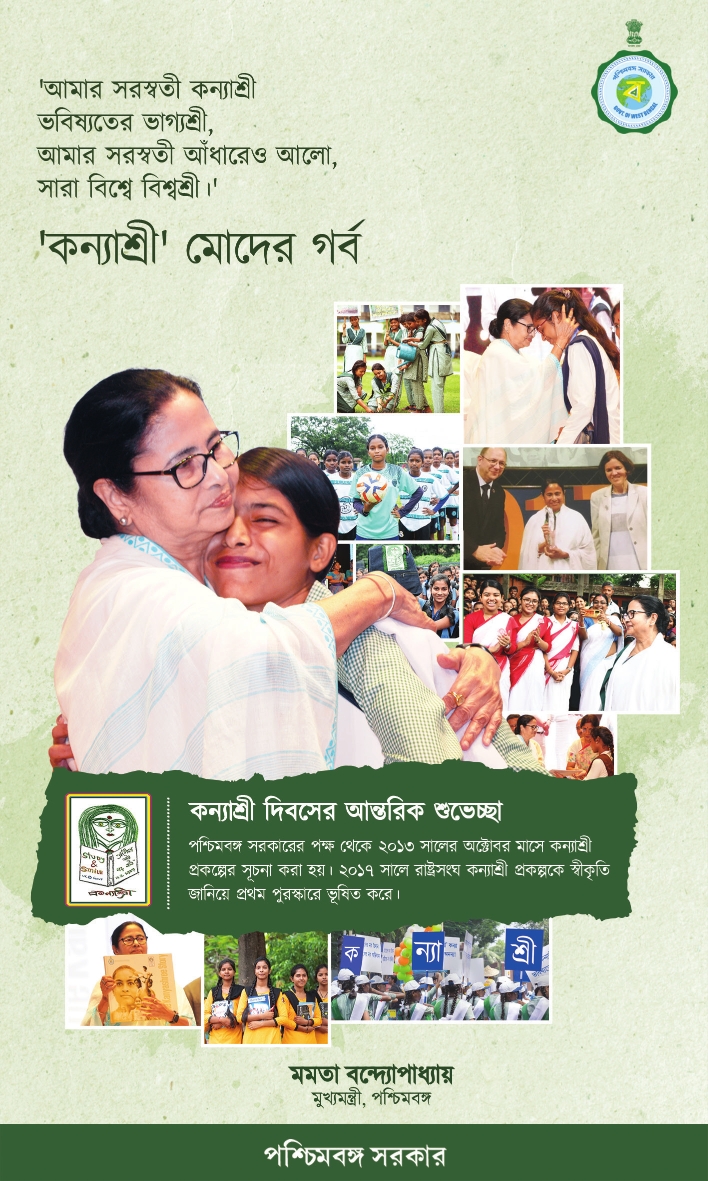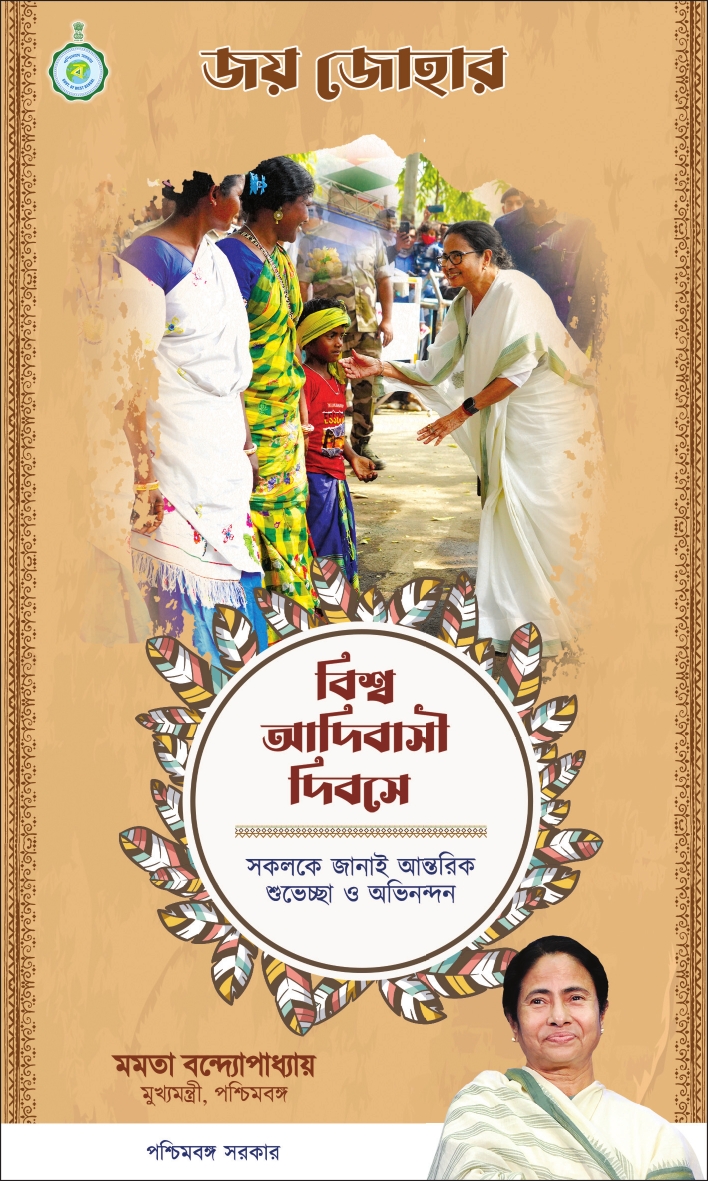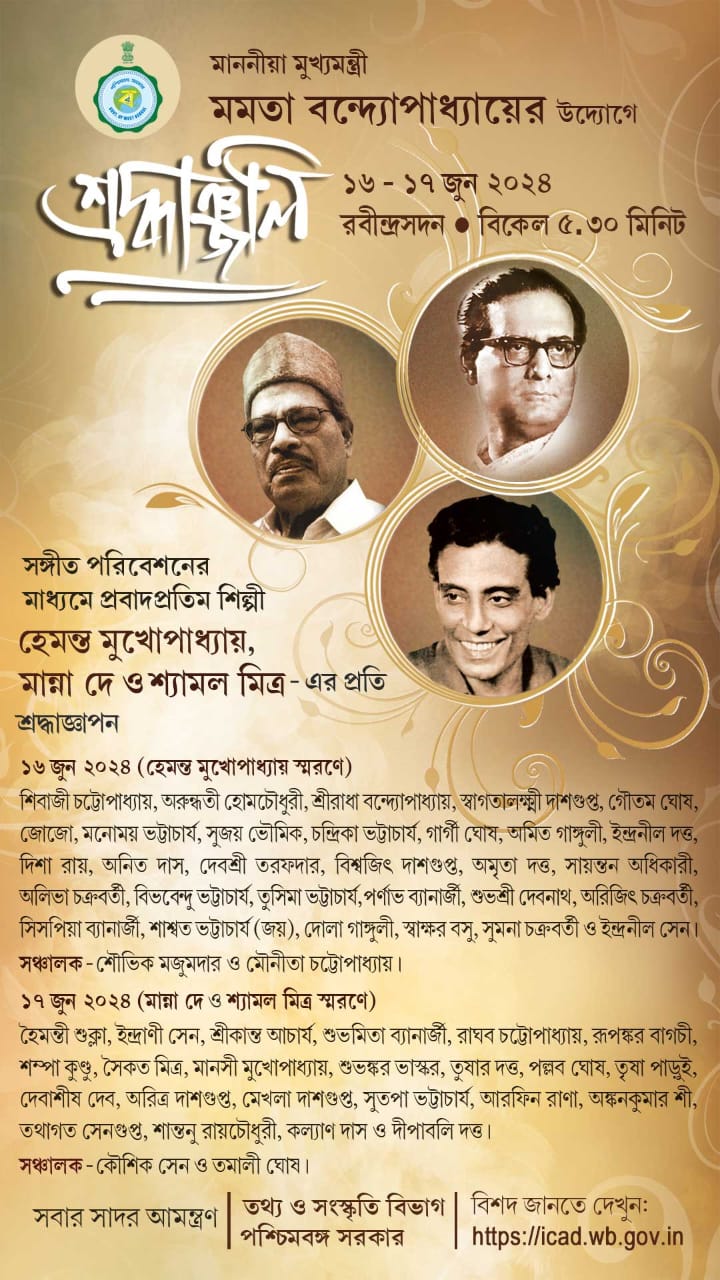“সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন— এই জন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। এ কলার উৎসব হইলে চলে না।’’
এ অনুভব রবীন্দ্রনাথের।
“যিনি নানা স্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমেরই উৎসবের দেবতা— মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।’’
এই প্রাতিস্কিক প্রতীতীও রবীন্দ্রনাথের।

দুর্গাপুজায়, মিলনের মধ্যে প্রেম ও সত্যের শক্তিকে অনুভব করাতেই দুর্গোৎসব সম্পূর্ণতা অর্জন করে। তাই, তাই-ই, নিজে প্রত্যক্ষত দুর্গা-পুজারি না হওয়া উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দুর্গা পুজো।
অনুভবী রবীন্দ্রনাথের দুর্গাপুজো সংক্রান্ত ভাবনা তাই দিভমূঢ়ের হুজুগ নয়, চৈত্রিক দিয়াড়িতে প্রণিহিত।
ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সে পুজো বন্ধ হল রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতি বছরের মতো সেবারও গিয়েছেন রামমোহনকে ঠাকুরবাড়ির পুজোয় নিমন্ত্রণ করার জন্য। জানিয়েছেন, “রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিনদিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।’’
রামমোহন সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। উলটে দেবেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে ছাড়লেন, ঈশ্বর কায়াহীন, শারীরিক অস্তিত্বহীন এক অনুভব। ঈশ্বরীয় ভাবনা দৈহিক নয়, চৈত্তিক। প্রতিমার বোধন সংক্রান্ত লোকাচারে নয়, চৈত্তিক উদ্বোধনে ঈশ্বরীয় বোধের দীপন। এই কথাটা বুঝে ফেলার পরিণামে দেবেন্দ্রনাথের মনোলোকে ওলটপালট। তিনি তাই আত্মজীবনীতে লিখলেন, “যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল।” দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাইরা দলবেঁধে শপথ নিলেন, “পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না, যদি কেহ যাই, তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না।’’
এই বোধ প্রজন্মান্তরে রবীন্দ্রনাথেও সংক্রমিত। সিটি কলেজে সরস্বতী পুজো করতে উদ্যোগী সুভাষচন্দ্র। বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বারাণসীতে শিবলিঙ্গে প্রণাম করেছেন সরলা দেবী। তিরস্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথই ভেসে যান শারদীয় আলোর বেণুর সুরে। ভুবন যখন মেতে ওঠে দুর্গাপুজোর অবকাশে তখন তাঁর পুতুল পুজোর বিরোধিতা কেমন যেন মাতাল হয়ে নিজেকেই খুইয়ে ফেলে।
তাই ২২ অক্টোবর, ১৯০৩ (১৩১০ বঙ্গাব্দের ৬ কার্তিক)-এ লেখা একটা চিঠিতে কাদম্বিনী দেবীর কাছে মনের আগল হাট করে খুলে দেন কবীন্দ্র রবীন্দ্র। লেখেন, “সাকার নিরাকার একটা কথার কথা মাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাই না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহারই।”
পরবর্তী আরও একটি চিঠিতে এই বক্তব্যেরই দৃঢ়তর উপস্থাপন। ১৮ মার্চ, ১৯১২-তে লিখিত সেই পত্রটিরও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কাদম্বিনী দেবী। সেই পত্রে আরও অকপট, আরও প্রতত রবীন্দ্র-ভাবনা।
“প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনও বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনও বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনও মুশকিল থাকে না। তাকে বিশেষ কোনও একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনও দোষ আছে, একথা আমি মনে করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে।’’
অর্থাৎ, দুর্গামূর্তির পুজোয় রবীন্দ্রনাথের কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু কেবল দুর্গার মূর্তিতেই ঈশ্বর প্রকটিত, অন্য কোনও মূর্তিতে কিংবা নিরীশ্বরবাদীয় ভাবনায় ভুবনে ঈশ্বরে নেই। এই সংকীর্ণতায় তাবৎ রাবীন্দ্রিক আপত্তি।
৫ অক্টোবর, ১৮৯৪। বাংলায় তখন শারদীয় আনন্দ উৎসবের প্রহর আসন্ন। চতুর্থী কিংবা পঞ্চমী তিথিতে রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে লেখেন, “কাল দুর্গাপুজো আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত লোকের মনে যখন একটা আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে।” অর্থাৎ, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী নিরাকারবাদী একেশ্বরের উপাসক রবীন্দ্রনাথও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাণঢালা উৎসবে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পারেন না। বাঙালির প্রাণের উৎসব তাঁর প্রাণেও ঢেউ তোলে।
সেবার সুরেশ সমাজপতির বাড়িতে যাওয়ার সময় বড় বড় বাড়ির ঠাকুর দালানে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ তাঁর চোখে পড়েছিল। লক্ষ্য করেছিলেন, সেই প্রতিমা নির্মাণের সময় তা ঘিরে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা। মনে হয়েছিল, “দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই দিনকতকের মতো পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে।’’ ইন্দিরা দেবীকে লেখা উল্লিখিত পত্রে এই বাক্যটি পড়ে যদি কারও মনে হয়, এই হল পৌত্তলিকতা বিরোধী ঠাকুরবাড়ির প্রকৃত বৌদ্ধিক উদ্গীরণ, তবে তাঁর চিঠির পরের লাইনটাও পড়া দরকার। সেটাতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনও উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক’রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়। সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।’’
অর্থাৎ, রবি ঠাকুরের দুগ্গা দালানটি পৌত্তলিকতায় প্রতান নয়, চারদিনের হুজুগমাত্র নয়।
সেই দুর্গা দালানে লগ্ন উৎসবময়তায় দুর্গার চিন্তন ও পূজন সার্থকতা অর্জন করে।
‘কবীনাং কবিতমঃ’ উপলব্ধি করেছিলেন, “একদিকে সত্য, অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্য দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।’’ দুর্গাপুজোয় সমাজমঙ্গলের মধ্য দিয়েই উৎসবের আঙিনা থেকে আনন্দলোকে গমন।
রবীন্দ্রনাথের সংবেদী সতর্ক দৃষ্টি দুর্গাপুজোর এই স্বরূপটিকে চিনতে ভুল করেনি।
“নিখিলে তব কী মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।’’
আরও পড়ুন- আমার বলার কিছু আছে